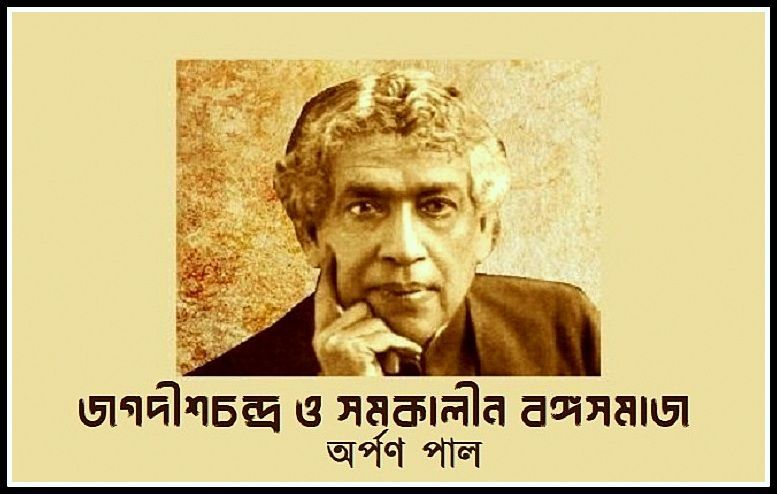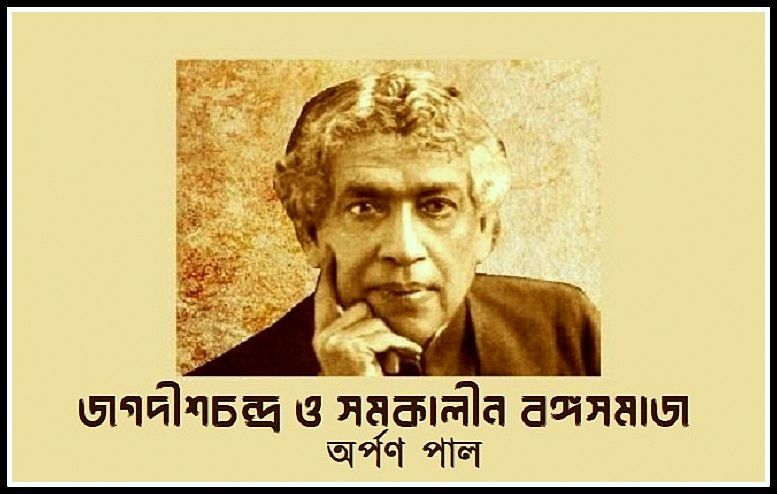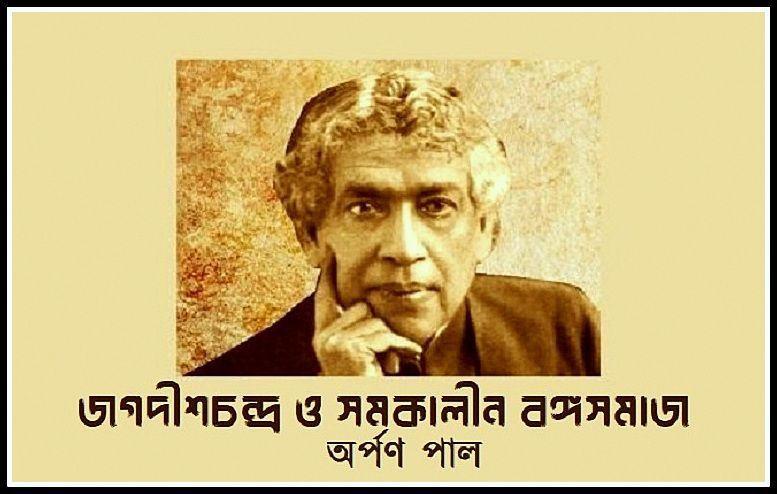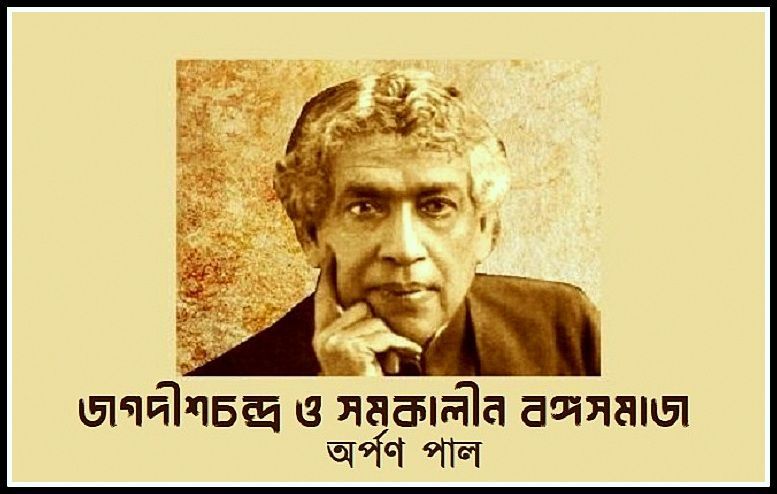পুরানো সেই মিষ্টিকথা
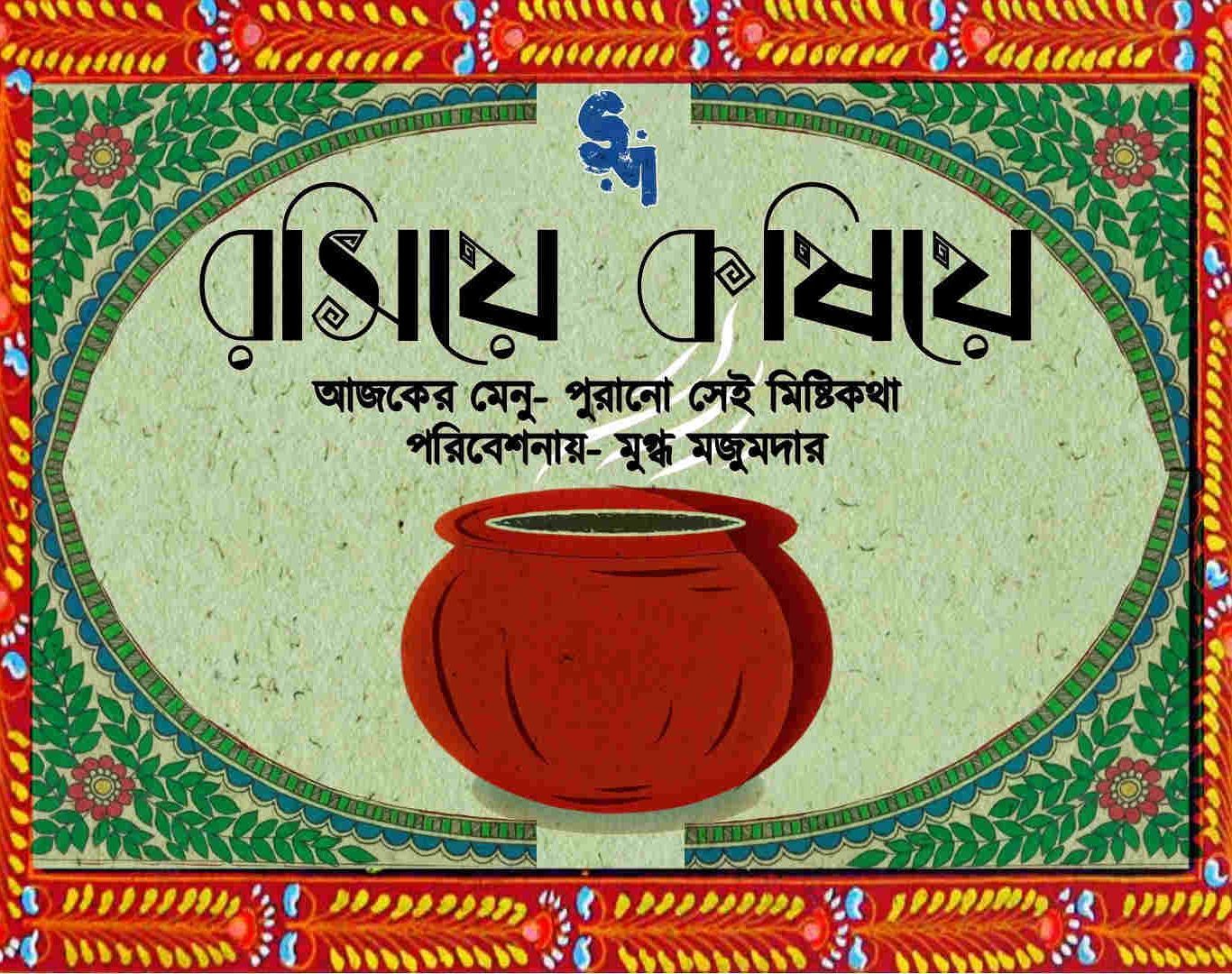
যে সময়টার কথা বলছি সেটা আজকের মতো ছিল না। সেকালে জীবন চলত মন্দাক্রান্তা তালে। আহারেবিহারে, রসিকতায় মানুষের ফুরসত ছিল অনেক বেশি। তখন ইন্টারনেট দুনিয়াদারি ছিল না। ফলে মানুষের মধ্যে ভাব ভালোবাসা হত, লড়াই হত, আবার তা মিটেও যেত হাসিখুশিতে। রাজারাজড়া থাকতেন মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে। কিন্তু গ্রাম-মানুষের রোজকার তন্ত্রীতে তার ছায়া ঘনাত না। সেকালে শিল্পের কদর ছিল। শিল্পীরা শিল্পের পেটেন্ট নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাতেন না। যাই হোক, সেই সময়টার নাম দেওয়া যাক– মধ্যযুগ। মানে মোটামুটি তেরো থেকে আঠার শতাব্দীর বাংলা। এই সময় বাংলার বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন চৈতন্যদেবের মতো ভক্তপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো নামী কবি, রামপ্রসাদের মতো কবিসাধক প্রমুখ। মধ্যযুগের বাংলা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন ইতিহাসবিদ, সমাজবিদ কিংবা সাহিত্যবিদগণ। সেসব গুরুভার আলোচনাকে প্রণাম জানিয়ে আপাতত হেঁশেল ঘরে মুখ মিঠে করা যাক। অর্থাৎ চলো যাই মিষ্টান্নে…
প্রথমেই দেখা যাক সেকালে মিষ্টান্ন বলতে ঠিক কী বোঝানো হত? সংস্কৃত মিষ্ ধাতু (সেচন করা) থেকে মিষ্ট কথাটির জন্ম যার অর্থ সিক্ত বা আর্দ্র করা হয়েছে এমন। অর্থাৎ যে অন্ন বা খাদ্যের মধ্যে রসসিক্ত বা মিষ্ট স্বাদযুক্ত গুণটি বর্তমান, তাকেই মিষ্টান্ন বলা যেতে পারে। মিষ্টির ক্ষেত্রটি ছিল বৃহৎ। ছানা, সর, ক্ষীর, পায়েস থেকে পিঠে, পুলি বা নাড়ু সবই পড়ত মিষ্টান্নের মধ্যে। সেসব মিষ্টি তৈরির মূল উপকরণ ছিল দুধ আর গুড়। অবিশ্যি মিষ্টির জন্য ব্যবহৃত গুড় প্রস্তুত হত আখ থেকে। সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে সেকালে গুড়ের সমৃদ্ধির জন্য বাংলাকে গৌড় নামে ডাকা হত। সেকালে বাংলায় দুধের উৎপাদনও ছিল যথেষ্ট। ‘চর্যা’র ২ সংখ্যক পদে পাওয়া যাচ্ছে দুধ দোয়ানোর কথা– “দুলি দুহি পিটা ধরন না জাই”। বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে দেখা যাচ্ছে আয়ান ঘোষের ‘বিরাট গোয়াল’। আয়ানের স্ত্রী রাধা আর অন্য সব মহিলারা ননী, মাখন বেচতে যেত মথুরায়। এরা সম্ভবত ছিল আহির গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদিকে বারাসাত-বাদুড়িয়ার কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে পরমান্ন রান্নার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। চাঁদ বেণের বাড়ির হেঁশেল। সেখানে রান্না মানেই যেন যজ্ঞিবাড়ির হালচাল। চাঁদের ছয়জন পুত্রবধূ পায়েস রাঁধতে বসেছেন। বিপ্রদাস এর বর্ণনা দিচ্ছেন–
দুগ্ধে চিঁড়া দিয়া কাটি দিল বহুতর।অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল দিলেক তারপর।।পশ্চাতে শর্করা দিয়া ওয়াল্যা রাখিল।আর বধূ এক হাঁড়ি ঘৃত চড়াইল।।সুপক্ক হইল ঘৃত দিয়া সত্বর।পরমান্ন দিল নিয়া তাহার উপর।।
অবশ্য মিষ্টির সবচেয়ে বেশি উল্লেখ পাচ্ছি বৈষ্ণব সাহিত্যে। বোষ্টমরা প্রাণীহত্যা পছন্দ করতেন না। তাঁরা মাছ-মাংস ছুঁতেন না। তাঁদের আমিষ রান্নার ফাঁক পূরণ করেছিল মিষ্টান্ন। খোদ কৃষ্ণই ছিলেন নন্দ গোয়ালার সন্তান। তিনি দধি-ননী চুরি করে খেতেন। চুরি করে খাওয়ার জন্য গোকুলে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফলত কৃষ্ণকথার সূত্রে বোষ্টমদের যে মিষ্টির প্রতি কিছুটা বেশি ঝোঁক থাকবে আশ্চর্য কী! তা ছাড়া বাংলার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। নবদ্বীপে পুরুষোত্তম মোদক তাঁকে মিষ্টি গড়ে খাওয়াতেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী একমুষ্টি অন্নসেবার কথা বলে বিস্তর পদ রেঁধে খাইয়েছিলেন। এর মধ্যে মিষ্টান্নের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মিষ্টি কলার বড়া, ক্ষীর, নারিকেল পুলি, সঘৃত পায়েস, দুগ্ধ লকলকি, সন্দেশ, কী নেই সেই ভোজনপর্বে! একইরকম আরেকটি ভোজনপর্বের উল্লেখ করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সেই ভোজটি হয়েছিল পুরীতে সার্বভৌম মশাইয়ের বাড়িতে। ষাটির মা ছিলেন এই পর্বের রাঁধুনি। তবে মহাপ্রভু আজীবন পেটরোগা ছিলেন। ইদানীংকার মতো সেকালেও ছিল আধিব্যাধি। চৈতন্যদেব ছিলেন গ্যাস্ট্রিক-অ্যাসিডিটিতে ভুক্তভোগী। তাই আহারান্তে কষায়-ক্ষার জাতীয় মুখশুদ্ধি খেতেন। পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের বোন দময়ন্তী দেবী তাঁর জন্য শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ু বানিয়ে পাঠাতেন। এই নাড়ু কীভাবে প্রস্তুত হত তার রেসিপি জানা যায় না। তবে বোঝা যায় আদা শুকিয়ে এই বিশেষ ধরনের নাড়ুটি তৈরি হত। আরেকধরনের নাড়ু বানাতেন দময়ন্তী দেবী। মিষ্টিটির নাম গঙ্গাজলি নাড়ু। নারকেলকোরাকে চিনির সঙ্গে হালকা আঁচে নেড়ে ছাঁচে বসিয়ে তৈরি হত গঙ্গাজলি নাড়ু। তবে এই রান্নায় আঁচের একটা গুরুত্ব আছে। এমনভাবে রান্না করতে হবে যাতে নারকেল কোরা ধরে না যায়। অর্থাৎ শাদাটে রংটি যেন অপরিবর্তিত থাকে। আগুনের কম তাপে পাক হলে নারকেলের ধবধবে শাদা রংটি গঙ্গাজলের রঙে রূপ নিত। সম্ভবত সেইজন্য এমন নামকরণ। ফি-বছর দময়ন্তীর বানানো নাড়ু নিয়ে পুরীতে যেতেন রাঘব পণ্ডিত। চৈতন্যদেব পরমতৃপ্তির সঙ্গে সেসব মিষ্টান্নের স্বাদ নিতেন।
নজরে থাকুক
রসিয়ে কষিয়েঃ দ্বিতীয় পর্বঃ ভোজনের ‘গুরু’-ত্ব
চৈতন্যের প্রয়াণের পর বোষ্টমদের মধ্যে মিষ্টিচর্চা আরো বেশি পপুলার হল। বোষ্টমদের নতুন ঠিকানা হল বৃন্দাবন। সেখানেও মিষ্টির ভীষণ রকমের আদর ছিল। রাধাকৃষ্ণের মোচ্ছব মানেই ছিল মিষ্টান্নের ছড়াছড়ি। দিন যত গড়াল মিষ্টি তৈরিতে হাত পাকালেন বাঙালিরা। শিল্পীদের হাতযশও হল। এল মিষ্টান্ন বিক্রেতারা। মুকুন্দ চক্রবর্তী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে লিখে গেছেন সেকালের কালকেতু ব্যাধের গুজরাট নগরে হালুইকর জাতির লোকজন থাকতেন। এদের পেশাই ছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিষ্টি বিক্রি করা। রামেশ্বরের ‘শিবায়ন’ কাব্যে রয়েছে মোদকদের কথা। এরা মুড়ি, মুড়কি ও মিষ্টান্ন বিক্রি করত। বোঝা যায় বাংলায় মিষ্টান্নের চাহিদা কতখানি ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। শুধু কৃষ্ণ পুজোয় নয়, বাঙালি দেব-দেবীরা ক্রমশ মিষ্টান্ন-প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মধ্য ও অন্ত্যমধ্যযুগে। অনেকের মতে অষ্টাদশ শতকের দিকে পর্তুগিজ বণিকরাই নাকি বাঙালিদের শিখিয়েছিলেন কীভাবে দুধ থেকে ছানা তৈরি করতে হয়। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে বিপুল পরিমাণে ছানার উল্লেখ পাই তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি সাহেবদের আগমনের বহু আগে থেকেই বাঙালিরা ছানা তৈরি করতে জানতেন।
মধ্যযুগের এমন অনেক মিষ্টি ছিল যার খোঁজ আজকে আর পাওয়া যায় না। রসামৃত বা রসামৃতলহরী তার মধ্যে অন্যতম। জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্যে এই মিষ্টিটির উল্লেখ পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বলরামের ভোগ হিসেবে এটি নিবেদিত হত। জল ঝরানো ছানার সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে দক্ষ হাতে ময়েম দিয়ে মণ্ড তৈরি করে রাখা হয়। পরে মণ্ড থেকে গোল্লা আকৃতির চ্যাপ্টা গুছি ঘিয়ে ভেজে মোলায়েম চন্দনী ক্ষীরে ডুবিয়ে রসামৃতলহরী প্রস্তুত করা হত। এইরকম অজস্র হারিয়ে যাওয়া মিষ্টির কথা পাই মধ্যযুগের সাহিত্য জুড়ে। মেট্রোপলিটন রোজনামচায় আমরা নতুনকে স্থান দিয়েছি বটে, কিন্তু পুরোনোকে কি সত্যিই সংরক্ষণ করতে পেরেছি?