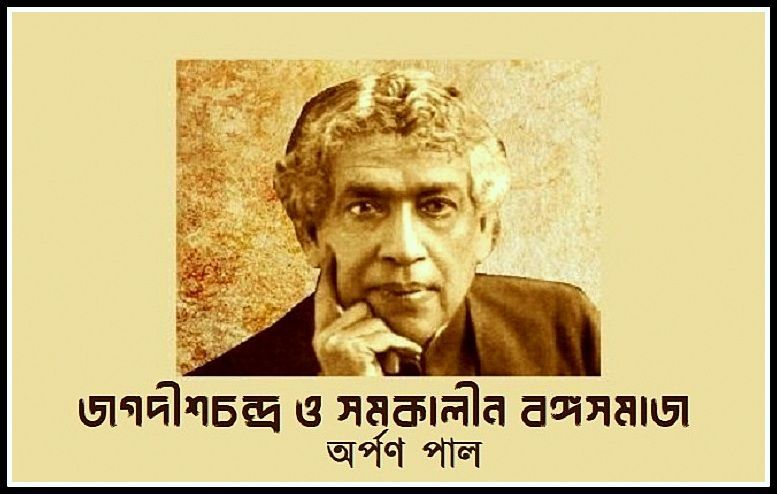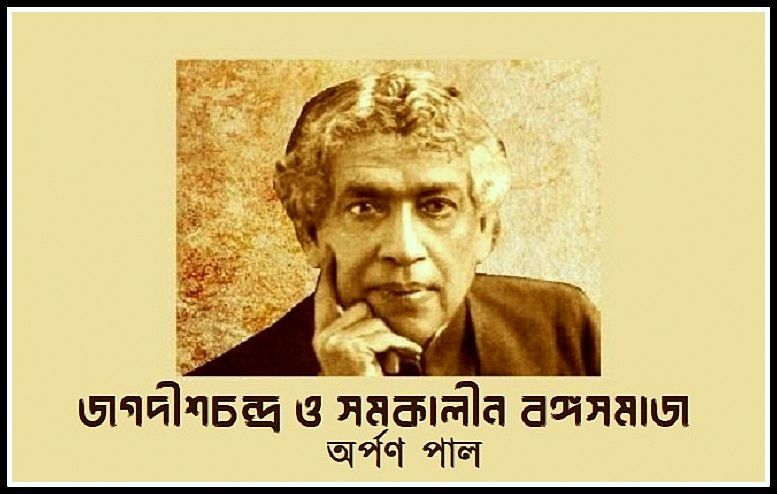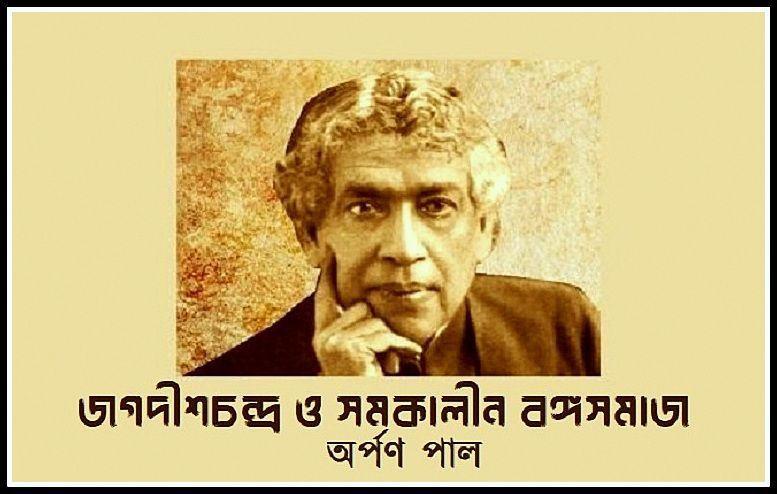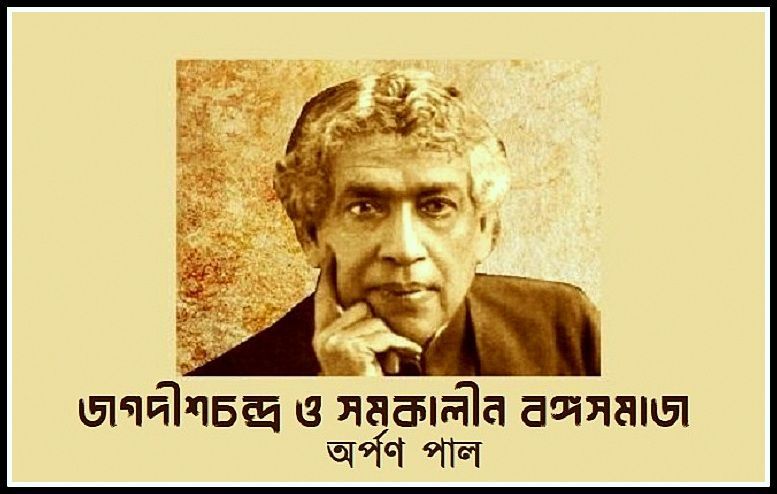পরামানিকরা যেদিন চাপে ফেলে দিয়েছিলেন বাবুদের : কলকাতার একটি শতাব্দীপ্রাচীন ধর্মঘট

তাঁদের হাতেই আমার-আপনার মাথা। তাঁদের হাতেই জাতি-ধর্ম-স্ট্যাটাস নির্বিশেষে মানবসভ্যতার এমন অসহায় আত্মসমর্পণ। হাতে ক্ষুর দেখেও যাঁদের দিকে গলা আপনাকে বাড়িয়ে দিতেই হয়, তাঁরা খচে গেলে কেমন হবে? ভাবতেও শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে আসে। মোটামুটি দেড়শো বছর আগে সত্যিই কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। দু-অক্ষর নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। না। রক্তপাত অবধি গড়ায়নি। তবে বড়সড় একটা কর্মবিরতি পালন করেছিলেন তাঁরা। আজ্ঞে হ্যাঁ। পরামানিক, মানে নাপিতদের ধর্মঘট। খাস কলকাতাতেই।
এমনিতেই ধর্মঘট আর কলকাতা বেশ সেলিব্রেটেড কাপল। উত্তম- সুচিত্রার লেভেলের নয়, তবে নিঃসন্দেহে বেটার লাভস্টোরি দ্যান টোয়াইলাইট। ধর্মঘট, বনধ আর হরতাল - এই তিন জ্ঞাতিভাই হল গিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালির থ্রি ম্যাজিকাল ওয়ার্ডস। অন্তত এক দশক আগেও পরিস্থিতি এমনই ছিল। মাসে তিনটে করে বনধ হত আর আমরা মৎস্য মারিতাম, খাইতাম সুখে। বর্তমান সরকারের কল্যাণে অবশ্য সে সুখ বানপ্রস্থে গিয়াছে। তবে মনে পড়লে এখনও কি মনটা সামান্য চিনচিন করে ওঠে না? অল্প অল্প মেঘ আসেনা হৃদয়- আকাশে? ফোকটের ছুটির অধিকারটুকু এভাবে কেড়ে নেবার জন্য কর্মবিমুখ ল্যাদ-বিলাসী মধ্যবিত্ত মনে মনে এই সরকারকে মোটেই ক্ষমা করেনি।
প্রসঙ্গে ফিরি। অনেকের দেখেছি এমন ধারণা আছে যে কমিউনিস্টদের হাত ধরেই এই বনধ বা ধর্মঘটের সংস্কৃতি আমাদের বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়েছে। একেবারে বুঝভুম্বুল ধারণা। বামেরা এই কালচারের শ্রেষ্ঠ রূপকার হতে পারেন, কিন্তু ভারতে তাঁদের কুঁড়ি আসার বহু আগেই এখানে বেশ কয়েকটা ধর্মঘট পালিত হয়ে গেছে। ইতিহাস বলছে, ভারতের প্রথম ধর্মঘট বাংলাতেই। ১৮২৭ সালে বাংলাদেশে পাল্কিবাহকেরা যে এক মাসের ধর্মঘট পালন করেছিলেন, তার আগে গোটা ভারতে এরকম কোনও প্রয়াসের সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল তার প্রধান পীঠস্থান। এরপর ১৮৫১ সালে গোরুর গাড়ির চালক, অর্থাৎ গাড়োয়ানদের ধর্মঘট বাংলার এবং ভারতের দ্বিতীয় ধর্মঘট। এই দুটি ধর্মঘট নিয়ে একাধিক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ততটা আলো পায়নি তার অনতি-পরবর্তী ধোপা ও ক্ষৌরকারদের ধর্মঘট। আজ এই নিবন্ধে ক্ষৌরকারদের ধর্মঘট বিষয়ে সামান্য দু' চার কথা বলব।
পরামানিক-কুলে তখনও তো জাভেদ হাবিবের মতো যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি প্রমাণ করে ছাড়বেন যে নিজের কাজটা দুর্দান্তভাবে করতে জানলে (এবং সঙ্গে প্যাকেজিংটা দুর্দান্ত হলে, অবশ্যই) ক্ষৌরকাজও মানুষকে প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে। স্বভাবতই ক্ষৌরকারদের মানুষ বলে গ্রাহ্য করতেন না বাবুরা। অথচ তাঁরা হাত তুলে নিলে কী কেয়ামত হতে পারে, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়েছিল তাঁদের। আসলে তখনকার সামাজিক বিন্যাস অনুযায়ী ক্ষৌরকাজ ছিল বংশগত পেশা। মোটামুটি উনিশ শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত জীবিকার সঙ্গেই জাতি ও বর্ণ বিষয়টা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল। সমাজে এ নিয়ে বেশ কড়াকড়ি ছিল। তা ছাড়া সনাতন ভারতীয় মননে বরাবরই পারলৌকিক চিন্তাভাবনার বাড়াবাড়ি। বংশ-নির্দিষ্ট জীবিকা মেনে না চললেই ‘পাপ’। ফলে যে কেউ ইচ্ছে করলেই গোরুর দুধ দুইয়ে বিক্রি করতে পারতেন না, কিংবা হাতে কাঁচি তুলে নিয়ে কাটাকুটির ব্যবসা শুরু করে দিতে পারতেন না। তাই ক্ষৌরকারেরা আচমকা একদিন “কামাব না!” বলে বসায় বাবুসমাজ পড়েছিল মহা বিপাকে। বিপাকটা কত গভীর, তা এই লকডাউনের বাজারে আঁচ করা কঠিন না। অন্যান্য প্রদেশের কথা যদি বাদ-ও দিই, অন্তত মাথা আর গালের চুল-টুল তো মানুষ আজও প্রফেশনাল হাতেই কাটতে চান। তাই নাপিত- ধর্মঘট শুরু হবার চার-পাঁচদিনের মাথায় কলকাতায় ত্রাহি রব উঠে গেল।
কেন হয়েছিল এই ধর্মঘট? অবশ্যই পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্য। তবে এর পিছনে সাহেবদের অবদান অনেকটাই। আয় বাড়ানোর জন্য ইংরেজ সরকার সেসময় পৌর-করের পাশাপাশি যেমন নানা শ্রেণির ব্যবসায়ীদের ওপর কর চাপিয়েছিল, তেমনই রেহাই দেয়নি বিভিন্ন বংশগত পেশায় জড়িত শ্রমজীবী মানুষদেরও। এই ধরনের বৃত্তিগত করের ক্ষেত্রে সরকার খুব ভেবেচিন্তে মোটা টাকা লোটার ব্লু প্রিন্ট কষেছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল ‘লাইসেন্স ফি’। এর অনাদায়ে তাঁদের আর ক্ষৌরবৃত্তি করতে দেওয়া হবে না। এইসব কর আদায়ের জন্য ইংরেজরা আঙুল বেঁকিয়েই রাখত। নির্মমভাবে প্রশাসনিক সাঁড়াশি ব্যবহার করে সরকার বছরের পর বছর কীভাবে বিপুল পরিমাণ কর সংগ্রহ করেছিল তার স্পষ্ট কাগুজে প্রমাণ রয়েছে। ১৮৭৯ সালে ক্ষৌরকর্মীদের ওপর বছরে ১২ টাকা হারে লাইসেন্স ফি ধার্য করা হয়। শহরে ক্ষৌরকর্মীর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। আগেই উল্লেখ করেছি, ধর্ম, সংস্কার, বর্ণ, সামাজিক রীতিনীতির কারণে এ দেশের মানুষ বংশগত বৃত্তি পরিবর্তন করার কথা ভাবতেও পারতেন না। ফলে কর ধার্য করলে পেশাগত নিরাপত্তার কারণেই কর না দিয়ে উপায়ান্তর থাকবে না তাঁদের, এমনই ভেবেছিল সরকার। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে পাল্কিবাহক, গাড়োয়ান বা রজকদের দেখানো পথই বেছে নিলেন ক্ষৌরকর্মীরা।
কার্যক্রম স্থির করার জন্য ক্ষৌরকর্মীরা কলকাতায় গঙ্গার ধারে জগন্নাথ ঘাটে একটি সমাবেশ করলেন। ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকা এই নিয়ে একটি প্রতিবেদনও করেছিল। সেখানে লেখা হয়েছিল : “সেদিন জগন্নাথের ঘাটে নাপিতদের এক সভা হয়। সভাস্থলে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে প্রতি মাথার চুল ছাঁটা এক আনা ও দাড়ি কামানো দু’পয়সা। এখন দু’ পয়সা আর এক পয়সা আছে। শুনিলাম হিন্দুস্থানী নাপিত অনেক জুটিয়াছিল। এক পয়সায় সর্বাঙ্গ কামাবে আর হাত- পা বেশ ঘণ্টাখানেক টিপিয়া দেবে। এক পয়সায় আর কত করিবে। তবে বাজার করা ও জল আনাটা বাকি থাকে কেন? যে রূপে দ্রব্যসামগ্রী দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহারা ও কথা সহজেই বলিতে পারে। ইহার উপর উপযুক্ত লাইসেন্স ও ট্যাক্সের হাঙ্গামা। একজন নাপিতের দিন গুজরান হওয়াই ভার, তার উপর আবার প্রতিজনকে বৎসরে বারো টাকা করিয়া ট্যাক্স! কতই বা রোজগার করে।” এই একই প্রতিবেদনে অবশ্য খানিক উল্টো সুরও ধরা হয়, “আমরা যদি বলি যদি নাপিতেরা ধর্মঘট করিল তখন বাবুরাও ধর্মঘট করুন যে আমরাও আর দাড়ি কামাব না- ঘরে ঘরেই ও কাজটা সারিব।” তবে ‘ঘরে সারিব’ বললেই তো আর হল না। প্রথমত, বাবুদের ঘরে সেই রেওয়াজ একেবারেই ছিল না। দ্বিতীয়ত, শুধু দৈনন্দিন ক্ষৌরকাজ নয়, বিয়ে বা শ্রাদ্ধের মতো নানা সামাজিক অনুষ্ঠানেও ক্ষৌরকর্মীদের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য ছিল। বিশেষত শ্রাদ্ধে গণ-ক্ষৌর কে করবে, নাপিত না থাকলে?
এই ধর্মঘটের পরিণতি কী হয়েছিল সে বিষয়ে অবশ্য নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোণঠাসা মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোটা নিজেই একটা স্টেটমেন্ট। ফলাফল পরের কথা। শ্রমজীবী মানুষ যে নিজেদের উদ্যোগে জোট বাঁধতে শিখে গেছিলেন, সেটা একটা সমাজের পক্ষে নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর। ইংরেজ সরকার সাবধান হয়েছিল কি না বলা মুশকিল, তবে বাবুসমাজ অন্তত একটা বার্তা নিশ্চিতভাবেই পেয়েছিল যে পশ্চাতে যাঁদের রাখা হয়, তাঁরা ইচ্ছে করলেই পশ্চাতের যথেচ্ছ ক্ষতিসাধন করতে পারেন। যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে এখানেও বাংলাই পথ দেখিয়েছিল। পরে বোম্বাই শহরে তিন হাজার ক্ষৌরকর্মী একেবারে এই মডেলেই নানা দাবিদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেন।
নজরে থাকুক
এক হৃদয়ের দুই অলিন্দ : তিলোত্তমা ও ইস্ট-মোহন দ্বন্দ্ব
যে-কোনো অস্ত্র বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যেতে বাধ্য। ফলে আশি সাল পেরোতে না পেরোতে ধর্মঘট জিনিসটাকে আমরা একটা নিয়মতান্ত্রিক প্রহসনে পরিণত হতে দেখেছি। যা ছিল শ্রমজীবী মানুষের দাবি আদায়ের ব্রহ্মাস্ত্র, বহুমাত্রিকতা হারিয়ে অনেকদিনই সে ট্রেড ইউনিউয়ন আর শ্রমিক ইউনিয়নের একচেটিয়া খেলনা হয়ে গেছে। আমরা মধ্যবিত্তরা ছুটি ছাড়া তার অন্য কোনও তাৎপর্য থাকতে পারে বলে শিখিনি। আমরা মৎস্য মেরেছি, খেয়েছি সুখে। আর যাঁদের দাবি আদায়ের জন্য এত আয়োজন, তাঁদের মলিন মুখ মলিনতর হয়েছে। জামার পকেট আরও একটু ছিঁড়ে গেছে। পুজোয় জামা কেনার রেওয়াজটুকু ধরে রাখতে পারেননি তাঁদের বেশিরভাগই। এখন ধর্মঘট মানে ইউনিয়নের শখের ব্যায়ামচর্চা। এখন ধর্মঘট মানে টিনের তলোয়ার। আটের দশকের পর তেমন চমকপ্রদ ধর্মঘট আমাদের চর্মচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, আর দেখতে পাবার আশাও নেই। তাছাড়া বৃত্তিগত ধর্মঘট আর হয়তো আমরা দেখব না। কারণ বংশগত বৃত্তি বিষয়টাই এখন লুপ্তপ্রায়। অন্যান্য অনেক পেশার মতো পরামানিক- বৃত্তিও বহুদিনই আর বংশগত নয়। জোট বাঁধা বড় কঠিন।
ধান্দাবাজি ছাড়া যে কোনও ক্ষেত্রেই এখন জোট বাঁধা কঠিন। তবে তা বলে কোনও মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান বা ন্যয্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত না করাই ভালো। ইতিহাস সবসময়েই আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে এসেছে যে মানুষকে খুব বেশি কোণঠাসা করলে বিষয়টা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে যেতে কে কখন কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে সেটা আগে থেকে বলা মুশকিল। বিশেষত, ক্ষৌরকর্মীদের না চটানোই বোধহয় নিরাপদ। আপনি পঁচিশ টাকা দিয়ে ইটালিয়ান সেলুনেই চুল কাটান বা কাচের এসি ঘরে বসে ‘এমিনেম’ শুনতে শুনতে আড়াইশো টাকার হেয়ারকাট নিন, যাদের হাতে কাঁচি ক্ষুরের মতো জিনিসপত্র থাকে তাদের একটু সমঝে চলাই ভালো।
কখন কী কেটে দেয়…।
[গ্রন্থঋণ : অশোক ঘোষ/ বাংলায় ধর্মঘট/ গাঙচিল, কলকাতা/ প্রথম সংস্করণ/ জানুয়ারি, ২০১৬]
[পোস্টার : অর্পণ দাস।]