শূন্যে ভাসে সারেগামা
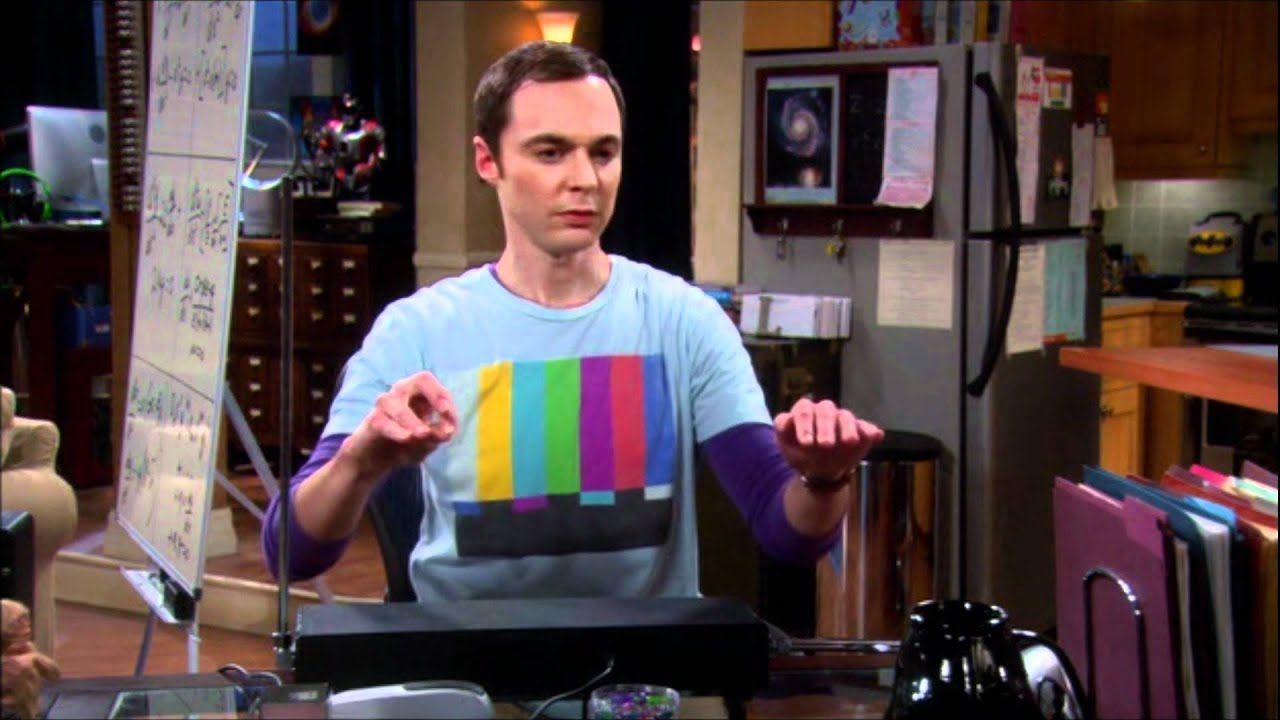
১৯২০ সালের অক্টোবর মাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘা পুরোপুরি শুকোয়নি। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ফিজিক্যাল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের ল্যাবরেটরিতে বছর চব্বিশের এক ছোকরা ইঞ্জিনিয়ার সেদিন মহা ফাঁপরে পড়েছে। শেষ কয়েকমাস ধরে সে একটা যন্ত্র বানাতে ব্যস্ত ছিল, যা দিয়ে কোনো চলন্ত বস্তুর গতি শনাক্ত করা যাবে – আজকাল যাকে আমরা মোশন সেন্সর বলি, সেই জিনিস। বস্তুর গতি তো আর ওভাবে ধরা যায় না, তাই তার চলাফেরার পথে তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র (electromagnetic field) তৈরি করে কম্পাঙ্ক (frequency) মাপা হয়। এর জন্য বাতাসের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের নিখুঁত মাপজোক করতে যে উচ্চ-কম্পাঙ্কের ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রনিক দোলক (oscillator) প্রয়োজন, সেটাও সে নিজেই বানিয়েছে। কাজেই সেন্সর তৈরি হয়ে গেছে সহজেই, মুশকিল হয়েছে তার সঙ্গে অ্যালার্ম লাগানোর পর। যতবার সে সেন্সরের কাছে যাচ্ছে, কম্পাঙ্কের পরিবর্তনের জন্য অ্যালার্মের আওয়াজের তীক্ষ্ণতার কমবেশি হচ্ছে। আর এই কমবেশি তীক্ষ্ণতায় অদ্ভুতভাবে সুরসপ্তক বোঝা যাচ্ছে, কিছুতেই সেই সুরের মোহ ছেড়ে সে বেরোতে পারছে না – সমস্যা এখানেই! সঙ্গীত আর বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি আজকের? হাইস্কুল অবধি তাঁর দু’টিমাত্র শখ ছিল, চেলো বাজানো আর হাতেকলমে বিদ্যুত-চুম্বক-প্রিজমের যন্ত্র বানানো। মাথা খাটিয়ে একবার লক্ষাধিক ভোল্টের টেসলা কয়েল বানিয়ে শিক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকেই সে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আব্রাম ফেদোরোভিচের নজরে পড়ে যায়। ভাগ্যিস! নাহলে একবছর আগে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়, কুখ্যাত হোয়াইট আর্মির হাত থেকে বাঁচিয়ে কে তাকে আশ্রয় দিত এই ইন্সটিটিউটে? ফেদোরোভিচের তত্ত্বাবধানেই তো একের পর এক আবিষ্কার করে চলেছে সে। কিন্তু এখন তাঁর এই সুরের ক্ষ্যাপামি তিনি কি সহ্য করবেন?
সহ্য করেছিলেন ফেদোরোভিচ। রীতিমতো লোক ডেকে সেমিনার করে তাঁর ছাত্রের এই অদ্ভুত কৃতিত্ব সবাইকে দেখিয়েছিলেন। অদ্ভুত কেন? কারণ কোনোরকম স্পর্শ ছাড়াই, শূন্যে হাত বুলিয়ে, এক একটা আস্ত মিউজিক্যাল পিস বাজিয়ে ফেলা যাচ্ছে সেই যন্ত্রে! শুনতে অবাক লাগলেও ঘটনাটা সত্যি। এই সত্যির হাত ধরেই বিজ্ঞানের মঞ্চে এলেন তরুণ প্রতিভা লেভ তেরমেন আর সঙ্গীতের দুনিয়া পেল প্রথম ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র – ইথারফোন। এই আবিষ্কারে মুগ্ধ হলেন স্বয়ং লেনিন; তিনি লেভকে গোটা ইউরোপ ঘুরে তাঁর আবিষ্কার প্রচারের ছাড়পত্র দিলেন। অভূতপূর্ব সাড়া ফেলল সেই মিউজিক্যাল ট্যুর। কথা নেই বার্তা নেই, হাওয়ায় হাত ঘোরালেই নাড়ুর মতো সুর টপকে পড়ছে! যদিও সে সুরে মিষ্টত্ব প্রায় নেই, কেমন জানি গা ছমছমে আবহ। তা ব্যাপারখানাও তো কম ভৌতিক নয়, তাই ভালোই খাপ খেয়ে যায়। এদিকে জাত বিজ্ঞানীর যা স্বভাব, আবিষ্কার করে শান্তি নেই তার উন্নতিও করা চাই। সেদিনের সেই গতি বোঝার যন্ত্র ততদিনে লেভের হাতে ভোল পাল্টে হয়ে গেছে রেডিও ওয়াচম্যান – আজকের সমস্ত হোম অ্যালার্ম সিস্টেমের আদিপুরুষ। ইথারফোনেও কয়েকবার কাটছাঁট করে, সেটিকে অপটিক্যাল প্রযুক্তির সঙ্গে জুড়ে ১৯২৭-এর মধ্যে বানিয়ে ফেললেন রাশিয়ার প্রথম টেলিভিশন সিস্টেম।
সে বছরের শেষে আমেরিকা পাড়ি দিলেন লেভ। সেখানে পৌঁছনোমাত্র পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের হাতে সাধের নামটি খুইয়ে হলেন লিয়ন থেরেমিন আর বাদ্যযন্ত্রটি পরিচিত হল তাঁর নামেই – থেরেমিন। থেরেমিনের পেটেন্ট বাগিয়ে এর ব্যবসায়িক উৎপাদনের ভার দিলেন রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা (RCA)-কে আর নিজে মার্কিন মুলুকে ঘাঁটি গেড়ে শুরু করলেন আরও গবেষণা। জনপ্রিয় সুরকার হেনরি কাওয়েলের অনুপ্রেরণায় তৈরি করলেন বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রনিক তালবাদ্য, রিদ্মিকন। ১৯৩২ সালে কার্নেগি হলে এমন এক কনসার্টের আয়োজন করলেন, যেখানে সবকটি বাদ্যযন্ত্রই ইলেকট্রনিক !
এই সবের গুরুঠাকুর্দা যে যন্ত্রটি, সেই থেরেমিনের রহস্যটা কিন্তু বেশ মজার। এখানে তড়িৎশক্তি দিয়ে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যন্ত্রের ভিতর বৈদ্যুতিক সার্কিট বেয়ে চলে ইলেকট্রনের ছোটাছুটি আর এই ছোটাছুটিকে ব্যাহত করতে বসানো হয় ক্যাপাসিটর। ক্যাপাসিটর জিনিসটা খানিক স্যান্ডউইচের মতো, পাঁউরুটির জায়গায় ভাবুন দুটো প্লেট আর স্টাফিং-এর জায়গায় ভাবুন গ্যাস বা তরল, যা বিদ্যুৎ তথা ইলেকট্রনের কুপরিবাহী। এবার ইলেকট্রনগুলো ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে যেতে না পারলেও তো আর চুপ করে বসে থাকবে না, তারা ক্লোজ্ড সার্কিটের অন্যদিকে ঘুরবে – তৈরি হবে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের অল্টারনেটিং কারেন্ট। কম্পাঙ্কের মাত্রা ২৫০ কিলোহার্ট্জ, মানুষের শ্রবণসীমার অনেক অনেক বাইরে! তবে উপায়? যন্ত্রের ভিতরে রাখা হল আরেকটি সার্কিট, অন্য কম্পাঙ্কের কারেন্ট তৈরির জন্য। এই দুই কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহ মিশিয়ে, হেটেরোডাইনিং নামক বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপন্ন হল এমন প্রবাহ যার কম্পাঙ্ক পিয়ানোর কম্পাঙ্কের প্রায় সমান। বাঃ, কিন্তু এতকিছুর মধ্যে হাতের কাজ কী? ওইখানেই মজা – থেরেমিনের ক্যাপাসিটর বস্তুটি আধাখ্যাঁচড়া, ওই লম্বা অ্যান্টেনাটি তার একটা প্লেট। আর অন্য প্লেট হল আমাদের হাত। ইয়ার্কি হচ্ছে? আজ্ঞে না, মানবদেহ যে তড়িৎপ্রবাহের আখড়া সে কথা তো আমি-আপনি সবাই জানি, লেভ তেরমেন শুধু মাথাটি খাটিয়ে সেটিকে কাজে লাগিয়েছেন। হাত আর অ্যান্টেনার মাঝের দূরত্ব যত বাড়ে-কমে, ক্যাপাসিটারে জমা চার্জের পরিমাণ বাড়ে-কমে, কম্পাঙ্কের মাত্রা বদলায়। এইভাবে শব্দের তীক্ষ্ণতা (pitch) এবং প্রাবল্য (volume), দুইই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সুর সৃষ্টির জন্য বাদ্য ও বাদক, উভয়ের ‘এক দেহ-এক আত্মা’ হয়ে ওঠার এমন রূপক বোধকরি রূপকথাতেই মেলে।
এহেন চমকদার বাজনা কিন্তু বাণিজ্যিক ভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থ। কারণ দেখতে-শুনতে যতই সহজ লাগুক, আদতে এই যন্ত্র বাজানো কঠোর অধ্যবসায়-সাপেক্ষ। ফলত অচিরেই এর বিক্রিতে ভাঁটা পড়ল এবং আপনার সন্তানের হাতে থেরেমিনের বদলে উঠল হারমোনিয়াম। তবু থেরেমিনের ব্যবহারে কিন্তু ফুলস্টপ পড়েনি, বরং বিভিন্ন কাল্ট কম্পোজিশনের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে গেছে। Rolling Stones থেকে Led Zeppelin, বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন রকব্যান্ডের লাইভ পারফরম্যান্সে জায়গা করে নিয়েছে থেরেমিন। তার সুর ব্যবহৃত হয়েছে Spellbound (1945), The Day The Earth Stood Still (1951), The Ten Commandments (1956), The Machinist (2004), First Man (2018) প্রভৃতি সিনেমার আবহে। জনপ্রিয় টিভি সিরিজ The Big Bang Theory-তে জিনিয়াসপ্রবর শেলডনকেও থেরেমিন বাজাতে দেখা যায়।
আরও পড়ুন : বিজ্ঞানের বর্ণভেদ / সায়নদীপ গুপ্ত
বিজ্ঞানের চমৎকার না সুরের ঝংকার – কোন গোত্রে ফেলব এমন যন্ত্রকে? পদার্থবিজ্ঞানী না সঙ্গীতজ্ঞ – কোন দাঁড়িপাল্লায় মাপব লেভ তেরমেনের জিনিয়াসকে? যন্ত্রসঙ্গীতের এই অনন্য রূপকার আমেরিকার মাটিতে বসে কুখ্যাত আলকাত্রাজ কারাগারের জন্য তৈরি করেছেন মেটাল ডিটেকশন সিস্টেম, আবার দেশে ফিরে বানিয়েছেন ইলেকট্রনিক আড়িপাতার যন্ত্র, যা কাজে লাগিয়ে কোল্ড ওয়ারের সময় মার্কিন দূতাবাসের তথ্য হাতিয়েছিল রাশিয়া। এইবছর থেরেমিন আবিষ্কারের শতবার্ষিকী পূর্তি। এই অদ্ভুত প্রতিভার মূল্যায়নের চেষ্টা বৃথা, বরং তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বিজ্ঞানের বিশালতার প্রতি, সুরের সততার প্রতি দায়বদ্ধ থাকাই শ্রেয়। আমরা ওটুকুই পারি।


Triparna
এইরকম একটা অনবদ্য বিষয় নির্বাচনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
দ্বিজিৎ
অজানা জিনিস জানলাম, তাও বেশ একটা সরস গল্পের মত করে। খুব সুন্দর লেখা।
Rupsa
বেশ অদ্ভুত লাগলো পুরো ব্যাপারটা পড়ে।নতুন একটা যন্ত্রের নাম জানলাম ও তার উৎস ও কত অসাধারণ কিছু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এর আবিষ্কারের সাথে জড়িয়ে আছে জেনে দারুন লাগলো সায়ন দা ।লেখাটা খুব ভালো আর এটা যে তোমার কত পড়াশোনার প্রতিফলন , তা বলার অবকাশ রাখে না ☺️