বিজ্ঞানের বর্ণভেদ

Black lives matter – এইটুকু বুঝতে কয়েক শতকের ইতিহাসের বৃত্তে জর্জ ফ্লয়েড আর জেকব ব্লেকের মৃত্যুও ঢুকে গেল। এই বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে হতে হয়তো আরও কিছু মৃত্যু এভাবেই মেনে নেব আমরা। বর্ণবৈষম্য বিষয়টা আমাদের কাছে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ব্যাপারে যত বেশি প্রকট, অন্য কিছুতে ততটাও নয়। ইউরোপের কিছু অংশ ও আমেরিকায় দাসপ্রথার সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকায় সেখানে এই বৈষম্য সমাজে ও মননে গেঁড়ে বসে আছে। শুধুই তাই? বৈষম্য কি শুধুই অধিকারে? বঞ্চনা কি শুধুই সামাজিক বা অর্থনৈতিক? আজ্ঞে না, শিকড় ছড়িয়ে গেছে আরও দূরে। চামড়ার রঙ প্রভাব ফেলেছে আপাত নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলেও।
আশ্চর্য হলেন? চলুন, কয়েক বছর পিছিয়ে যাই। কেমব্রিজের পার্টনার্স হেলথকেয়ার সংস্থায় ২০০৫-০৬ সালে বিভিন্ন সময়ে ৭ জন এমন রোগী ভর্তি হন যারা হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে আক্রান্ত, সোজা কথায় উচ্চ রক্তচাপের কারণে হার্টের জটিল অসুখ। সংস্থার পরীক্ষায় জানা যায়, তাদের এই অসুখ বংশগত; ঘটনাচক্রে এদের মধ্যে ৫ জনই কৃষ্ণাঙ্গ। সেই অনুযায়ী চলে চিকিৎসা। মাত্র কয়েক বছর হল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক জানিয়েছেন, এই তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তবে ভুল হল কোথায়? খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এল বর্ণবৈষম্যের এক অদ্ভুত নজির!
আজ থেকে মোটামুটি বছর কুড়ি আগে মানবদেহের জিন ম্যাপিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। একে প্রক্রিয়া না বলে বিজ্ঞানের মহাযজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয়না। ডিএনএর ডাবল হেলিক্স গঠনের আবিষ্কারক জেমস ওয়াটসনের নেতৃত্বে ১০ বছর ধরে খেটেখুটে মানবদেহের কয়েক কোটি জিনের মানচিত্র বানান সম্ভব হয়। লক্ষ্য একটাই – ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চিকিৎসা ব্যাবস্থাকে আরও উন্নত, আরও ব্যক্তিনির্দিষ্ট করে তোলা। সম্প্রতি জানা গেছে এই যজ্ঞের আগুনে যে ১৭ লক্ষ মানুষ নিজস্ব ডিএনএ নমুনার ঘি ঢেলেছিলেন, তাদের মধ্যে প্রায় ৯৬% নমুনা এসেছে ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত মানুষদের থেকে; অর্থাৎ সাদা চামড়া। যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১৩% আফ্রিকান-আমেরিকান এবং ১৮% হিস্প্যানিক/লাতিন, সেই দেশের চিকিৎসা গবেষণায় এই দুই জনগোষ্ঠীর মিলিত অবদান ৪% মাত্র! ব্রিটেনের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ রিসার্চের সাম্প্রতিক সমীক্ষাত ইউরোপেও এই বৈষম্যের চিহ্ন প্রকট।
সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে? বোঝার জন্য আরেকবার ফিরে যাই সেই কেমব্রিজের সংস্থার কাছে। সেখানে গবেষকরা ওই ৭ জন রোগীর ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখেন, তাদের কিছু জিনগত ত্রুটি আছে। আমাদের এক একটা জিন আসলে এক একটা নির্দিষ্ট কাজের কোড। জিনঘটিত কোন অসুখের পিছনে থাকে এইরকম এক বা একাধিক কোডের কিছু না কিছু ত্রুটি। আর এই ত্রুটি বোঝার উপায় হল ওই জিনের নমুনাকে মানবদেহের স্বাভাবিক বা স্ট্যান্ডার্ড জিন মানচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা। পার্টনার্স হেলথকেয়ারের বিজ্ঞানীরাও সেটাই করছিলেন, কিন্তু তাদের জানা ছিল না, তারা যাকে জিনগত ত্রুটি ভাবছেন সেটা আসলে জিনগত বৈচিত্র্য। ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত মানুষের জিনে যা অস্বাভাবিক, আফ্রিকান মানুষের জন্য তাই স্বাভাবিক, কারণ জাতিগত ভেদে একই জিনের বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকে। যেহেতু সিংহভাগ ইউরোপিয়ান জিন নিয়ে গড়ে উঠেছে স্ট্যান্ডার্ড মানচিত্র, তাই স্ট্যান্ডার্ডের ধারণাতেই থেকে গেছে মহা ভ্রান্তি। যে জীববৈচিত্র্য আমাদের প্রাণজগতের এক চূড়ান্ত সত্য, জিনগত স্তরে তাকেই বিন্দুমাত্র পাত্তা দেওয়া হয়নি। ফলাফল? ব্যক্তিনির্দিষ্ট চিকিৎসার লক্ষ্যমাত্রা থেকে কয়েক দশক পিছিয়ে গেছি আমরা। জিনঘটিত যে কোন অসুখের সর্বোত্তম চিকিৎসা হিসেবে রোগীর জিনসমষ্টির প্রেক্ষিতে ওষুধ এবং ওষুধের মাত্রা স্থির করা হয়, একই অসুখের বিভিন্ন রোগীর জন্য ওষুধের মাত্রা ও চিকিৎসার ধরণ হতে পারে সম্পূর্ণ আলাদা। এমতাবস্থায় রোগনির্ণয়ের মাপকাঠিতেই যদি বৈষম্য থেকে যায়, তাহলে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।
এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। এই ধরণের গবেষণায় নমুনা সংগ্রহের সময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই দস্তুর। তবে কি আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে স্বেচ্ছায় যোগদানে কোন বাধা ছিল? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের আরও একবার টাইম মেশিনে চেপে পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক দশক। ১৯৩২ সাল, আমেরিকার অ্যালাবামা প্রদেশ। সরকারি জনস্বাস্থ্য বিভাগ, টাস্কেগি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলে ওই অঞ্চলের ৬০০ জন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে নিয়ে এক গবেষণা শুরু করল। উদ্দেশ্য, চিকিৎসার অবর্তমানে সিফিলিস রোগের পরিণতি নির্ণয়। আরেকবার পড়ুন। হ্যাঁ, কোন রকম চিকিৎসা না দিয়ে দিনের পর দিন কয়েকশো মানুষের মধ্যে সিফিলিস কীভাবে থাবা বসায়, কতজন সুস্থ হয়, কতজন মারা যায়, আর কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় – এইসব নথিবদ্ধ করা! উল্লেখ্য, ৬০০ জনের মধ্যে ২০১ জন ছিলেন সুস্থ অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় কন্ট্রোল গ্রুপ; বাকি ৩৯৯ জন রোগাক্রান্ত, এবং এদের কাউকেই কখনও জানানো হয়নি যে চিকিৎসা দেওয়া হবে না! উল্টে তাদের বিনা খরচে চিকিৎসার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আর সেই আশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ প্লেসিবো ওষুধ দেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন? না স্যার, ১৯৩২ থেকে ১৯৭২; দীর্ঘ ৪০ বছর। এর মধ্যে রোগাক্রান্তরা মারা গেছে, তাদের থেকে সংক্রমিত হয়েছে আরও অনেকে, এবং ভূমিষ্ঠ হয়েছে ১৯টি শিশু যারা জন্মাবধি সিফিলিসে আক্রান্ত!
এরপরেও ভয় হয়না? এরপরেও বিশ্বাস থাকে দেশের সরকারের উপর? এরপরেও কি কোন কৃষ্ণাঙ্গ নিজের ডিএনএ দিতে সম্মত না হলে তাকে বলা যায়, “বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যোগদান তোমার কর্তব্য”? যে সমাজে গায়ের রঙ কালো বলে বাসের সিট পাওয়ার জন্যও লড়তে হয়েছে, যে শাসনে কালো মানেই সন্দেহজনক, সেখানে ডিএনএ চাইলে তা গবেষণায় লাগবে নাকি মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানোর কাজে, সেই ভ্রান্তি অমূলক নয়। রোগমুক্ত মানবসভ্যতা যদি বিজ্ঞানীদের স্থির সংকল্প হয়, এই ভ্রান্তি দূর করার কাজে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মিশে, তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করে তাদের বিশ্বজনীন বিজ্ঞানচর্যায় একাত্ম করতে হবে। এই কাজের জন্যও বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদের হতে হবে এই জনগোষ্ঠীরই একজন। তবেই আশ্বাস পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে, ভবিষ্যতে যে কোন মানুষের জিনগত নমুনা নিলে তার বৌদ্ধিক স্বত্বের অধিকার যাতে কোনভাবেই লঙ্ঘিত না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ক্যানসারের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির পিছনে HeLa কোষ প্রদানকারী হেনরিয়েটা ল্যাক্সের বঞ্চনা কীভাবে চাপা পড়ে গেছে, তা অল্পবিস্তর আমরা অনেকেই হয়ত জানি। বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ না করার জন্যও এই বঞ্চনাও কম দায়ী নয়।
আপাতত এইটুকুই সুখবর, দেরিতে হলেও উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। আমেরিকায় All of Us, ব্রিটেনে Future Genetics, আফ্রিকা মহাদেশে Human Heredity and Health in Africa (H3Africa) – এই সবকিছুর উদ্দেশ্য, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসার সুফল পৌঁছে দেওয়া। মঞ্জিল এখনও দূরে, খরচ এখনও সাধ্যের বাইরে। তবু সব গোত্রের মানুষকে সামিল করা গেলে অন্তত প্রথম ধাপটুকু দৃঢ়ভাবে পেরনো যায়।
ঋণস্বীকার :
(১) “Fighting Unfairness in Genetic Medicine” by Stephanie Devaney, Scientific American
(২) Tuskegee Experiment, www.history.com
#বিজ্ঞান #বর্ণভেদ #সায়নদীপ গুপ্ত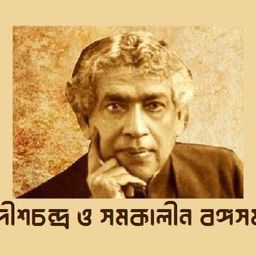
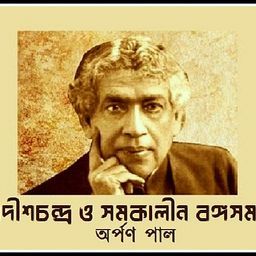
Soumya
ভালো লেখা। শেষের অংশটা বেশ ভয়াবহ! আচ্ছা, মার্কিন সরকার এইসব ঘটনা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি!
ধ্রুব ঘোষ
সমাজসচেতনতামূলক, প্রাসঙ্গিক, ও বিজ্ঞানের সরলীকরণে সমৃদ্ধ সুন্দর এক প্রবন্ধ