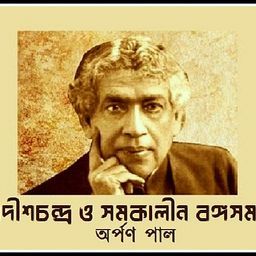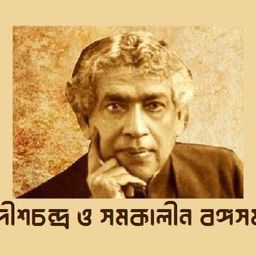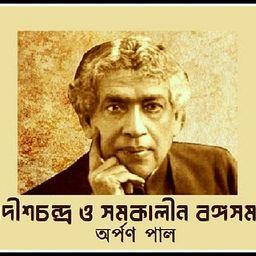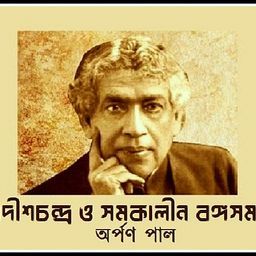কোভিড সুনামির দ্বিতীয় ঢেউ ও আমরা

কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ প্রবল শক্তিতে আছড়ে পড়েছে ভারতে। দিল্লি-মহারাষ্ট্র সহ কিছু রাজ্য ইতোমধ্যে বিধ্বস্ত। পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিদিন বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। সরকারি-বেসরকারি সব হাসপাতালে কোভিড রোগীর জন্য নির্দিষ্ট শয্যাসংখ্যা বাড়িয়েও পরিস্থিতি সামলানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। ২রা মে ২০২১ ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৮,০৬০ জন মানুষ, মারা গেছেন ৩,৪২২ জন। এগুলো সরকারি পরিসংখ্যান, যা প্রতিদিন বাড়ছে। বাস্তবে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। পরিস্থিতি মোটের ওপর উদ্বেগজনক, অথচ গতবছরের তুলনায় এবার মানুষের সচেতনতা আরও কম। তাই বিজ্ঞানের জটিল কচকচি এড়িয়েও তার নির্যাসটুকু পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।
virus disease 2019 (COVID-19) একটি ভাইরাস-ঘটিত রোগ। ২০০২ সালের Severe acute respiratory syndrome (SARS) নামক রোগ হয়েছিল যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে, তার সমগোত্রীয় (কিছু জিনগত তফাৎ সহ) বলে বর্তমান ভাইরাসটিকে SARS corona virus-2 (SARS-CoV-2) নাম দেওয়া হয়েছে। ভাইরাস হল জীব ও জড়ের মাঝামাঝি একধরণের সংক্রামক পদার্থ। একমাত্র সংক্রামিত জীবকোষের মধ্যেই এদের জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়, তার বাইরে এরা জড়বৎ। ভাইরাসের মূল উপাদান হল একটি জেনেটিক পদার্থ (DNA/RNA) এবং তাকে ঘিরে প্রোটিনযুক্ত পুঁতির সমন্বয়ে গঠিত ক্যাপসিড (Capsid) নামক একটি খোলস। জেনেটিক পদার্থ এবং ক্যাপসিডের বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাইরাস আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সদস্য। প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক ভাইরাসের খোলসে নেই, এমনকি তার জিনে সেগুলো তৈরি করার সংকেতও নেই। কাজেই এসবের জন্য অন্য কোনও কোষকে অবলম্বন করতেই হয়। কিছু ভাইরাসের ক্যাপসিডের বাইরে একটি স্নেহপদার্থযুক্ত পর্দা (Envelope) থাকে। আশ্রয়দাতা কোষের পর্দাকেই একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে ভাইরাস নিজের গায়ে একে চাদরের মতো জড়িয়ে নেয়। স্নেহপদার্থ দিয়ে তৈরি এই চাদর কড়া অ্যালকোহল বা ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। করোনাভাইরাসের এরকম পর্দা আছে, তাই বারবার ভালো করে অন্তত কুড়ি সেকেণ্ড সাবান দিয়ে হাত ধুলে একে নষ্ট করা যায়।
কোষের গায়ের নির্দিষ্ট প্রোটিন অণুকে গ্রাহক হিসেবে ব্যবহার করে ভাইরাস সেই কোষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তারপর খোলস ছেড়ে তার আরএনএ বা ডিএনএ কোষের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং তার মধ্যে সঞ্চিত রসদ কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ভাইরাস-দেহ নির্মাণ এবং পরিশেষে আশ্রয়দাতা কোষের ধ্বংসপ্রাপ্তি করে অন্যান্য কোষে ছড়িয়ে পড়ে। এহেন করোনাভাইরাস ‘Angiotensin converting enzyme-2’ (ACE2) নামক একটি মানবকোষের প্রোটিনকে গ্রাহক হিসেবে ব্যবহার করে। কিছু প্রেশারের ওষুধ এই গ্রাহকের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। অনেকে ভেবেছেন এর ফলে COVID-19 সংক্রমণের তীব্রতা বাড়তে পারে, তাই স্বেচ্ছায় প্রেশারের ওষুধ বদলেছেন বা বন্ধ করেছেন। বাস্তবে এসব ওষুধ খেলে কতটা ক্ষতি হবে তা প্রমাণিত নয় কিন্তু ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করলে স্ট্রোক বা হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল প্রেশারের ওষুধ যেমন চলছিল, তেমনই চালিয়ে যাওয়া।
এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের শরীরে একটি ভাইরাস কীভাবে পৌঁছবে, তার পদ্ধতি নির্দিষ্ট। SARS-CoV-2 আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে নাক-মুখ বা চোখ দিয়ে। এই কারণেই নাক-মুখ-চোখ আড়াল করার জন্য মাস্ক-ফেস শিল্ড ব্যবহার করতে বলা হয়। কোনও সংক্রামিত ব্যক্তির হাঁচি-কাশিতে বা কথা বলার সময় ভাইরাসবাহী বহু জলীয় বিন্দু (droplets) নির্গত হয়। এগুলো সাধারণত ছয় ফুট পর্যন্ত যেতে পারে, কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে এর তিন-চার গুণ দূরত্ব অতিক্রম করাও সম্ভব। এরা সরাসরি আমাদের নাকে-মুখে ঢুকতে পারে অথবা বিভিন্ন জিনিসের উপর পড়তে পারে। দরজার হাতল থেকে পলিথিনের প্যাকেট বা জামা-কাপড়ের উপর ভাইরাসটি বেঁচে থাকতে পারে কয়েক ঘণ্টা থেকে দু-চারদিন অবধি। এসব কারণেই শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, নাক-মুখ বাহু বা মুখোশে আড়াল করা, চোখ-নাক-মুখে অপ্রয়োজনে হাত না দেওয়া এবং বাইরের জিনিস ছোঁওয়ার পরে বা নিজের চোখ-নাক-মুখে হাত দেওয়ার আগে ভালো করে হাত ধোওয়া জরুরি।
গবেষণায় দেখা গেছে বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজের সময় কৃত্রিমভাবে বাতাস-বিস্ফোরণে ভাইরাস-পূর্ণ বিশেষ ধরণের ড্রপলেট তৈরি হতে পারে যা বদ্ধ ঘরের বাতাসে ঘণ্টা পাঁচেক ভেসে থাকতে সক্ষম। এইভাবে সংক্রামিত হওয়ার ভয় মূলত ঐ পরিবেশে কর্মরত চিকিৎসক-নার্সদের। গতবছর ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষকেরা দাবি করেছেন, ১৯৩০ সালের গবেষণার ভিত্তিতে প্রচারিত ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখার উপদেশটি যথেষ্ট নয়। জোরে হাঁচলে-কাশলে যে ড্রপলেট তৈরি হয়, তা ২৭ ফুট অবধি যেতে পারে এবং তা খানিক শুকিয়ে যাওয়ার পরে যে সূক্ষ্মতর পদার্থ (droplet nucleus) পড়ে থাকে, তা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে কয়েক ঘণ্টা। এতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা আমাদের দেশে সম্ভব নয়, তবে জনবহুল স্থানে সবাই যদি মুখোশ পরে থাকেন এবং হাঁচি-কাশির সময় বাহু দিয়ে (হাতের তালু দিয়ে নয়) নিজের নাক-মুখ আড়াল করেন, তাহলে ভাইরাস এতটা ছড়িয়ে পড়ার ভয় থাকে না। সেক্ষেত্রে ছয় ফুট দূরত্বই যথেষ্ট।
শরীরে প্রবেশের পর করোনাভাইরাস প্রথমে শ্বাসনালীর উপরের দিকে বাসা বাঁধে, পরে ক্রমশ ফুসফুসে প্রবেশ করে। সংক্রমণ শরীরের কোন অংশে কতটা ছড়াচ্ছে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা (immunity) কেমন কাজ করছে, তার উপর নির্ভর করে রোগের তীব্রতা। শরীরে ভাইরাস থাকলেও কোনও রোগলক্ষণ থাকে না অনেকের। এই asymptomatic carrier-রা কিন্তু জীবাণু ছড়াতে সক্ষম, যদিও হাঁচি-কাশি না হওয়ায় কম ছড়াবে। সংক্রমণের পর ভাইরাসের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সময় (incubation period) পেরোলে রোগের লক্ষণ দেখা যায় – যা করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে গড়ে পাঁচদিন, যদিও ১৪ দিনের মধ্যেও রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যাঁরা কোনোভাবে সংক্রামিত মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন বা এসে থাকতে পারেন, তাঁদের উচিত এই সময়টুকু অন্যদের থেকে আলাদা থাকা, যাতে অজান্তে সংক্রমণ না ছড়ায়।
শুরুতে শুকনো কাশি, গলায় ব্যথা, জ্বর, গায়ে-মাথায় ব্যথা, বমি ভাব, খিদে কমে যাওয়া, খানিক পেটে ব্যথা আর পাতলা পায়খানা ইত্যাদি হতে পারে। ঘ্রাণশক্তি কমে যাওয়া COVID-19 এর এক বিশেষ লক্ষণ। এরপর যখন ভাইরাস ফুসফুসের ক্ষতি (নিউমোনিয়া) শুরু করে, তখন শ্বাসকষ্ট স্পষ্ট হতে থাকে। রোগলক্ষণ শুরু হওয়ার ৭-১০ দিনের মাথায় শরীর মরিয়া হয়ে এলোপাথাড়ি প্রতি-আক্রমণ শুরু করে এবং সেইসব অস্ত্রের ঝড়ে (cytokine storm) আচমকা ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে “Acute respiratory distress syndrome” (ARDS) নামক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কারও কারও প্রথমেই শ্বাসকষ্ট হতে পারে আবার অনেকের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ৭৫% হওয়ার পরেও শ্বাসকষ্ট থাকে না। হৃদপিণ্ড বা মস্তিষ্কও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিছু ক্ষেত্রে। রক্তে লিমফোসাইট কমে নিউট্রোফিল বেড়ে যাওয়া বা ইন্টারলিউকিন-৬ নামক রাসায়নিকটির বৃদ্ধিকে অশনিসংকেত হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া বড় ভয় হল বেজায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া – যা স্ট্রোক, অঙ্গহানি বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ভাইরাস শরীরের কতটা ক্ষতি করতে পারবে তা ভাইরাস আর শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার লড়াইয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বার্ধক্য, ডায়াবেটিস, কিডনির অসুখ, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন অসুখে যেহেতু প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, তাই এইসব রোগীদের শরীরে COVID-19 অনেক বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম।
শরীরে SARS-CoV-2-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য শ্বাসনালীর উপরের অংশের (Nasopharynx) দেওয়াল থেকে সংগ্রহ করা রস (swab) পরীক্ষা করা হয়। Polymerase chain reaction (PCR) পদ্ধতিতে ভাইরাসটির আরএনএ বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াটিই প্রামাণ্য। TrueNAT, CB-NAT ইত্যাদি পরীক্ষাগুলোও উচ্চমানের। সহজতর এবং সস্তা কিছু পরীক্ষা (যেমন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট) ব্যাপক হারে জনগণের স্ক্রিনিং করতে কার্যকর। ফুসফুসের High Resolution CT Scan কোভিড নিউমোনিয়া চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। অবশ্য রোগের বিভিন্ন লক্ষণ আর প্রাথমিক পরীক্ষার ফল দেখেও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ধরতে পারবেন যে রোগীর COVID-19 হয়েছে। রোগীর সংখ্যা যদি খুব বেড়ে যায়, তখন চিকিৎসকের আন্দাজকেই মান্য ধরে নিয়ে চিকিৎসা চালাতে হবে।
সংক্রামিত সব ব্যক্তির শরীরে সমপরিমাণ ভাইরাস (viral load) থাকে না। PCR পদ্ধতিতে করোনাভাইরাস পরীক্ষা করার সময় এর পরিমাণ অনুমান করা যায়। যে ব্যক্তির শ্বাসনালীতে এই ভাইরাসের পরিমাণ বেশি, তার রোগের তীব্রতা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাঁর থেকে ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনাও (infectivity) অধিক বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সংক্রামিত হওয়ার সময় একবারে কতটা ভাইরাস শরীরে ঢুকল (infective dose), তার সঙ্গে রোগের তীব্রতার সম্পর্ক COVID-19 এর ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত না হলেও বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। মানুষের শরীরে এই ভাইরাসের পূর্বপরিচয় নেই বলে ভাইরাস এবং ইমিউনিটি উভয়কেই দৌড় শুরু করতে হয় একসঙ্গে। ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে থাকে এবং ইমিউনিটিও তাকে চিনে নিয়ে তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে তাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করে। মনে করুন প্রথমে এক লক্ষ ভাইরাস দেহে প্রবেশ করলে তারা যে হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে আপনার ইমিউনিটি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এবং এর ফলে কাশি, জ্বর জাতীয় কিছু উপসর্গ হয়, কিন্তু ফুসফুসের বড় ক্ষতির আগেই আপনার প্রতিরক্ষাবাহিনী ভাইরাসকে কব্জা করে ফেলে। তাহলে দশ হাজার ভাইরাস প্রথমবারে প্রবেশ করলে আপনার হয়ত কোনও উপসর্গই হবে না, আবার আক্রমণকারীর সংখ্যা প্রথমেই এককোটি হলে আপনি হয়ত মারাত্মকভাবে অসুস্থ হবেন। জার্মানিতে প্রথমদিকের কিছু ছোটখাটো পরীক্ষায় এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি কিন্তু দেখা গেছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে COVID-19-এ মৃত্যুর হার অন্যদের তুলনায় বেশি এবং অনেক কম বয়সের চিকিৎসকেরাও মারা যাচ্ছেন, যা থেকে অনেকেই মনে করছেন ইনফেক্টিভ ডোজ আর অসুখের ভয়াবহতার মধ্যে বাস্তবে সম্পর্ক আছে। একজন সংক্রামিত ব্যক্তির সন্নিধানে দশ মিনিট কাটিয়ে আপনি যতগুলো ভাইরাস পেতে পারেন, COVID-19 ওয়ার্ডে কাজ করা চিকিৎসক-নার্সেরা দীর্ঘ সময় রোগীদের সঙ্গে নিয়মিত কাটিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাইরাস পারিশ্রমিকস্বরূপ পান। এর ফলে তাঁদের ইমিউনিটি অসম যুদ্ধে পেরে ওঠে না এবং ফল হয় ভয়ঙ্কর।
এই যুক্তিতে দু’ধরনের জিনিসের গুরুত্ব বোঝা যায় -
(১) মাস্ক, ফেসশিল্ড, পিপিই ইত্যাদি; এগুলি ইনফেক্টিভ ডোজ কমাতে সাহায্য করে। যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে কোভিড রোগীদের পরিচর্যা করছেন, তাঁরা পিপিই পরবেন। অন্যরা জনবহুল স্থানে অন্তত মাস্কটুকু (পারলে ফেসশিল্ড) পরবেন। মাস্ক পরা সত্ত্বেও অমুকবাবু অসুস্থ হয়েছেন তাই আমরা পরব না, এই জাতীয় কুযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অনুচিত। বিষ না খেয়েও অনেকেই মারা যান বলে নিশ্চয়ই আমরা সায়ানাইড খাব না। মাস্ক ব্যবহার না করা ব্যক্তি-স্বাধীনতা হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না, কারণ এভাবে অনেকের শরীরে ভাইরাস ছড়িয়ে অন্য মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করা হয়।
(২) ভ্যাক্সিন; এইটি আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনীকে আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখে। কোনও ভ্যাক্সিন ১০০% সুরক্ষা দেয় না, কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে অন্তত ভয়াবহ অসুখ আর মৃত্যু থেকে বাঁচাতে সক্ষম। বেশিরভাগ রোগ এবং ওষুধের সঙ্গে কোভিড ভ্যাক্সিনের কোনও ঝগড়া নেই, তবু সন্দেহ থাকলে নিজের চিকিৎসককে সরাসরি প্রশ্ন করুন। একবার কোভিড হলে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, তা সম্ভবত যথেষ্ট শক্তিশালী বা দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই সেরে ওঠা রোগীরাও ভ্যাক্সিন নেবেন।
অনেক ভাইরাসই বহুরূপী, করোনাভাইরাসও তাই। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে আসার আগেই জিনগত পরিবর্তনের ফলে ভাইরাসটির অনেকগুলো নতুন রূপ (mutant) সামনে এসেছে। এদের মধ্যে সাউথ-আফ্রিকান মিউট্যান্ট বেশ চিন্তার কারণ। ভারতে এবার কিছু ডাবল এবং ট্রিপল মিউট্যান্ট (দুই বা তিন ধরনের করোনাভাইরাসের জেনেটিক সংমিশ্রণজাত) পাওয়া গেছে। গবেষকদের মতে এদের সংক্রমণক্ষমতা বেশি, হয়ত কিছুটা বেশি ক্ষতিকর এবং আগে কোভিড হওয়ার কারণে শরীরে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক প্রতিরোধকে বোকা বানাতে সক্ষম। এরা ভ্যাক্সিনের নাগাল এড়াতে পারে কিনা, তা প্রমাণিত নয়, তবে কোভিশিল্ড বা অন্য কিছু উন্নত ভ্যাক্সিন যেহেতু শুধুমাত্র ভাইরাসটির স্পাইক প্রোটিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে, তাই নতুন মিউট্যান্টের কাছে এদের পর্যুদস্ত হওয়ার সামান্য সম্ভাবনা থেকে যায়। কোভ্যাক্সিনে গোটা ভাইরাসটির মৃতদেহ থাকে বলে তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ মিউট্যান্টগুলোর বিরুদ্ধেও কার্যকর হবে বলে প্রাথমিক পরীক্ষায় অনুমান, কিন্তু সেকথা জোর দিয়ে বলার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। তাছাড়া ভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরেও ছয় সপ্তাহ লাগতে পারে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে, তাই ভ্যাক্সিন নিয়ে মাস্ক-সাবান-স্যানিটাইজারকে টা-টা করা চলবে না।
কোভিড আটকানোর জন্য ভিটামিন-সি, বি-কমপ্লেক্স, জিংক ইত্যাদি খেতেই পারেন, কিন্তু এদের উপযোগিতা প্রমাণিত নয়। এদের ভরসায় প্রমাণিত পদ্ধতিগুলো বাদ দেবেন না। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন প্রোফাইল্যাক্সিসের যথার্থতাও অপ্রমাণিত, ভ্যাক্সিন নেওয়ার পর এটা খেলে বরং ইমিউনিটি তৈরিতে বাধা পড়তে পারে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারত, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া সহ কিছু দেশের বিশেষজ্ঞরা আইভারমেক্টিন এবং ডক্সিসাইক্লিন নামক দুটি ওষুধ ব্যবহার করছেন, তবে অনেক বিশেষজ্ঞ আবার এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে একমত নন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আস্ফালন সত্ত্বেও অ্যাজিথ্রোমাইসিন বিশেষ কাজের নয়। ফ্যাভিপিরাভির অনেক বিক্রি হল গত বছর কিন্তু ফল উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় চিকিৎসকেরা উৎসাহ হারিয়েছেন। রেমডেসভির নামক একটি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ বেশ কাজের, কিন্তু মৃতসঞ্জীবনী সুধা নয়। মৃদু কোভিডে এর কোনও ভূমিকা নেই, আবার রোগের শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করলেও কাজ করে না। মাঝারি ও বাড়াবাড়ি পর্যায়ে ঠিক সময়ে প্রয়োগ করলে কাজে আসে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে বেশ কিছু। সুতরাং গুগল ঘেঁটে চিকিৎসককে চাপ দেবেন না এই ওষুধটি দেওয়ার জন্য বা কালোবাজারে বহুমূল্যে কিনে বাড়িতে নিজের উপর প্রয়োগ করবেন না। ইন্টারলিউকিন-৬ ঘটিত সাইটোকাইন ঝড়ের বিরুদ্ধে কার্যকর টসিলিজুম্যাব নামক একটি দামি ওষুধের জন্য হাহাকার চোখে পড়ছে। ওষুধটি নির্দিষ্ট কিছু রোগীর বাইরে বেশিরভাগের জন্যই কার্যকর নয় এবং প্রাণঘাতী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। সস্তা ডেক্সামিথাসোন বরং কাজের, কিন্তু যাঁদের রোগ মাঝারি পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অক্সিজেন লাগছে, একমাত্র তাঁদের জন্যই। সুতরাং চিকিৎসা বিষয়ক সিদ্ধান্ত চিকিৎসকদেরই নিতে দিন। নিজেরা সুরক্ষার নিয়মগুলো মেনে চলুন।
আরও পড়ুন : কোভিড ভ্যাকসিন: নিষ্ঠুর উপেক্ষা পেরিয়ে শাশ্বত সাধনার গল্প / সায়নদীপ গুপ্ত
অক্সিজেনের সঠিক প্রয়োগ, ভালো ক্রিটিকাল কেয়ার চিকিৎসা, প্রয়োজনে ভেন্টিলেশন, ভেন্টিলেশনে কাজ না হলে extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) ইত্যাদি হল গুরুতর অসুস্থদের বাঁচানোর পথ। এই সবকিছুই সীমিত পরিমাণে আমাদের হাতে আছে। এগুলো ব্যবহার করতে হবে কিন্তু অপব্যবহার করা চলবে না। এরই মধ্যে অনেক জায়গায় হাসপাতালের শয্যা এবং অক্সিজেনের ঘাটতি শুরু হয়েছে। শয্যা অপ্রতুল হওয়ায় উপসর্গহীন বা সামান্য উপসর্গযুক্ত রোগীদের ভর্তি করে রাখা সম্ভব নয়। বাড়িতে কোভিড রোগীকে যত্নে কিন্তু আলাদাভাবে রাখুন। আলাদা ঘর থাকলে সেই ঘরে একা। অক্সিমিটার থাকলে অবশ্যই অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপুন এবং কমতে শুরু করলে স্বাস্থ্য দপ্তরে, চিকিৎসককে বা হাসপাতালে ফোন করে ভর্তি করার চেষ্টা করুন। বেড না পাওয়া পর্যন্ত সময়টুকু বাড়িতে অক্সিজেন দেওয়া উচিত এবং তা তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। এরকম পরিস্থিতি না হলে কোভিড আক্রান্ত উপসর্গহীন প্রিয়জনের নাকে অকারণে অক্সিজেনের নল গুঁজে দেওয়ার দরকার নেই। অদরকারে অক্সিজেন কিনে বাড়িতে জমিয়ে রাখা একধরনের অপরাধই বলা চলে এই মহামারীর সময়।
আরও পড়ুন : রুখে দেওয়ার গল্পেরা / ব্রতেশ
সরকার, হাসপাতাল, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, পুরকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালক সহ সকলকেই নিজেদের দায়িত্ব সৎভাবে পালন করতে হবে। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দশ কিলোমিটার পথ অ্যাম্বুলেন্সে রোগী নিয়ে যেতে পঁচিশ হাজার টাকা দর হাঁকা বা হাসপাতালে বেড দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার চেষ্টা গুরুতর অপরাধ। সব স্তরের কর্মীদের দায়িত্বশীল এবং মানবিক হওয়া প্রয়োজন। নাগরিকদের কর্তব্য নিয়ম মেনে এমনভাবে থাকা যাতে এই দ্রুত বর্ধমান রোগীর সংখ্যাকে আমরা আর বাড়িয়ে না তুলি, কারণ এরপর চাপ সামলাতে না পেরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং বিনা চিকিৎসায় অনেকের প্রাণ যাবে। এই বিষয়ে অবশ্য সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব ছিল প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতাদের। তাঁরা যা দায়িত্ববোধের নিদর্শন রেখেছেন এখন পর্যন্ত, তাতে শ্রদ্ধা বা ভরসার তলানিটুকুও গ্রীষ্মদাহে শুকিয়ে গেছে। এখনই সংশোধনের কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়লে দেশ তাঁদের ক্ষমা করবে না।
........................
[ কভার : অর্পণ দাস ]