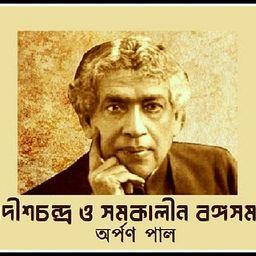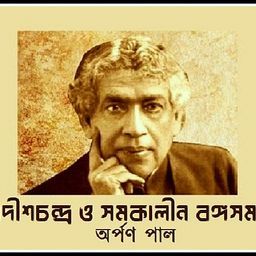জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ (দ্বাদশ পর্ব)
_1366x1366.jpg)
........................
পর্ব ১২। অজন্তায় ভ্রমণ : নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র-নন্দলাল-অসিতকুমার প্রসঙ্গ
ভারতীয় শিল্প এবং লোক-সংস্কৃতির ওপর প্রবল আকর্ষণ বোধ করতেন নিবেদিতা। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার পাশাপাশি এ দেশীয় শিল্পকলার জাগরণে তাঁর ভূমিকার কথা নানা উপলক্ষে প্রকাশ পেয়েছে বহুবার। ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নন্দলাল বসু বা অসিতকুমার হালদার, বা বিদেশিদের আর্নেস্ট হ্যাভেল বা কাকুজো ওকাকুরা— প্রত্যেকেই অনুভব করেছেন নিবেদিতার এই আগ্রহ এবং ভালোবাসাকে। এর প্রকাশ দেখা গিয়েছে ‘মডার্ন রিভিউ’-এর পাতায় প্রকাশিত নিবেদিতার একাধিক প্রবন্ধে। তাছাড়া ওকাকুরা-র ‘আইডিয়ালস অভ দ্য ইস্ট’ বইটি লেখবার কাজেও নিবেদিতার সাহায্য ছিল যথেষ্ট।
ভারত-শিল্পের জাগরণেরই একটা অধ্যায় অজন্তা-শিল্পের প্রচার-কর্মসূচি। যে কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন নিবেদিতা। এই পর্বে সেই আলোচনা।
ভারতের পশ্চিম দিকে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ থেকে একশো কিলোমিটার দূরে প্রায় সাড়ে পাঁচশো মিটার লম্বা এক সারি গুহার নামই অজন্তা। স্থানীয় এক গ্রাম অজিন্ঠা থেকে সহজ বাংলায় এই গুহাকে অজন্তা গুহা বলা হয়ে থাকে। খ্রিস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে গড়ে ওঠা এই গুহাচিত্র এবং ভাস্কর্য বহু বছর ধরেই মানুষের মনে সম্ভ্রম এবং বিস্ময় জাগিয়ে এসেছে। মূলত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত এই গুহাগুলোর ভেতরের দেওয়ালে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানাবিধ পৌরাণিক ঘটনার দৃশ্য, বিশেষ করে বুদ্ধের জীবনের নানা অধ্যায়ের দৃশ্য। ফুটিয়ে তোলা রয়েছে জাতকের ঘটনাকেও।
অজন্তার এই আশ্চর্য ভাস্কর্য এবং অঙ্কনশিল্প সমন্বিত গুহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮১৯ সালে, এক ব্রিটিশ অফিসার জন স্মিথ-এর হাত ধরে। এর পরের কয়েক দশকে আস্তে-আস্তে এই গুহা-ভাস্কর্যের খ্যাতি ছড়ায় এবং উনিশ শতকের আঝামাঝি সময়ে ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তখনই শুরু হয়েছিল এই গুহাগুলোর ভেতরের দেওয়ালে আঁকা ছবির নকল করবার ব্যবস্থা। যাতে ভবিষ্যতে মূল ছবি নষ্ট হলেও সে-সবের কপি অন্তত রক্ষিত থাকে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এক সেনা-অফিসার মেজর রবার্ট গিল (Robert Gill) এই কাজে প্রথম হাত লাগিয়েছিলেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে পরপর দু’বার এই শিল্পকর্মের নকল করে রাখা কপিগুলো আগুন লেগে পুড়ে যায়। প্রথমবার ১৮৬৬ সালে, লন্ডনের ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে রাখা রবার্ট গিল-এর আঁকা তিরিশটা ছবির মধ্যে পঁচিশটা পুড়ে যায়। পরে ১৮৮৫ সালে বম্বের জামশেদজি স্কুল অভ আর্ট-এর অধ্যক্ষ জন গ্রিফিথস সাহেবের তেরো বছর ধরে এঁকে নির্মাণ করা একশোটা ছবি লন্ডনেরই এক মিউজিয়ামে পুড়ে যায়। তবে এখনও সেখানে দেড়শোর বেশি ছবি রয়ে গিয়েছে। অজন্তা-গুহার ওই আশ্চর্য সব চিত্র সম্বন্ধে মানুষের মনে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে এই দুই সাহেবের পরিশ্রমের কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। গ্রিফিথ সাহেবের লেখা ‘দ্য বুদ্ধিস্ট কেভ টেম্পল অভ অজন্তা’ নামে দু-খণ্ডে প্রকাশিত বইকে তো এখন অনেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিরল বই বলে গণ্য করে থাকেন। মাত্র তিন কি চার কপি সন্ধান মেলে অসাধারণ এই বইয়ের।
কিন্তু আরও একবার প্রত্যেক গুহার সমস্ত ছবি নতুন করে কপি করবার প্রয়োজন অনেকের কাছেই মনে হচ্ছিল বারবার। বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষ দিকে সেই কাজে এগিয়ে এলেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ সেই আর্নেস্ট হ্যাভেল সাহেবের বন্ধু ডঃ উইলমট হেরিংহ্যাম (Wilmot Herringham, ১৮৫৫ - ১৯৩৬)-এর স্ত্রী মিসেস ক্রিশ্চিয়ানা হেরিংহ্যাম। ইনি নিজেও খুব ভালো ছবি আঁকতেন। ইনি কলকাতায় আসেন ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে, সঙ্গে ছিলেন মিস ডেভিস নামে আর এক মহিলা। কলকাতায় আসবার পর স্বাভাবিকভাবেই হেরিংহ্যামের সঙ্গে আলাপ হয় নিবেদিতার, এবং তাঁর মাধ্যমে নন্দলাল বসু আর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেও। নিবেদিতারই পরামর্শে মিসেস হেরিংহ্যাম অজন্তার গুহা থেকে ছবি কপি করে আনবার দায়িত্ব দেন নন্দলাল বসু আর তাঁর চেয়ে বছর বয়সি তাঁরই ছাত্র অসিতকুমার হালদারকে। খরচের দায় নিলেন ঠাকুরবাড়ির তিন ভাই—অবনীন্দ্র-সমরেন্দ্র-গগনেন্দ্রনাথ। যাত্রার দিন ঠিক হল ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শীতের এক সন্ধেয়। যদিও প্রথমদিকে নাকি মিসেস হেরিংহ্যাম এই অল্পবয়সী ছেলেদুটির ওপর ঠিক ভরসা করতে পারেননি।
দিন কয়েক পরে একই পথে রওনা দিলেন আরও পাঁচ জন— জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু, নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টিন এবং ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। সেটা ছিল বড়দিনের ছুটি, সুতরাং সকলেই ভ্রমণের আনন্দে উত্তেজিত এবং পুলকিত। আর জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার পরামর্শমতো পরে আনা হয় আর দু-জন ছাত্রকে, বেঙ্কটাপ্পা আর সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁদের নাম। শিল্পীরা ওখানে টানা তিন মাস ছিলেন।
শিল্পীদের টিম দিনের পর দিন কাজ করতে লাগল অজন্তার বিভিন্ন গুহায়। সবাই থাকতেন কাছেই ফরদাপুর নামে একটি গ্রামে। ওই সময়কার অভিজ্ঞতার কিছুটা পাওয়া যায় নন্দলালের জবানিতে:
‘সস্ত্রীক জগদীশ বাবু, সিস্টার আর গণেন কেভ গেলেন দেখতে বড়দিনের ছুটিতে। গলার রুদ্রাক্ষ মালায় হাত দিয়ে ‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ বলতে বলতে টাঙ্গা থেকে নামলেন সিস্টার। কেভে কাজ চালাচ্ছি আমরা তন্ময় হয়ে। বাইরের জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছিল। খাবার সময় বয়ে যেত। এই সব দেখে ওঁরা ভাবলেন, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। জগদীশবাবুর সঙ্গে ছিল ওঁর মগ-বাবুর্চি। সে লেগে গেল রান্না করতে। আমি তখন জাত মানতুম খুব। মুরগী খেতুম না; মুসলমানের হাতে তো নয়ই। লেডি বোস, সিস্টার অনুরোধ করলেন, একসঙ্গে খেতে। তবুও চেষ্টা করতুম, জল আর ভাত বাঁচিয়ে খাওয়ার। ক্রমে সব সয়ে গেল। ভালো লাগে না নিজেদের ঝামেলা নিজেদের বইতে, বললুম সিস্টারকে। সিস্টার বললেন— গণেনকে রাখছি এখানে, তোমাদের তত্ত্বাবধানের জন্যে।’ [ভারতশিল্পী নন্দলাল, ১, ১৬৬ পৃ]
এই সফর সেরে এসে ১৯১১ সালে ‘অজন্তা’ নামে একটা বই প্রকাশ করেছিলেন অসিতকুমার হালদার। পরে নিবেদিতাও ‘দ্য অ্যানশিয়েন্ট অ্যাবে অভ অজন্তা’ নামে একটা বড় প্রবন্ধ লেখেন, সেটা প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে ধারাবাহিকভাবে ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই লেখাটা তাঁর ‘ফুটফলস অভ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি’ বইয়ে সংকলিত হয়। সেখানে কিছু ছবিও ছিল। এখন আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই বইটার একটা সটীক, সচিত্র এবং সম্পাদিত বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।
জগদীশচন্দ্র বা অবলা বসু, এঁদের কেউই এই সফর নিয়ে কিছু লিখেছেন বলে তো নজরে আসে না। তবে এই সফরের পর আর মাত্র দুটো বছর বেঁচেছিলেন নিবেদিতা।
.......................
#Jagadish Chandra Bose #Sister Nivedita #জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ #series #silly পয়েন্ট