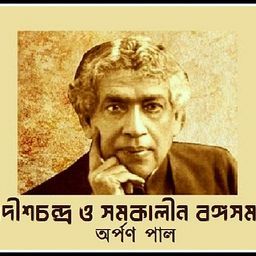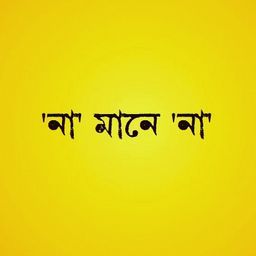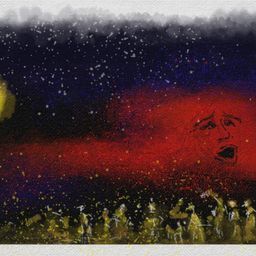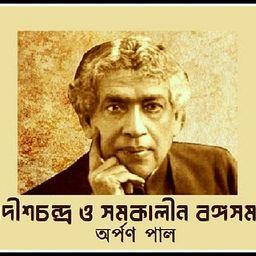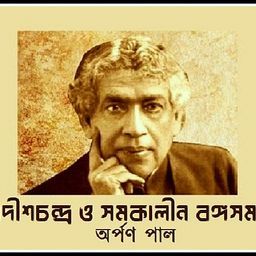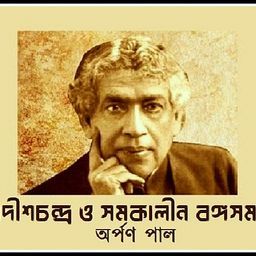জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ (শেষ পর্ব)
_1366x1366.jpg)
........................
শেষ পর্ব। নিবেদিতার শেষ জীবন ও পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্রের নিবেদিতা-স্মরণ
মিসেস সারা বুল তাঁর উইলে জগদীশচন্দ্রের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটা অঙ্কের বরাদ্দ উল্লেখ করে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর সেই খবর জেনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ওলিয়া, উইলের সেই বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে না দিতে হয়, সে জন্য মামলাও করেন। তিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন, ভারতীয় কালাজাদু শিখে সেটা তাঁর মায়ের ওপর প্রয়োগ করেই নিবেদিতা এইভাবে তাঁর মায়ের সম্পত্তি হাত করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন। আর এটা করবেন বলেই তিনি তড়িঘড়ি এ-দেশে এসেছিলেন। তখনকার দিনে সে-দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র এই মামলা-ঘটিত খবর ছাপার পাশাপাশি নানাভাবে ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকেও হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা চালাত, যে-সব খবরে স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হতেন নিবেদিতা। তিনি ঠিক করেন, আর এ দেশে থাকা চলে না। তাই ভারতে ফিরে এলেন ১৯১১-র এপ্রিল মাসে।
পরের আগস্টে খবর পেলেন, মামলায় হার হয় ওলিয়ার, এবং সেই খবরে ভেঙে পড়ে সে ইতিমধ্যে আত্মহত্যাও করে বসেছে। বিষণ্ণ নিবেদিতা, সব মিলিয়ে তখন তাঁর মানসিক অবস্থা এতটাই হতাশাগ্রস্ত যে অনেকে ওই সময়কার তাঁকে দেখে বলেছিলেন তাঁর যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে।
নিবেদিতা নিজেও বুঝতে পারছিলেন, তাঁর এই পৃথিবীতে থাকবার মেয়াদ দ্রুত যেন শেষ হয়ে আসছে। অনেক কাজ এবার গুটিয়ে নেওয়া দরকার। মে মাসে যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে মায়াবতী যাওয়ার কথা হল, নিবেদিতা গেলেন বাগবাজারে মায়ের বাড়ি, মা-কে একবার প্রণাম করে আসতে। কে জানত, ওটাই তাঁর মায়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।
মায়াবতী যাত্রায় নিবেদিতার সঙ্গী হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র, এবং অরবিন্দমোহন বসুও। মায়াবতীর আশ্রমে জগদীশচন্দ্র একদিন বক্তৃতাও দেন।
এই সফর সেরে তাঁরা ফেরেন জুলাইয়ের তিন তারিখ। এরপরেই আবার পরিকল্পনা কড়া হল, পুজোর ছুটিতে যাওয়া হবে দার্জিলিং।
ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন স্বামীজীর মা ভুবনেশ্বরী দেবী এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। নিবেদিতা মানসিকভাবে আরও একটু রিক্ত হয়েছেন। তবু তাঁর মনে আনন্দ, আরও একটা সফর শুরু হতে চলেছে।
তবে যাওয়ার আগের কদিন তাঁর কাটল দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে। সারা বুল-এর একটা ছোট জীবনী লিখলেন ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায়, নিজের আরও কিছু লেখার কাজ সারলেন, জগদীশচন্দ্রের একটা বইয়ের সম্পাদনাও চলল পাশাপাশি। একদিন হাতে পেলেন দীনেশচন্দ্র সেন-এর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বইয়ের দুটো খণ্ড। এই বই লেখবার কাজে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। দেখা করে এলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও। তাঁকে জানিয়ে রাখেন, তিনি যে নাটকটা লিখছেন, সেটা যেন ফিরে এসে গোটা পড়বার সুযোগ পান। সে নাটক তাঁর আর পড়া হয়নি।
২.
দার্জিলিং-এ দিনগুলো কাটছিল ভালোই। এখানে নিবেদিতা উঠেছিলেন দ্বারকানাথ রায়-এর (অবলা বসুর দিদি সরলা রায়ের স্বামী) বাড়ি ‘রায়ভিলা’য়। খাতির-যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছিল না। দিনের বেলায় বেশিরভাগ সময়ই কেটে যায় অতিথিদের সঙ্গে আলাপচারিয়া, তারই মধ্যে সময়সুযোগমতো চলে লেখালিখির কাজ।
এরই মধ্যে একদিন জগদীশচন্দ্র এসে প্রস্তাব দেন, চলুন সান্দাকফু ঘুরে আসা যাক। ওখানে একটা মঠও আছে, গেলে সেটাও দেখা আসা যাবে।
যদিও তখন দার্জিলিং থেকে সান্দাকফু যাওয়া বড় সহজ ছিল না। ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়, সব মিলিয়ে প্রায় দুদিন লাগে শুধু যেতে। তবু নিবেদিতা উৎফুল্ল এই প্রস্তাবে। যাওয়ার সবকিছু বন্দোবস্ত হয়ে গেল।
কিন্তু যাওয়ার দিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন নিবেদিতা। বমি, সেই সঙ্গে জ্বর আর রক্ত-আমাশা। এই অবস্থায় যাওয়া চলে না, তাই বাতিল হল যাওয়া।
ভাগ্যক্রমে তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার। তাঁকেই ডাকা হল। তিনি এসে নিবেদিতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন, জানালেন ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ দিয়ে গেলেন।
অসুস্থ নিবেদিতার বিছানার পাশে বসে থেকে দিনের পর দিন সেবা করে চললেন অবলা বসু। জগদীশচন্দ্র একবার প্রস্তাব দিলেন, কলকাতায় ফিরে গেলে কেমন হয়। কিন্তু এই রুগ্ন আর অসুস্থ মানুষটাকে কলকাতা নেওয়াই তো মুশকিল। ইতিমধ্যে অক্টোবরের সাত তারিখে লেখা হল নিবেদিতার শেষ ইচ্ছেপত্র। তাতে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি বিলিবন্টনের দায়িত্ব তুলে দিলেন বস্টনের বাসিন্দা এবং উকিল ই জী থর্প-এর হাতে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তুলে দেওয়ার কথা হল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে। ওঁরাই এই অর্থ নিয়ে মেয়েদের শিক্ষার কাজে ব্যয় করেন যেন, সেই শর্তই দেওয়া রইল।
অবশেষে এল সেই দিন। অক্টোবরের ১৩ তারিখ। সেদিন শুক্রবার। আগের দিনগুলো ছিল কুয়াশাছন্ন, সেদিনই অলৌকিকভাবে আকাশ একেবারে পরিষ্কার। সকালের নরম আলো এসে পড়ল নিবেদিতার শয্যাপাশে। সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নিবেদিতা। মৃদু গলায় বললেন, ‘দ্য বোট ইজ সিংকিং, বাট আই মাস্ট সি দ্য সানরাইজ।’
আস্তে-আস্তে চোখ বুঝলেন নিবেদিতা। সকাল সাতটার সময় খবর ছড়িয়ে পড়ল দার্জিলিং শহরের দিকে, প্রয়াত হয়েছেন তিনি।
৩.
সব মিলিয়ে দার্জিলিং-এ নিবেদিতা এসেছিলেন সাতবার। জীবনের দুশোর বেশি দিন তিনি এখানে কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে এই শহর শোকে ভেঙে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এখানকার বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, প্রত্যেকেই তাঁর শেষযাত্রায় সামিল হলেন। ওই শহর সেদিন সম্ভবত সবচেয়ে বড় মিছিলটা দেখল।
সেই মিছিলে হাঁটলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শশিভুষণ দত্ত, ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, ইন্দুভূষণ সেন, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বশীশ্বর সেন এরকম বহু মানুষ। বেলা চারতের সময় সেই মিছিল এসে থামল শ্মশানে।
চিতার ওপর নিবেদিতার প্রাণহীন দেহকে সাজিয়ে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে আস ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ মুখাগ্নি করলেন। আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল নিবেদিতার প্রাণহীন দেহ। রয়ে গেলেন অসংখ্য মানুষের স্মৃতিতে।
৪.
নিবেদিতার মৃত্যুর পর জগদীশচন্দ্র কোনো স্মৃতিচারণ লেখেননি কোথাও। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকের কাছেই যে তাঁকে নিয়ে কিছু বলেছেন, তার কোনো নথি মেলে না। একমাত্র নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘And then the book which she was helping me to write is staring me in the face. I have not at present the strength to do anything with it.’
শোকে মানুষ ভেঙে পড়েন, এ স্বাভাবিক। কিন্তু সেই শোকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেও তো অনেকে প্রিয় মানুষকে নিয়ে কিছু লেখেন, বা পরিচিতদের কাছে কখনও মনের আগল খুলে সেই মানুষটিকে নিয়ে দু-চার কথা বলে থাকেন— জগদীশচন্দ্রের বেলায় সেরকম কোনো নজির আমরা পাইনি। নিবেদিতার মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচেছিলেন আরও ছাব্বিশ বছর, এত বড় একটা সময়কালে তিনি কখনও কিচ্ছু লেখেননি। অনেকে এর পেছনে আসল কারণ খোঁজবার চেষ্টা করেন বটে, তবে তাঁর মনের নাগাল পাওয়া আজকের দিনে বোধ হয় এতটা সহজ নয়।
তবু জগদীশচন্দ্র অন্তত পরোক্ষভাবে নিবেদিতার জীবনী লেখবার কাজে সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। লিজেল রেমঁ, যিনি নিবেদিতার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখে পশ্চিমে খ্যাতি পেয়েছেন, তিনি যখন কলকাতায় জগদীশচন্দ্রের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিবেদিতা বিষয়ক কিছু স্মৃতিচারণ সংগ্রহ করে আনবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন জগদীশচন্দ্র জানিয়েছিলেন, নিবেদিতা তাঁকে তাঁর বৈজ্ঞানিক-জীবনের ওঠাপড়ার সময় কতটা সাহায্য করেছিলেন, সে ব্যাপারে অবশ্যই বলবেন। কিন্তু রেমঁ-কে এই চিঠি লেখবার মাত্র তিন মাস পরেই প্রয়াত হন জগদীশচন্দ্র, ফলে তাঁর সে স্মৃতিচারণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে আমাদের।
তবু জগদীশচন্দ্রের প্রয়াণের পর তাঁর কাছে থাকা নিবেদিতার চিঠি বা বেশ কয়েকটা ডায়েরি— বেশ কিছু উপাদান লিজেল রেমঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন অবলা বসু। সে-সবের শেষ পর্যন্ত কী গতি হল, তা আর জানা যায় না। এতদিন পরে সে-সমস্ত নথিপত্র না পাওয়ার সম্ভাবনাই কম। পাওয়া গেলে, এঁদের মধ্যের সম্পর্কের আরও কিছু অজানা দিক আমাদের কাছে উন্মোচিত হত নিঃসন্দেহে।
এই দুই মহামানব যে জীবনের বেশ কিছুটা সময় একত্রিত হয়েছিলেন, পরস্পরে মিলে কিছু কাজ অন্তত একত্রে করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন— এটাই এখন আমাদের সান্ত্বনা। স্বামীজীর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েও নিবেদিতা যেভাবে এক বিজ্ঞানীর জীবন এবং কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। তাঁর অকালমৃত্যু তাদের আরও অনেক যৌথ-কাজের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর যদি কেউ করে থাকেন, তিনি নিবেদিতা— এ আমরা অকপটে বলতে পারি।
…………………………………
সমাপ্ত
#Jagadish Chandra Bose #Sister Nivedita #জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ #series #silly পয়েন্ট