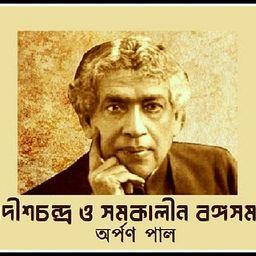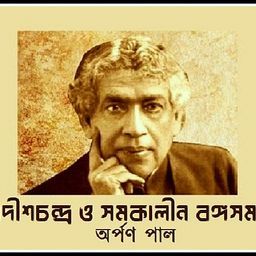জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ (ত্রয়োদশ পর্ব)
_1366x1366_1366x1366.jpg)
........................
পর্ব ১২। অজন্তায় ভ্রমণ : নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র-নন্দলাল-অসিতকুমার প্রসঙ্গ
মোটামুটি ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি থেকে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন গতি পেতে শুরু করে, সৌজন্যে বঙ্গভঙ্গ।
লর্ড কার্জন আর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার-এর পরিকল্পনা-মতো ওই বছরের জুলাই মাসের ষোল তারিখে এই সরকারী নির্দেশ ঘোষিত হয়। পূর্ববঙ্গ আর আসাম প্রদেশকে বাকি বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা আলাদা প্রদেশ হিসেবে নির্ধারিত হয়। যদিও প্রশাসনিক দিক থেকে সুবিধে হওয়াই এই ঘোষণার পেছনে আসল কারণ বলে দেখানো হয়েছিল, তবু বাংলার কোটি কোটি মানুষ এই ঘটনা বাঙালি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করবার একটা চক্রান্ত হিসেবেই দেখেছিলেন।
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি গর্জন ওঠে এই কলকাতা শহর থেকেই। এরকিছু আগে এই লর্ড কার্জনের এক মন্তব্যের প্রতিবাদে অমৃতবাজার পত্রিকায় বেনামে একটা চিঠি প্রকাশ করেছিলেন নিবেদিতা, যে ঘটনা বাংলায় বেশ আলোড়ন তুলেছিল। আর এবার যখন সেই কার্জনই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করবার এই প্রচেষ্টায় লেগে পড়েছেন বলে প্রচারিত হল, তখন নিবেদিতাও সেই ঘটনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদে সামিল হবেন, এ সহজেই অনুমান করা চলে। এই ঘোষণার আগে মে এবং জুন মাস তিনি বসু দম্পতির সঙ্গে কাটিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরেই আগস্ট মাসে নিবেদিতা ফেডারেশন হল তৈরির প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। এর আগে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালির উদ্যোগে টাউন হলের সভায় বিক্ষোভকারী এবং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের একটা মিলন-সভা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিয়েছিলেন ‘অখণ্ড বঙ্গ ভবন’ তৈরির। সেটাকে সমর্থন জানান জগদীশচন্দ্র বা নিবেদিতা। পরে নিবেদিতাই এর নাম পালটে ‘মিলন মন্দির’ রাখবার কথা বলেন, সেটাই সকলে মেনে নিয়েছিলেন।
এরপর আসে রাখিবন্ধনের দিন। সেই বছরের অক্টোবরের ষোল তারিখে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলকাতা জুড়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। সেই দিন বিকেল তিনটেয় গুরুতর অসুস্থ হয়েও আনন্দমোহন বসু চেয়ারে আসীন হয়ে সার্কুলার রোডের পাশের এক পার্কের সভায় এসে এই মিলন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিন ওই সভায় ছিলেন জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র বা নীলরতন সরকারের মতো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
ওই বছরের অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হল, আর ডিসেম্বরে কাশীতে অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন, তাতে যোগ দিলেন নিবেদিতা। সেখানে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে-র সঙ্গে।
২.
বিপ্লবী আন্দোলন গতি পেতে লাগল ১৯০৬/৭ সাল থেকে। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বা ভূপেন্দ্র দত্ত-র কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন গতি পায়। নিবেদিতা নিজেও সক্রিয়ভাবে বেশ কিছুটা যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যদিও তাঁর এক জীবনীকার তাঁর এই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াকে সরাসরি মেনে নিতে পারেননি। নিবেদিতা যে বহু বিপ্লবীর সঙ্গেই ভেতরে-ভেতরে যোগাযোগ রাখতেন বা তাঁদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, এ তথ্য আজ আর গোপন নয়। তখনই তিনি ব্রিটিশ সরকারের বেশ কিছু কর্তাব্যক্তিদের নজরে পড়ে গিয়েছিলেন।
১৯০৭-এর জুন মাসের দিকে তাঁর ওপর পুলিশি সন্দেহ বেশ তীব্র হয়ে ওঠে, আর তখন তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে তিনি স্থির করেন, এই দেশে আর বেশিদিন থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। পুলিশ তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে, যে-কোনো সময় তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন। যদিও নিবেদিতা- জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর বইয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে নিবেদিতার বিদেশযাত্রার প্রস্তুতি চলছিল বেশ কিছু আগে থেকেই, আর এর সঙ্গে তাঁর গ্রেপ্তার-সম্ভাবনার কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য সে-সময়ে রাজনৈতিক আবহাওয়া বা পরিস্থিতি এমনই ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক মনে হতে পারে এমন যে কাউকেই সরকারের পুলিশবাহিনী চাইলেই গ্রেপ্তার করতে পারত। তাই আমরা দেখি, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনি কলকাতা ছাড়লেন, পৌঁছলেন ইংল্যান্ডে। দীর্ঘ দিন পর পেলেন পরিবারের সান্নিধ্য। আর এর কয়েক মাস পর, যখন বসু-দম্পতিও লন্ডনে আসেন, তখন তাঁদের সঙ্গে অনেকদিন পর আবার মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটল। নিবেদিতার ক্ল্যাপহ্যামের বাড়িতে এলেন বসু-দম্পতি, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল নিবেদিতার মায়েরও।
পরের বছর, ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা পৌঁছলেন আমেরিকায়। ওই মাসেই আমেরিকায় যান জগদীশচন্দ্রও। সেখানকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল বক্তৃতার জন্য। নিবেদিতা অবশ্য পরের বছর জানুয়ারিতেই আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে। জানুয়ারির ২৬ তারিখে মৃত্যু হয় মায়ের। তাঁকে সম্পূর্ণ হিন্দু প্রথায় দাহ করা হয়, তাঁর নিজেরও শেষ ইচ্ছে ছিল এটাই।
অন্যদিকে জগদীশচন্দ্ররাও ইংল্যান্ডে ফেরেন ১৯০৯-এর মার্চ মাসে। এরপর কয়েক মাস তাঁরা ঘুরে বেড়ান ইউরোপের নানা শহরে। বেশ কিছু সফরে সঙ্গী হয়েছিলেন নিবেদিতা, আমেরিকা থেকে এসেছিলেন সারা বুলও। সবাই মিলে অনেক বছর পর আবার একত্র হন, দিনগুলো কাটতে থাকে চমৎকারভাবে।
কিন্তু ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও কিছুটা সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে থাকায় নিবেদিতা স্থির করেন যে এখানে আর থাকা চলে না। সেইমতো ১৯০৯-এর জুলাইয়ের মাঝামাঝি নিবেদিতা চলে এলেন ভারতে, বোম্বে শহরে জাহাজ থেকে নেমে তিনি বেশভূষায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েই (অনেকে বলেন পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই) ট্রেনে চেপে চলে আসেন কলকাতায়। এই সফরে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বসু দম্পতিও।
এরপর নিবেদিতার দিনগুলো কাটতে থাকে নানান কর্মব্যস্ততায়, এবং ওই ১৯০৯ সালের শেষ দিকে তিনি, জগদীশচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন মিলে যাত্রা করেন অজন্তার উদ্দেশ্যে। এই অজন্তা পর্বের কথা আমরা আগের অধ্যায়ে বলেছিলাম।
৩.
ইতিমধ্যে আলিপুর বোমা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, শুরু করেছেন দুটো পত্রিকার সম্পাদনা। তবে কয়েক মাস পর যখন তাঁর আবার গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখন নিবেদিতাই উদ্যোগ নিয়ে অরবিন্দকে পাঠিয়ে দেন চন্দননগরে। এবং তাঁর পত্রিকা ‘কর্মযোগিন’-এর সম্পাদনা-ভার তুলে নেন নিজের কাঁধে। পরে অরবিন্দ চলে যান পন্ডিচেরিতে, সেখানে আশ্রম-জীবন শুরু করেন এবং ঋষি অরবিন্দ হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করেন।
ইতিমধ্যে নিবেদিতার লেখালিখি এবং অন্যান্য কাজকর্মও চলছিল স্বাভাবিক গতিতেই। অন্যদিকে জগদীশচন্দ্রের জন্য একটা নিজস্ব ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরি তৈরির ব্যবস্থা করে দিতেও উদ্যোগী হন, চিঠি লেখেন বরোদার গায়কোয়াড়কে। যদিও সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি, নিজস্ব গবেষণাগার পেতে জগদীশচন্দ্রকে অপেক্ষা করতে হয় আরও প্রায় সাত বছর। তাও সে কাজটা হতে পেরেছিল তাঁর নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ এবং দানের টাকায়।
এই ১৯১০-এ দুটো সফরে নিবেদিতার সঙ্গী হতে পেরেছিলেন বসু দম্পতি। গরমের ছুটিতে মে মাসের ২৫ তারিখ থেকে টানা ৪৮ দিন ধরে তাঁরা একত্রে ভ্রমণ করেন কেদারবদ্রি। এই সফরের বেশিরভাগ দিনই তাঁদের কেটেছিল হাঁটাহাঁটি করেই। জগদীশচন্দ্র সুস্থ থাকলেও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অবলা বসু। প্রসঙ্গত, এই সফর থেকে ফিরেই জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সেই লেখা ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে’। এরপর অক্টোবরে পুজোর ছুটিতে বসু-দম্পতি যাত্রা করেন দার্জিলিং-এ, সঙ্গী হন নিবেদিতা। সে-যাত্রায় নিবেদিতাকে হঠাৎ আবার ফিরে আসতে হয় সারা বুল-এর অসুস্থতার খবরে। তড়িঘড়ি রওনা দেন আমেরিকায়। সারা বুল-এর শয্যাপাশে উপস্থিত হন নভেম্বরে। যদিও মিসেস বুল বেশিদিন বাঁচেননি, পরের বছর জানুয়ারির ১৪ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিজের উইলে জগদীশচন্দ্রের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা নিয়ে (দুটো পর্যায়ে প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার বরাদ্দ করেছিলেন যার অর্থমূল্য আজকের দিনে বহু কোটি টাকা) এই সারা বুল-এর মেয়ে ওলিয়া-র সঙ্গে কিছু পরে অবাঞ্ছিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয় নিবেদিতাকে, তবে সে আলোচনা পরের পর্বে।
১৩তম পর্ব সমাপ্ত।