মৃত্যু ও রবীন্দ্রনাথ

“যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হত”, ‘আত্মপরিচয়’-এ বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক নিমেষে জীবনের অপচয়ধর্ম ও মৃত্যুর অনিবার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের মনে। কবির অফুরান প্রাণশক্তির কথা মুখে মুখে ফেরে মানুষের, আর মৃত্যুকেও যে তিনি জীবনের সুপ্তি হিসেবে দেখেছিলেন, সে আমরা অনেকটা মোহাবিষ্টের মতো দেখি, কোনও মহামানবকে প্রত্যক্ষ করার ভঙ্গিতে। কিন্তু ‘মিথ’ ভেঙে পাঠে একটু মন দিলেই দেখা যাবে, জীবনে দীর্ঘ সময়জুড়ে একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যুশোক বয়ে বেড়ানো, এবং প্রায় সারাজীবন ধরেই তাঁর সৃজনচিন্তার বিপরীতে এই সমাজের মরণশীল স্থবিরতাকে দেখার যন্ত্রণা সহ্য করে চলা এই মানুষটি আমাদের মতোই শোকার্ত হয়েছেন, বিব্রত হয়েছেন পদে পদে। কিন্তু তাঁর অসাধারণত্ব মৃত্যুর সামনে অটল তিতিক্ষায়; তফাৎ গড়ে দেয় ওটুকুই। সাধারণ মানুষ যখন মৃত্যু, পরাজয়ের মতো ঘটনাকে সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করছে জীবনে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই চালনা করছেন জীবনীশক্তি রূপে। যেখানে এতদিনের সাজানো কল্পনার, মনুষ্যসৃষ্ট সত্যের মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়া, রবীন্দ্রনাথ সেখানেই দেখছেন কোনও এক কসমিক ডিজাইন, প্রকৃতির সত্যের ধ্রুবপদ। আমরা যেখানে দেখছি আগত অনর্থ, তিনি সেখানেই দেখছেন দূরবর্তী সার্থকতা।
হয়তো তাঁর এমন অবিশ্বাস্য জীবনবোধ তৈরি হয়েছিল মৃত্যুকে ঘিরে, ব্যক্তিগত পরিসরের গভীর অভিঘাত থেকেই। ১৯০২ সনে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর দীনেশচন্দ্র সেনকে চিঠিতে তাঁর আদরের 'ছুটি'-কে নিয়ে লিখছেন, "যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যু দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন।" (১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯/ ‘চিঠিপত্র’ ১, পৃষ্ঠা ১০৫) ওই একই দিনে সত্যরঞ্জন বসুকে লেখা আরেকটি চিঠিতে পাচ্ছি, "ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না --- তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।" (‘চিঠিপত্র’ ১, পৃষ্ঠা ১০৫) ক'দিনের হেরফেরে মোহিত সেনকে ঈশ্বর সম্বন্ধে আবারও বলছেন, "তিনি আমাকে আমার শিক্ষালয়ের এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিলেন।" (অগ্রহায়ণ, ১৩০৯/ ‘চিঠিপত্র’ ১, পৃষ্ঠা ১০৭)।
এই একই পূর্ণতার আভাস পাওয়া যায় লেডি অবলা বসুকে লেখা চিঠিতে, পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু প্রসঙ্গে --- "অল্প দিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে-ব্যাপারটা কল্পনায় নিতান্তই দারুণ এবং অসঙ্গত বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমন ভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই।" (এপ্রিল, ১৯০৮/ ‘চিঠিপত্র’ ৬, পৃষ্ঠা ৯০) প্রথমত, উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত ‘বিপ্লব’ শব্দটির শিকড় খুঁজতে খুঁজতে চলে যাওয়া যায় সংস্কৃতে, যেখানে তার একটি অর্থ "শোক"; ইংরাজি ‘misery’, ‘distress’, ‘trouble’, ‘disaster’ ইত্যাদি দেখলে আরও স্পষ্ট হয় ধারণা। (সূত্র: Monier Williams’ Sanskrit-English Dictionary) কাজেই পুত্রশোকের প্রেক্ষিতে সংস্কৃত-মূলের "বিপ্লব" ব্যবহার করা নিতান্তই উদাসীন বা উদ্দেশ্যহীন প্রয়োগ নয় বলেই মনে হয়। প্রাত্যহিক ব্যবহারে "বিপ্লব"-এর তুলনামূলক পরিচিত যে অর্থটি নিয়ে আমরা কাজ করি, ‘revolution’ -- তার মধ্যে একটা 'হয়ে-ওঠা'র দর্শন কাজ করে – এতদিন যা ছিল, তা থেকে উন্নীত হওয়া। মৃত্যুজনিত "বিপ্লব" (শোক)-কে নিজের জীবনের সমগ্রে স্থান দিয়ে নিজেরই উত্তরণের অস্ত্র করে তোলা বৈপ্লবিক (revolutionary) নয় কি? যে কারণে নীতুর মৃত্যুতে মীরাদেবীকে কবি লিখতে পারেন, “যে রাত্রে শমী গিয়েছিল, সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম, বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা শুনলুম, তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয় – নইলে ভালোবাসা এখনও টিঁকে থাকে কেন?” (সৈয়দ মুজতবা আলী, ‘মৃত্যু’)।
দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যের (এবং বিশেষত ভারতীয়) জীবনদর্শনে যে একটি হৃদস্পন্দন-সুলভ ছন্দ আছে, যা এক মুহূর্তে কেন্দ্রানুগ (অন্তর্মুখী, microcosmic) এবং পরমুহূর্তেই কেন্দ্রাতিগ (বিশ্বমুখী, macrocosmic), তা রবীন্দ্রনাথের এই যাপনের মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রাচ্যদর্শনের যে পথ তিতিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা ব্যক্তিমানুষের শোককে, অনিশ্চয়তাকে জয় করে জীবনের একটা নৈর্ব্যক্তিক অথচ সংবেদী বার্ডস-আই-ভিউ নেওয়ার কথা বলে, রবীন্দ্রনাথ সেই উপপাদ্যেরই 'এক্সট্রা'। জীবনের তাৎক্ষণিকতায় তিনি আঘাত পান, ভেঙে পড়েন; কিন্তু সেই যে আঘাতের জারণ, তা পরক্ষণেই প্রাণের স্ফুরণ হয়ে জীবনের সামগ্রিকতায় ধরা দেয়।
লক্ষণীয় এটুকুই। স্ত্রী-সন্তান-পরিজনের মৃত্যু তাঁর 'ছোট আমি'-কে বিলক্ষণ পোড়ায়; উদাসীন সে কোনও অর্থেই নয়। কিন্তু যে 'বড়-আমি' কেন্দ্রাতিগ হয়ে ছুটছে বহির্বিশ্বে, তার কাছে এই মৃত্যু পাথেয়, শিক্ষণীয়। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঈশ্বর, তাঁর জীবনদেবতা সাধারণ জনচেতনার সাকার ঈশ্বরের মতো পূজাপ্রার্থী নন। তিনি একাক্ষর; তিনি পণ করে বসে নেই যে তুষ্ট হলে তিনি সুখ, এবং রুষ্ট হলে দুঃখ দেবেন আমাদের। বস্তুত, তিনি অরূপ; জীবনচারণে তাঁর পথের একপাশে জমা হচ্ছে প্রাপ্তি, অন্যপাশে অপ্রাপ্তি; এক হাত তাঁর মুঠো করা, অন্য হাত আলগা। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে গেলে দেখা যাবে, কাল-কে সেখানে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে দুইভাবে। একদিকে সে আমাদের ক্ষয়মান আয়ুষ্কাল যা প্রতিদিন বিনষ্ট হচ্ছে; আবার অন্যদিকে সে-ই “অবিচ্ছিন্ন প্রবাহস্বরূপ অক্ষর কাল (everlasting time)” (গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষ সম্পাদিত ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’, ৯ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪১১)। এই দুয়েরই তুল্যমূল্য বিচারে আয়ুষ্কালব্যাপী সুখ-দুঃখ, বেদনাতুর অভিজ্ঞতা সবই পূর্ণতায়, অনন্তে আশ্রয় পায় রবীন্দ্রনাথের চোখে।
সে জন্যই 'আত্মপরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ যাকে বারবার "জীবনের সমগ্র" বলছেন, সে নানাভাবেই প্রকৃতির অন্তঃস্থ সেই প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যেই প্রাণপ্রবাহের অন্তর্গত জীবন, এমনকি মৃত্যুও; সুখ, এবং দুঃখও। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায় ডিলান টমাসের কবিতার প্রথম তিনটি পংক্তি, “The force that through the green fuse drives the flower/ Drives my green age; that blasts the roots of trees/ Is my destroyer”! রবীন্দ্রমননে সবকিছু পর্যবসিত হচ্ছে এক শক্তিতে, যা জন্মমৃত্যুরহিত শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্; সে জন্ম ও মৃত্যুর ধারক, এবং সমস্ত বৈপরীত্যের এক ধরণের মেল্টিং পট – “হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। ... নৃত্য করো, হে উন্মাদ নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়।” (‘আত্মপরিচয়’, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭) কবি জন ডানের "One short sleep past, we wake eternally"-এর মতোই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর শেষ ধাপ জাগরণ। নাহলে কোন অদ্ভুত প্রাকৃতিক পোয়েটিক জাস্টিসের কথায় কেউ লিখতে পারেন, "শ্রাবণ রাতে অঝোর-ধারে উদাস করে কাঁদাও যারে/ আবার তারে ফিরিয়ে আনো ফুল ফোটানো ফাগুন রাতে" (‘গীতবিতান’/ পূজা পর্যায়)!
ভাবীকালের পটেও এমন মানুষকে বিস্মৃত হওয়া যে প্রায় অসম্ভব, বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মৃত্যুকেও জীবনের জয়গান করে তোলা এই মানুষটিকে আমরা কি অনন্তপ্রাণ করে রাখতে পেরেছি আমাদের চর্চায়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে গ্রহণে মৃত্যুতে ঔপনিষদিক ‘আনন্দ’ সঞ্চার করেছিলেন, আমরা অধিকাংশই আমাদের অসংলগ্ন, দূরদৃষ্টিহীন গ্রহণে আসলে তাঁর ‘মৃত্যু’কেই উদযাপন করেছি বারবার। আমরা যতবার রবীন্দ্রসংগীত গাইতে যাওয়ার আগে, বা রবীন্দ্রকবিতা পাঠ করার আগে তাঁর কথাগুলো আরেকবার অনুধাবন না করে জামাকাপড়ের রঙ মেলানোর দিকে বা খোঁপার ফুলের দিকে বেশি নজর দিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সেখানেই। যতবার তাঁর শান্তিনিকেতনে আমরা পাঁচিল তুলে বলে দিয়েছি "এটুকু রবীন্দ্রনাথের", ততবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যতবার আমরা আমাদের সন্তানদের 'শিশু' পড়িয়েছি প্রতিযোগিতায় প্রাইজ আনার জন্য, যতবার আমরা আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে প্রসাধনীর মতো রবীন্দ্রনাথের ছবি দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছি, যতবার আমরা "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে" কেবলমাত্র স্মরণসভার দিকেই ‘ধেয়েছি’, যতবার আমরা আলো-আঁধারি প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রগান শুনতে শুনতে বেসুরে, বেতালে জোরে জোরে মাথা নেড়ে নিজের সঙ্গে তাঁর সখ্য প্রতিষ্ঠা করেছি সমাজে মান্যতা পাওয়ার আশায় --- রবীন্দ্রনাথ ততবার ব্যর্থ, গো-হারা এক মানুষ।
এসব কোনোকিছুই দৃষ্টিকটু লাগতো না যদি এর মধ্যে সামান্য 'যাপন' থাকতো 'উদযাপন'-এর বদলে। আসলে উজ্জ্বলতম বিভারও বিড়ম্বনা অনেক। প্রয়োজনে সে অন্তরীণ হতে পারে না; বরাবরই সে দীপ্যমান নক্ষত্র। সে যতই কথা বলুক সমগ্রের, ‘আইকন’ খোঁজা মানুষ তাকে একক ভাবেই দেখে। তাই মাটির দিকে, পৃথিবীর দিকে নুয়ে পড়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেও আমরা তাঁকে “পূজার ছলে” ভুলে থাকাই শ্রেয় মনে করি। ভরসা এটুকুই, প্রকৃতির এই সাম্যের নিয়ম শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্য নয়, সবার জন্যই। তাই আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বহিরঙ্গে তাঁর মৃত্যু প্রতিপদে প্রকট হয়ে উঠলেও, অন্তরে নিশ্চয়ই কোথাও, এর অন্য প্রান্তে তিনি জেগে উঠছেন অনেকের মাঝে।
….……………………..
[মূল ছবি : প্রণবেশ মাইতি]






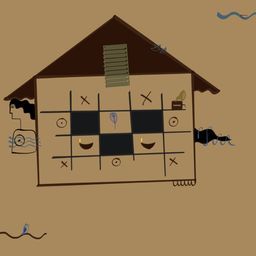
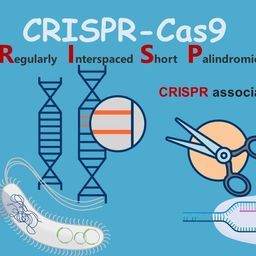

অভয়শঙ্খ মন্ডল
এই বিরাট বিশ্ব জুড়ে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে পরিপূর্ণতা বর্তমান, মৃত্যুকে তিনি সেই পূর্ণতার সমার্থক হিসেবেই দেখেছেন। মৃত্যু মাধ্যমে যে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ সাধিত হয়, সেই অনুপস্থিতিতেই আরো নিবিড় ভাবে প্রিয়জনকে খুঁজে পায় মানুষ। অনুপস্থিতি, উপস্থিতিকে যেন প্রত্যয়িত করে হাজির করে। দৈনন্দিনতার বাইরে তার যে মূল্য সেই মূল্যেই মানুষকে হাজির করে। রবীন্দ্রনাথ প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ছিলেন বলেই, মৃত্যুকে এত গভীর উপলব্ধিতে ধরতে পেরেছেন। আপনার লেখাটি আরও একবার সে কথা মনে পড়িয়ে দিল। ধন্যবাদ। ভালো থাকুন।