স্মৃতি ও বোধশক্তির মানচিত্র
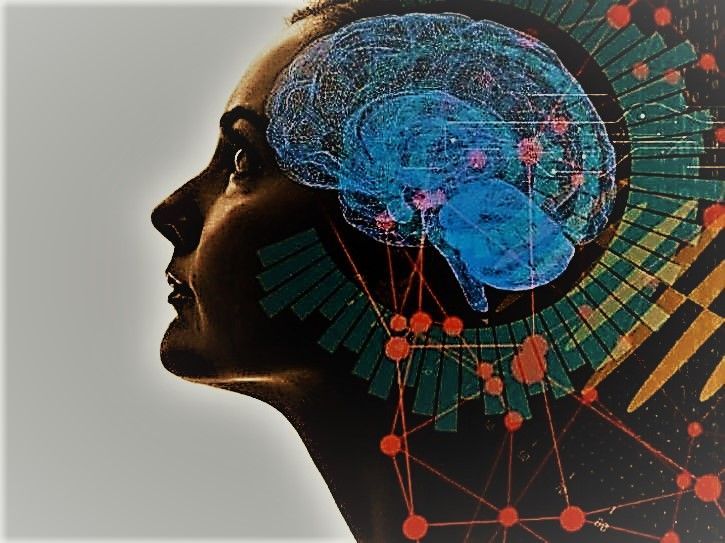
নরওয়ের ওয়েস্ট কোস্টে একটি দ্বীপের ছোট্ট এক জনপদ, নাম ফস্নেভো। আজন্ম সেখানেই শৈশব কেটেছে মে-ব্রিট মোজার নামের মেয়েটির। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সে সবার ছোটো, বাবা ছিলেন কাঠের মিস্ত্রি আর মা দেখাশোনা করতেন বাড়ির লাগোয়া ফার্মহাউসের। দিন রাত তাঁরা কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। বাবা মায়ের কাছ থেকে মে-ব্রিট পেয়েছিল পশু পাখিদের প্রতি দরদী হওয়ার শিক্ষা, আর জেনেছিল কাজের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান মেলে। এভাবেই ওই অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে অসম্ভব কৌতূহলী আর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বেড়ে ওঠে মে-ব্রিট।
বুদ্ধিমতী হলেও স্কুলের লেখাপড়ায় খুব বেশি মনোযোগ নেই সে মেয়ের। পড়াশোনার করার চেয়ে তার বেশি ভালো লাগত মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে; পোকামাকড় বা পাখিদের ওড়া কিংবা শামুকরা কী খায় – এই সব একদৃষ্টে হাঁ করে দেখতে। মা শেষে বোঝালেন, ভালো করে পড়াশোনা না করলে, স্কুলের পরে সোজা বিয়ে হয়ে যাবে; ব্যাস, ওখানেই জীবন শেষ! মায়ের এই কথা খুব আতঙ্কিত করে তুলল মে-ব্রিটকে। লেখাপড়ায় মনোযোগ বাড়ল তার। ছোট্ট মে-ব্রিটকে রূপকথার গল্প পড়ে শোনানোর সময়ে মা বেশি করে বলতেন সেইসব কথা, যা আশা আর বিশ্বাস সঞ্চারিত করে, স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। মে-ব্রিটের মনেও হয়তো সেভাবেই বাসা বেঁধেছিল নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন!
শুধু সে স্বপ্ন দেখাই নয়, তাকে সফল করার দিকেও এগোলেন যুবতী মে-ব্রিট। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি নিয়ে ভর্তি হলেন, সঙ্গে নিলেন গণিত ও নিউরো-বায়োলজি। সেখানে পরিচয় হল সহপাঠী এডোয়ার্ডের সঙ্গে। দুজনেরই ইচ্ছে ব্রেন নিয়ে উচ্চশিক্ষা আর গবেষণার। পিএইচডি গবেষণা চলাকালীনই দুটি হৃদয় বাঁধা পড়ল, সংসার ভরিয়ে এল দুই কন্যা সন্তান। তাদের সামলে গবেষণা চালানোর কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, মে-ব্রিট নিজেই বলেছেন সে কথা – “ছোটো দুটি বাচ্চা নিয়ে অসুবিধা তো ছিলই। তখন বুকের দুধ খাওয়াতে হত। তাই ল্যাবে নিয়ে আসতাম ওদের। কোনো সেমিনারে গেলে সেখানেও নিয়ে যেতাম”।

দুই সন্তানসহ মে-ব্রিট, পিএইচডি সম্পূর্ণ করার মাস ছয়েক আগে
পিএইচডি শেষ হতে না হতেই পোস্ট-ডক্টর্যাল গবেষণার কাজ করার জন্য মে-ব্রিট আর এডোয়ার্ড ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনে বিশিষ্ট নিউরো-সায়েন্টিস্ট জন ও’কিফ-এর গবেষণাগারে সুযোগ পেয়ে গেলেন। এই জন ও’কিফ সত্তর দশকের শুরুর দিকে ইঁদুরের ব্রেনের ‘হিপ্পোক্যাম্পাস’ অংশে এক বিশেষ ধরনের নিউরনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন, যাদের নাম দিয়েছেন ‘প্লেস সেল’। ও’কিফের ল্যাবরেটরিতে কয়েক মাস কাজ করার মধ্যেই তাঁদের অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বার্তা এল নরওয়ের ‘ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’ থেকে। সেখানে তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে সহকারী অধ্যাপক পদের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন। ও’কিফের ল্যাবরেটরি ছেড়ে কী তাঁরা ফিরে যাবেন ট্রন্ডহেইমের মতো ছোটো শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে? সেখানে যে গবেষণার সুযোগ নেই সেভাবে! আবার দুজনে একই প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন ভাবে গবেষণা করার সুযোগ চট করে কোথাও পাওয়া যায় না। অগত্যা দেশেই ফিরে এলেন মোসের দম্পতী। কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না মোটেই। তখনও ভালো করে হাঁটতে না-শেখা দুটি শিশু। সেখানে একদম শূন্য থেকে শুরু করে নিজেদের ল্যাবরেটরি গড়ে তুলতে হয়েছে। গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় ‘অ্যানিম্যাল হাউস’ তৈরি করা বা ‘ফান্ডিং-এজিন্সি’ থেকে গ্রান্ট নিয়ে আসা। দুজনের অসম্ভব মনের জোর আর হার না মানা মনোভাব এবং কাজের প্রতি গভীর আকুতি সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে।
সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে শুরু করে গবেষণাগার কিংবা কফি খাওয়া থেকে বাড়ি ফিরে আসার রাস্তা তাঁদের আলোচনায় জুড়ে থাকে কেবল ব্রেনকোশের কথা। ব্রেনের অন্দরমহলে কোথায় থাকে ‘মেমোরি-সেল’ (স্মৃতিকোশ)? তারই নিবিড় অনুসন্ধান চালায় গবেষণাগারে মে-ব্রিট ও এডোয়ার্ড। ব্রেনের অন্দরমহলে স্মৃতি ধরে রাখার যে জটিল কার্যকলাপ চলে, মূলত সেই রহস্য উদ্ধার করার জন্যে নিরন্তর গবেষণা করেছেন এই দম্পতি। পরবর্তীতে মে-ব্রিট সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘সেন্টার ফর দ্য বায়োলজি অফ মেমোরি’ এবং এক দশকের মধ্যে ‘সেন্টার ফর নিউর্যাল কম্পিউটেশন’-এর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন।
মে-ব্রিট এর কাজের প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে, মগজ বা ব্রেন সম্পর্কে দু-চারটে প্রয়োজনীয় কথা জেনে নিলে মোসের দম্পতির গবেষণার বিষয় কিছুটা বুঝতে সুবিধা হবে। স্নায়ুকোশের (নিউরন) জাল বিছিয়ে রাখা আছে আমাদের মগজ মুলুকে। নিউরনের সংখ্যাটা প্রায় এক কোটির মতন। শুধু কী তাই? এক একটি নিউরনের মধ্যে আবার প্রায় এক হাজার থেকে এক লক্ষ সংযোগ সূত্র থাকে। আর এইসব সংযোগ সূত্রগুলির মধ্যে দিয়ে তড়িৎ সংবহন প্রবাহ আদান প্রদান হয় নিউরনগুলির মধ্যে। ব্রেনের যাবতীয় কার্যকলাপ চলে নিউরনের ওই বিপুল বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে। এছাড়াও নানান প্রাণরাসায়নিক পদার্থ জড়িত থাকে বিভিন্ন মগজীয় কাজে – দেখা, পেশি সঞ্চালন, শ্বাস ক্রিয়া, কথা বলা বা শোনার ক্ষমতা। এমনকি ভাবনা, চিন্তা, বোধ, মনন, অনুভূতি, চিন্তাশক্তি, মেধা, বুদ্ধি-বিবেচনা, স্মৃতি কিংবা বিশ্লেষণী ক্ষমতা – এইসব কিছুর ক্রিয়াকলাপের পেছনে আছে ব্রেনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

গবেষণাগারে কর্মরত মে-ব্রিট মোসের
জন মাইকেল ও’কিফ ব্রেনকোশের মধ্যে ‘পজিশনিং সিস্টেম’ ব্যাপারটি প্রথম আবিষ্কার করেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে ও’কিফ ওই আবিষ্কৃত বিশেষ ধরনের নার্ভকোশগুলির নাম দেন ‘প্লেস-সেল’। এই আবিষ্কারের তিন দশক পরে, ২০০৫ সাল নাগাদ মোসের দম্পতি খুঁজে পেলেন অন্য একধরনের ব্রেনকোশ, যারা আমাদের অবস্থান চেনাতে সাহায্য করে। মানে, ওই কোশগুলি আমাদের চিনতে সাহায্য করে, ঠিক কোথায় আমরা রয়েছি। কিংবা কতটা দূর বা কোন দিকে গেলে আমরা আমাদের ঠিকানায় পৌঁছাতে পারব? এই দিগনির্দেশ চেনানোর পেছনে কাজ করে – সেইরকম বিশেষ এক ধরনের নার্ভ-সেলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন মে-ব্রিট আর এডোয়ার্ড। নাম দিলেন ‘গ্রিড-সেল’। মানুষ ছাড়াও ইঁদুর, বাদুড়, বাঁদর ইত্যাদি অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও গ্রিডসেল আছে, যা তাদের নেভিগেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। ‘প্লেস-সেল’ এবং ‘গ্রিড-সেল’ আবিষ্কারের পরেই সামগ্রিক ভাবে স্পষ্ট হয়েছে, কীভাবে মানুষ সহ বেশ কিছু প্রাণী তাদের অবস্থান চিনতে পারে।
ঠিক কী কাজ এই গ্রিডসেলের? সেটাই আর একটু সহজ করে বোঝার চেষ্টা করব এখন।
কী করে আমরা বুঝতে পারি, যে আমরা যেখানে রয়েছি, সেটা কোন স্থান? আর কী করেই বা আমরা এক জায়গা থেকে চিনে চিনে অন্য জায়গা যেতে পারি? এই যে চেনানোর কাজ, সেটি নিখুঁত ভাবে করে থাকে গ্রিড-সেল। প্রতিটি স্থানের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র ছবির মতন ফুটিয়ে তোলে ব্রেনের মধ্যেকার এই ‘গ্রিডসেল’। এইভাবে প্রতিটি স্থান আলাদা করে চিনিয়ে দেয় মানুষ এবং অপরাপর প্রাণীদের। ওই স্থানের যাবতীয় মানচিত্র স্মৃতি হয়ে মজুত থাকে ব্রেনে। এভাবেই সম্ভব হয় ‘নেভিগেশন প্রক্রিয়া’। গ্রিড সেল যেন ঠিক ব্রেনের ‘ইন্টারনাল জিপিএস’। তাছাড়া, এই যে স্থান-জ্ঞান, এর সঙ্গে আবার নিবিড় ভাবে জড়িত দূরত্ব ও গতি। আমাদের সব অভিজ্ঞতার কথা মজুত করা থাকে মগজে! পরবর্তী সময়ে ওই জায়গায় আসার পর মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারি – এই সেই জায়গা! এই সেই পথ! কিংবা এই পথে গেলে আমার বাড়ি। ব্রেনের ‘পজিশনিং সিস্টেম’-এর কাজে গ্রিড সেল সংযোগ থাকার কথা আবিষ্কারের জন্যে ২০১৪ সালে ফিজিয়োলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পেলেন মে-ব্রিট মোসের, মে-ব্রিটের স্বামী এডোয়ার্ড মোসের এবং তাঁদের মেন্টর জন ও’কিফ। তাঁদের এই আবিষ্কার ব্রেনকোশ গবেষণায় যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত। পজিশনিং সিস্টেমের জ্ঞান থেকে কোনো বিশেষ গোত্রের কোশগুলি কীভাবে সামগ্রিক কগনেটিভ কাজ সুসম্পন্ন করে তার ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। স্মৃতি, চিন্তা এবং পরিকল্পনা করার মতন কাজগুলি কেমন ভাবে পরিচালিত হয় ব্রেনে তা বুঝতে পারা গেছে। এছাড়াও মোসের দম্পতির এই আবিষ্কারের জন্যে অ্যালজাইমার বা ডিমেনশিয়া সহ স্নায়ুঘটিত কয়েকটি দুরারোগ্য অসুখ সম্পর্কে ধারণাগুলি আরও পরিষ্কার হয়েছে।
************
#বিজ্ঞান #বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি #স্নায়ু বিজ্ঞান #মে-ব্রিট মোসের #সিদ্ধার্থ মজুমদার #সিলি পয়েন্ট #বাংলা পোর্টাল #science #brain mapping #silly point

সমিত মণ্ডল
লেখা টি পড়ে উৎসাহিত হলাম।জীবন যুদ্ধ,লড়াই মে-ব্রিটের আমাকে অনুপ্রাণিত করল। ধন্যবাদ।
মৃণালকান্তি দাশ
অত্যন্ত সরল ভাষায় একটি দুরূহ বিষয়কে উপস্থাপিত করলেন আপনি । আপনার কলম থেকে এরকম আরও লেখার অপেক্ষায় থাকলাম । ভালো থাকবেন খুব । সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা ।
Nirupam Chakraborti
তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। লেখকের অন্যান্য রচনার মতোই আকর্ষণীয়। আশাকরি ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক নিবন্ধ তিনি আমাদের উপহার দেবেন।
ANJANA GHOSH
অসাধারণ সুন্দর আর অমূল্য এক প্রতিবেদন। অবাক বিস্মকৈয়ে জানলাম ও'কিফ আবিষ্কৃত ব্রেনের 'প্লেস সেল' ও তার অনুসরণে মোসের দম্পতির আরো দীর্ঘ আর গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার শেষে আবিষ্কৃত গ্রিড সেলের কথা... "প্রতিটি স্থানের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র ছবির মতন ফুটিয়ে তোলে ব্রেনের মধ্যেকার এই গ্রিড সেল"... অনবদ্য expression . ... অত্যন্ত জটিল একটা বিষয়কে সাধারণের বোধগম্য করে উপস্থাপিত কি অনায়াস দক্ষতায়। সমৃদ্ধ হলাম একেবারেই অজানা এই বিষয়টা সম্পর্কে জেনে। অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে এরকম একটা interesting & informative বিষয় আপনার পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য।
Santu Bandyopadhyay
Dear Siddhartha, Well written article about the discovery of grid cells and their role in brain's navigation. Keep it up. Best wishes
Siddhartha Majumdar
ড. প্রদীপ পারেখ প্রদীপদা, আপনার সহৃদয় প্রশংসাসূচক মন্তব্য আমার কাছে বিশেষ প্রাপ্তি। লেখাটি পড়ে জানালেন বলে খুব ভালো লাগল। কোশ / কোষ দুটোই ঠিক। তবে বাংলা আকাদেমি cell এর ক্ষেত্রে 'কোশ' বানানটির ব্যবহার এগিয়ে রাখে।
প্রদীপ পারেখ
লেখাটা পড়ে বুঝলাম মোসের দম্পতির কাজ কেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁরা বিজ্ঞানী হিসেবে কী পর্যায়ের, কত উচ্চস্তরের। অথচ তাঁদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, এমনকি নামও শুনিনি। অথবা, শুনলেও ভুলে গেছি। এইরকম সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আড়ালে থেকে যাওয়া বহু বিজ্ঞানীর কথা আমাদের জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ মজুমদার। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ। লেখাটির ভাষাও বেশ তরতরে, সাবলীল। পড়তে ভালো লাগল। একটা ব্যাপারে খটকা লাগল শুধু। "কোষ" (cell) বানানটি না "কোশ" লেখা হল কেন?