জগদীশচন্দ্র ও সমকালীন বঙ্গসমাজ (অষ্টম পর্ব)
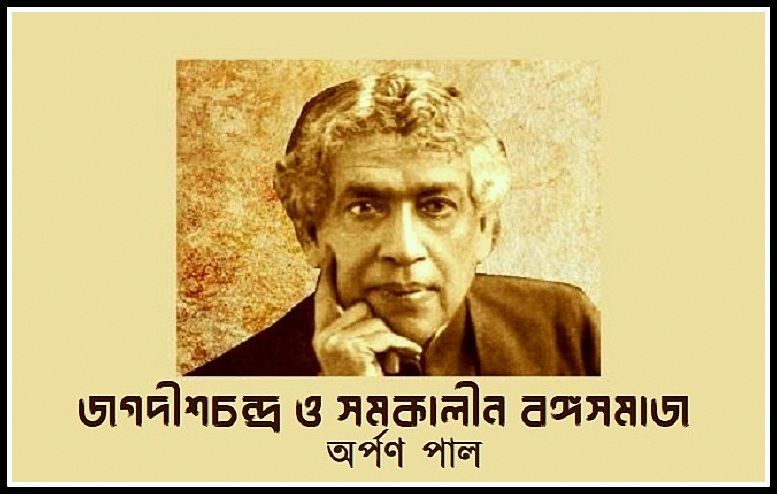
পর্ব ৮ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জগদীশচন্দ্র
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বঙ্গীয় বিদ্বান-জগতের উজ্জ্বল এক নাম। বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর দুয়েকের, এবং জগদীশচন্দ্রের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট এই কৃতি মানুষটির জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কলকাতায় নয়, এই শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। সেখানকার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ছেলে দ্বিজেন্দ্রলাল পড়াশুনো করেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। এরপর সরকারী চাকরিতে ঢোকেন, এবং কিছুকাল পরে সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাত্রা করেন কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করতে। পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরে তিনি আবার সরকারী চাকরিতেই ঢোকেন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরও হয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই ব্রিটিশ সাহেবদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁকে বদলি করে দেওয়া হত, সাতাশ বছরের চাকরিজীবনে তাঁকে মোট সতেরো বার বদলি করা হয়েছিল।
২. প্রায় পাঁচশো গান রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এর মধ্যে মাত্র ১৩২টি গানের সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গানগুলোর মধ্যে ‘ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে’, ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ বা ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’-এর মতো বেশ কিছু গান অমরত্ব লাভ করেছে। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গের সময় তাঁর লেখা গানগুলি সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, তাঁর নাম তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই সুরে উচ্চারিত হত। শুধু গান-ই বা কেন, তাঁর লেখা দেশাত্মবোধক নাটকগুলিও তখন মানুষকে প্রচণ্ডভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করত।
তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক প্রথম দিকে বেশ মধুরই ছিল। তাঁর আমন্ত্রণে ১৯০৪ সালে দোল পূর্ণিমার দিনে তাঁদের ৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে যে পূর্ণিমা মিলন-এর আসর বসেছিল, সেখানে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সারা গায়ে যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রঙ মাখিয়ে দেন, তখন রবীন্দ্রনাথ নাকি বলে ওঠেন, ‘আজ দ্বিজুবাবু শুধু যে আমাদের মনোরঞ্জনই করেছেন তা নয়, তিনি আজ আমাদের সর্বাঙ্গ-রঞ্জন করলেন।’
দু-জনেই ছিলেন দু-জনের গুণগ্রাহী। একে অন্যকে কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন, লিখিত ভাষায় পরস্পরের লেখার ভূয়সী প্রশংসাও করতেন। কিন্তু পরে একটা সময় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা কারণে বেশ মনোমালিন্য শুরু হয়, গুণগ্রাহী থেকে রবীন্দ্রনাথের ঘোর সমালোচকে পরিণত হন দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির আগের বছর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে ব্যঙ্গ করে লেখেন ‘আনন্দ বিদায়’ নামে একটি নাটিকা। সেই নাটিকার অভিনয়ের দিনে তাতে প্রবল রবীন্দ্র-বিদ্বেষ লক্ষ করে দর্শকেরা দারুণ ক্ষেপে যান, নাটক মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয় দর্শকের আপত্তিতে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন দেখেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের এই প্রকাশ। তাঁকে নাকি নাটকের মঞ্চের পেছন থেকে গোপনে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
এই ঘটনার পর বেশিদিন বাঁচেননি দ্বিজেন্দ্রলাল। ১৯১৩ সালের ১৭ মে তাঁর মৃত্যু হয়। আর ওই বছরের অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল প্রাপক হিসেবে ঘোষিত হয়। বেঁচে থাকলে দ্বিজেন্দ্রলাল কি ‘প্রাক্তন’ বন্ধুকে অভিনন্দন জানাতেন? কে জানে!
৩. ১৯০৭ সালের জুন মাস। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল চাকরিতে বদলি হয়ে গয়ায় কর্মরত। বছরখানেক হল তিনি এখানে এসেছেন, পেয়েছেন ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের পদ।

এই গয়ায় থাকাকালীন সময়ে জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। তাঁদের মধ্যে আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল (উনিশ শতকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুমহলে যে খামখেয়ালী সভা বসত মাঝেমধ্যেই, অন্যদের সঙ্গে সেখানে প্রায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন জগদীশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালও। অনুমান করা চলে, এইরকম সভাগুলিতেই এঁরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন), তাঁর একাধিক গান বা রচনার খুবই অনুরাগী ছিলেন জগদীশচন্দ্র। আর এইসময় তাঁদের পরিচয় বেশ খানিকটা গাঢ় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর দ্বিজেন্দ্রলাল-এর জীবনী বইয়ে লিখেছেন যে তাঁর (অর্থাৎ দেবকুমারবাবুর) অনুরোধে জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কিছু কথা লিখে জানিয়েছিলেন, তা এইরকম :
‘কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষায় করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিলেন, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।
‘ধরণী এক্ষণে দুর্ব্বলের ভার-বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে বীর্য্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্ম্ম-যুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্র-ধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।’ (দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনী, ৪৭৫ এবং ৪৭৬ পৃ)
দেবকুমারবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং বলেন যে তাঁর কয়েকটি গান শুনে জগদীশচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন, এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে— যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্ম-শক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া-উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন,— যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত’ একবার সেই আদর্শ এ বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া, মাতাইয়া তুলুন।’
এরপরে দেবকুমারবাবু লিখছেন, ‘বলা বাহুল্য— মাতৃভূমির সুসন্তান, দেশভক্ত জগদীশচন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখন এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল; এবং কিয়দ্দিন পরে তাহারই ফলে, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধের মহান সঙ্গীত— “আমার দেশ” রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রকৃতই সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।’ (ওই বইয়েরই ৪৭৬ পৃ)
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি বিশেষ গান যে জগদীশচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল তার আরও একটি প্রমাণ, দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি দিলীপকুমারের কাছে সেই গান ‘বঙ্গ আমার, ভারত আমার’ শুনতে চান। দিলীপকুমার লিখছেন, ‘বহু বৎসর পরে— বোধহয় ১৯২০ কি ২১ সাল— তাঁর সঙ্গে আবার দেখা লন্ডনে— তখন তিনি সানন্দে আমাকে বলেছিলেন: “গাও হে গাও তোমার বাবার বঙ্গ আমার, ভারত আমার। আহা কী গানই তিনি লিখে গেছেন! অমর— অমর!”... ইত্যাদি’।
‘আচার্য বসু অত্যুক্তি করেননি। পিতৃদেবের স্বদেশি গান কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার গ্রামে গ্রামে সপ্ত কোটি কণ্ঠে না হোক, হাজার হাজার কণ্ঠে বিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।’ (স্মৃতিচারণ, দিলীপকুমার রায়, ২১ পৃ)
দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল-প্রয়াণের সময় জগদীশচন্দ্র দেশেই ছিলেন। কিন্তু এই মৃত্যুতে তিনি কোনো স্মৃতিচারণ করেছিলেন কি না, তা জানা যায় না। কয়েক মাস পর রবীন্দ্রনাথের নোবেল-প্রাপ্তিতে শান্তিনিকেতনে যখন কলকাতা থেকে আগত অগণিত সুধীজন সমবেত হন তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে, সেখানে সভাপতি হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রই। বা আরও কয়েক বছর পরে জগদীশচন্দ্র গড়ে তোলেন তাঁর সাধের বসু বিজ্ঞান মন্দির। অকালে প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রলাল জেনে যেতে পারেননি এসবের কিছুই।
আজ আমরা স্রেফ ভাবতেই পারি, প্রায় সমবয়সী এই বন্ধুরা শিলাইদহে সপ্তাহান্তে মিলিত হচ্ছেন, সেখানে জ্যোৎস্নাধোয়া রাতে নদীতীরের স্নিগ্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁদের হাসি-গান-রসিকতা।
হায়, মানুষ হারিয়ে যায়, রয়ে যায় শুধু স্মৃতি!
..................

