কলকাতার আজ কাল পরশু
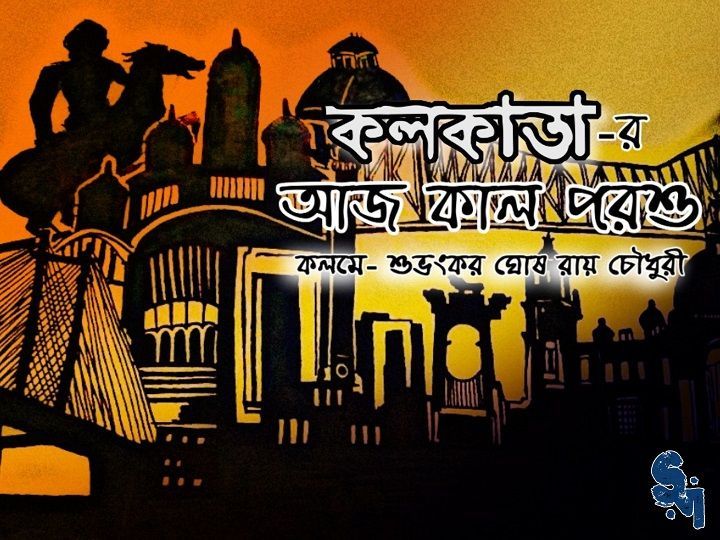
সময়টা ২০১১ সাল। আমেরিকা থেকে সপরিবার কলকাতায় ফিরলেন অভিষেক বিশ্বাস। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার; চাকরিসূত্রেই কয়েক বছর আমেরিকায় থাকা, তারপর পারিবারিক কারণেই কলকাতায় নতুন চাকরি নিয়ে ফিরে আসা।
তবে এতটা বললে সামান্য অবতারণা করা হয় মাত্র। আরও বলতেই হয়, অভিষেক ফিরলেন যখন, তখন মার্চ মাস পড়তে আর কিছুদিন বাকি। আসছে বিধানসভা ভোট– যাকে আজও আমরা চিনি ‘পরিবর্তন ২০১১’ নামে। নতুন অফিসে যাওয়া-আসার পথে, আমেরিকায় গিয়ে হারিয়ে ফেলা কলকাতার বন্ধুদের আবার-আড্ডায়, পথেঘাটে অপরিচিতের সঙ্গে অগোছালো শব্দ বিনিময়ে, আত্মীয়দের ঘরোয়া তর্কে বেশ একটা চোখে পড়ার মতো বদল খুঁজে পান অভিষেক। কমিউনিস্ট রেজিমে বড় হয়ে ওঠা, পড়াশোনা শেষে চাকরি জোগাড় করা অভিষেক শেষ যেমন দেখে গিয়েছিলেন তাঁর শহরকে, তার চেয়ে অনেকটাই বদলে গেছে এইবারের ‘সিটিস্কেপ’; শহরের নিজস্ব বডি ল্যাঙ্গুয়েজেও যেন ঠিক ‘আজ’ আর নেই। অস্পষ্ট, অনিশ্চিত হলেও নতুন কিছুর আভাস লেগে আছে তার চলনে বলনে। ভোটের তখনও দেরি, কিন্তু বাতাস এরই মধ্যে বইছে আগামীর।
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফটোগ্রাফার হিসেবে তদ্দিনে বেশ কিছু কাজ করে ফেলা অভিষেক ঠিক করে নেন তাঁর পরবর্তী প্রজেক্ট– কলকাতার আসছে-এক-দশক ডকুমেন্ট করবেন তিনি ছবিতে। ফেব্রুয়ারির মাঝ-বরাবর অভিষেকের এই দশ বছরের পরিকল্পনার প্রথম ছবি ওঠে ব্রিগেডের মাঠে– তৎকালীন সরকার আয়োজিত শেষ বড় র্যালি। শেষ শীতের গোধূলি, র্যালি ভেঙে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। ধু-ধু মাঠ, কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশের সারি, তাদের গায়ে বাঁধা মাইক। সন্ধের মুখের হাওয়ায় ইতস্তত উড়ছে বিচ্ছিন্ন কিছু লাল পতাকা।
এই প্রজেক্টের নাম অভিষেক রাখেন ‘Kolkatan Palimpsest’। যদি ডিকশনারি খুলে বসেন, দেখবেন, ‘palimpsest’ বলতে বোঝায় “something reused or altered but still bearing visible traces of its earlier form”– যা পুনঃব্যবহৃত বা পরিবর্তিত, অথচ যার শরীর থেকে অতীতের দাগও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। লেখনীর ভাষায়, ‘ওভার-রাইটিং’; কিন্তু কোনও শহরের, সমাজের আখ্যান লেখে যেই সময়, তার ভাষায় কী বলা যেতে পারে? অভিষেক এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন এই ‘পালিম্পসেস্ট’ প্রজেক্টকে– নতুন সরকার আসে, আক্ষরিকই এক যুগান্ত হয় এই শহরে। নতুন সাজে, ভাবনায়, প্রতিশ্রুতিতে চলতে থাকে যত পরের বছরগুলি, অভিষেকের ক্যামেরায় ধরা পড়ে আপাতভাবে আমাদের রোজকার চোখ এড়িয়ে যাওয়া, বা ‘নান্দনিক’ ফটোগ্রাফির যোগ্য মনে না-করা কিছু দৃশ্য। বিউটিফিকেশনের খাতিরে চিলড্রেনস পার্কের মাঝে সবুজ গাছপালা ছেঁটে বানানো হাতির আকৃতি রেলিং দিয়ে ঘেরা, আর সেই রেলিংয়ে শুকোতে থাকা পথবাসীদের ছেঁড়াখোঁড়া জামা; ঝুরঝুরে পুরোনো বাড়ির বাইরের একটা দেওয়ালে হঠাৎ কর্পোরেশন থেকে রংচঙে টাইলস বসিয়ে পানীয় জলের কলের সুব্যবস্থা; বেলেঘাটার অটোস্ট্যান্ডের কাছে মনীষীপুজোর হিড়িকে খাঁচাবন্দি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বিধান রায়; ছোট্ট চকচকে ফ্ল্যাটের সুইচবোর্ডে লাগানো ‘গুড নাইট’-মেশিনের পাশে দেওয়াল-জোড়া ভ্যান গঘের ‘স্টারি নাইট’; মেট্রো রেলের বগির মতো দেখতে সুলভ শৌচালয়; আধা-তৈরি ফ্লাইওভার আর ভাঙা রাস্তার পাশে ‘জি বাংলা’ বা ব্র্যান্ডেড সাজপোশাকের জ্বলজ্বলে প্ল্যাকার্ড। সব বন্দি হতে থাকে অভিষেকের ক্যামেরায়; ‘পালিম্পসেস্ট’ নিজের অর্থ তৈরি করে নিতে থাকে নিজেই। দীর্ঘ কিছু দশক নিজের ঐতিহ্যে গর্বিত প্রাচীনপন্থী অথচ দরাজ যে এক অদ্ভুত শরীর ছিল কলকাতার, হঠাৎই তার গায়ে চাপানো নিত্যনতুন পোশাক, সাজ, অলংকার শুধু এই শহরের চেহারা নয়, ভাষ্যও বদলে দিতে থাকে। অতীতের ওপরই জবরদখল চলতে থাকে ‘পরিবর্তন’-এর– যার উচ্চারণে ‘আগামী’র বা ভবিষ্যতের ছাপ স্পষ্ট। অভিষেকের ছবিতেও বাম-জমানার যুবকের নস্টালজিয়া প্রকাশ পায় না, আবার আজকের প্রতি কোনও অসহ্য বিতৃষ্ণাও ফুটে ওঠে না। খুব বিরল একটি ভাবে নিমজ্জিত তাঁর এই প্রোজেক্ট– কিছুটা নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ আলাপচারিতা কলকাতার সঙ্গে; যেন তিনি এই শহরের হয়েও ঠিক তার পক্ষে বা বিপক্ষে নন। অভিষেক ক্যামেরা নয়, হাতে একটা আয়না নিয়ে ঘুরছেন আসলে পথে পথে; শহরকেই দেখাচ্ছেন নিজের নতুন চেহারা; এবং খুব খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাঁর সেই নির্লিপ্তির আড়ালেও কোথায় যেন একচিলতে হাসি লেগে আছে – ‘smile’ নয়, ‘smirk’! বাঁকা, বুঝদার, বিকাশ রায়-সুলভ।
আসুন, এবার ঘোরাঘুরি ছেড়ে আমরা একটুখানি বসি লছমন বাওরার সুরের দোকানে। দোকানটা অবশ্য লছমনের নয়, সে নিতান্তই ছেলেমানুষ– বছর বাইশ বয়স। লালবাজার থেকে পোলক স্ট্রিট যাওয়ার পথে দুপাশের ফুটপাথে যে অসংখ্য সুরসামগ্রীর দোকান পড়ে, তারই একটি তৈরি করেছিলেন লছমনের দাদুর বাবা গত শতাব্দীর শুরুর দিকে। আশেপাশের দোকানগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে পুরোনো। একশ বছর পেরিয়ে গেছে, বংশানুক্রমে ছেলেরা সবাই-ই এসে বসেছে দোকানে। লছমনের দাদু, বাবা, ও নিজে। এখনও ওই যে খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছেন লছমনের বাবা; লছমন হাতে হাতে বাজনা এগিয়ে দিচ্ছে বা সরিয়ে রাখছে। আর ঠিক পাশেই একটা ঘুপচি, ছোট্ট ঘরে বসে লছমনের দাদু– নব্বই পেরিয়েছেন, চোখে দেখেন না তেমন– তবু আন্দাজে তানপুরার তার সারিয়ে ঠিকই বেঁধে দিচ্ছেন তানে। ওদের উল্টো ফুটে তিন-চারটে পুরোনো দোকান ভেঙে একটা কাচের দেওয়াল আর ভেতরে চকচকে লাইট দেওয়া ‘মিউজিক হাউজ’ করা হয়েছে। হাতের কাজ ফুরোলে লছমনের দাদু বাইরের টুলে বসে সামনের আবছা আধুনিকতার দিকে তাকিয়ে পুরোনো দিনের গল্প করেন আমাদের। ১৯৩৮ সালে, যখন ওঁর বয়স সাত, এই রাস্তা দিয়ে সুভাষ বসুর মিছিল যেতে দেখেছেন দোকানে বসে। ছয়ের দশকে মাঝে মাঝেই এই ঘরে ঢুঁ মারতেন শ্যামল মিত্র, আর এক-দুবার হেমন্ত বাবুও। চারিদিকের ভিড়ে, গোলমালে বৃদ্ধের এই গল্প কারোরই কানে গিয়ে পৌঁছোয় না হয়তো, কিন্তু লছমন এসব থেকে অনেক, অনেক দূরে ওই ‘মিউজিক হাউজ’-এর যুগে জন্মেও এই গল্পের শেষে চোখ মুছে নেয়। আড়ালে আমাদের বলে, “আমি আর কদিন চিনি কলকাতাকে! কিন্তু যেটুকু দেখেছি কলকাতার, তার অনেক বেশি শুনেছি বাবা আর দাদুর মুখে। দাদু যতদিন আছে, ততদিন যেন আমাদের দোকানটা নিয়ে কেউ কিছু না করে! একদিন তো যাবেই নতুনের হাতে ...”, আবার গলা বুজে আসে তার।
বস্তুত, এই শহরের ‘আজ’ ভারী গোলমেলে। কলকাতা ঠিক ‘আজ’ বাঁচে না। অভিষেকের ‘পালিম্পসেস্ট’-এর মতোই, তার আজে বরাবর অনেকটা অতীত লেগে আছে। তার বর্তমান বাসের মতো, অফিস টাইমের মেট্রোর মতো, লিলুয়া থেকে হাওড়া আসা বর্ধমান লোকালের মতো একটু দেরিতে আসে– ফলত, কলকাতার ‘কাল’ তবু যেন আজকের চেয়ে একটু বেশি ‘আজ’। আর কলকাতার ‘পরশু’ এক আজব পয়দা! তাকে দেখেছে এদিকে ওদিকে অনেকেই; তাকে চেয়েছেও হয়তো আরও বেশি মানুষ। কিন্তু তাকে কেউ স্বতন্ত্রভাবে মনে রাখতে চেয়েছে কি?
হাতিবাগানের স্টার, বা আরেকটু দূরে মিনার্ভা সেজে উঠেছে নতুনভাবে, তাদের ঐতিহ্য আর প্রাচীনতাকে কমার্শিয়ালাইজ করে; কিন্তু সেখানে নাটক দেখতে গেলে আজও আশেপাশের গলির বাড়িগুলো কোন শতাব্দীপ্রাচীন উপকথা আঁকড়ে বসে থাকে? কেন সে পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পুরোনো খড়খড়ি-আঁটা জানালার ওপারে আজও শোনা যায় গম্ভীর গলায় ছোটো কোনও এক নাটকের দলের রিহার্সাল? কেন মনে হয়, যে আগামীর চমক-দমক দেখে চোখ ধাঁধাচ্ছে আমাদের, সেই আগামীতেই এই বন্ধ জানালার ওপারের ছোটো ছোটো স্বপ্নগুলোর হয়তো শুধুই লড়াই, অপ্রাপ্তি? কেন এলগিন আর এক্সাইডের বহুতল, শশব্যস্ততা বাদ দিয়ে অনতিদূরে হরিশ মুখার্জি রোডে ঢুকে গদাধর আশ্রম বা বলরাম বসু ঘাটের দিকে যাওয়ার উঁচুনিচু গলিগুলো ধরে হাঁটলেই বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি এই শহরের ধুকপুক? ঘাটে যাওয়ার গলি ভাগ হয়ে গেছে আরও সরু সরু কানাগলিতে। দিনদুপুরেও সেসব রাস্তা অতল। বাড়ির সরু সরু দরজা, আধখোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় ওইটুকু উঠোনেই একফালি কলতলা। জমজমাট গড়িয়াহাটের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে বিজন সেতুর নিচে নিঝুম ট্রাম ডিপো। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজের তিনতলায় বৃদ্ধ বই-চিত্র গ্যালারিকে নবযৌবন দিতে লাগানো হয় নাটক করার নতুন স্পটলাইট। ২০১১-র ফেব্রুয়ারির অভিষেক বিশ্বাসের মতো ২০১৮-র ফেব্রুয়ারিতে পাঁচ-ছজন কুড়ির ঘরের ছেলেমেয়ে সেই বই-চিত্রে অভিনয় করে একটি নাটক, বিষয় কলকাতার সময়। ঘোরতর প্রাচীন শহরে সে নাটক বলে মেট্রোপলিসের কথা, আবার মেট্রোপলিটান সেট-আপ ছেড়ে মুহূর্তে চলে যায় বিকেলের বাগবাজার ঘাটের জনহীনতায়। তাদের হাতে কলকাতার অখণ্ডকাল অজাত হয়ে, ভ্রূণ হয়ে অতীত আর ভবিষ্যতের জোয়ার আর ভাটায় ভাসতে থাকে।
অভিষেক বিশ্বাসের ছবিতে হোক, লছমন বাওরার পরিবারের স্মৃতিতে বা বাস্তবে হোক, বা এতসব দৃশ্যকল্পেই হোক, এক সম্পূর্ণ অতীতবিজড়িত শহরে ‘আজ’ পেরিয়ে ‘কাল’ বাদ দিয়ে সোজা ‘পরশু’ এসে দাঁড়ালে বরাবরই তাকে বিসদৃশই লাগে, অসংলগ্ন লাগে। কলকাতা ভবিষ্যতের আশায় বা ভয়ে বাঁচলেও খুব কম সময়ই ভবিষ্যতের সঙ্গে ঘর করে বাঁচে। ১৮৯৫ সালে কোনও এক রেভারেন্ড হার্ট সাহেব কলকাতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন গোবিন্দপুর আর সুতানুটির নিরিখে, “unexactly defined, lying between the two”! আশ্চর্যের ব্যাপার এটুকুই, সম্পূর্ণ অন্য প্রেক্ষিতে, সময়ের যে খণ্ড কাল, তাতেও কলকাতার বর্তমান ওই উপরের সংজ্ঞার মতোই, অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী এক আবছায়া। সে সময় নয়, সময়ের জরা। প্রশ্ন শুধু তার অস্তিত্ব নিয়েই। উত্তর পাওয়ার আশা ছেড়ে কেবল ভাবা যেতে পারে, সে যেতে হয়তো চেয়েছিল ভবিষ্যতেই, কিন্তু তড়িঘড়ি এসে পড়া ‘উন্নয়ন’, ‘পরিবর্তন’-এর দৃঢ়, অগ্রগামী পদযাত্রার ঝড় থেকে বাঁচতে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অতীতে। তাই ভবিষ্যৎও তার কাছে ব্রাত্য, কালের নিয়মে অতীতও অপসৃয়মাণ। আর বর্তমান? এই তো, আর এক বছরের মাথায় শেষ হয়ে যাবে অভিষেকের এক দশকের কাজ; লছমনদের দোকানও কতদিন ওদের থাকে দেখা যাক!
[ছবি : মৌসুমী দত্ত।]


Tapas Datta
আর্টিকেল সুখপাঠ্য। আমরা যারা কোলকাতায় জন্ম গ্রহন করেছি লেখাটা বেশি করে রিলেট করছে। অভীর তোলা ছবি অন্য লিংক মারফত দেখলাম, বেশ বেশ ভালো। গতানুগতিক জীবন থেকে ঘুরে অন্য চিন্তা র সাহস তো দেখিয়ে ছে, সেটা কজন পারে। এগিয়ে যাও, শুভেচ্ছা রইলো।
arijit sen
ভালো লাগলো
Suvankar
সবাইকে অনেক, অনেক ধন্যবাদ। যে-কোনও প্রয়াসকেই সার্থক করে রসবেত্তা পাঠকের মতামত। এই সমাদরের চেয়ে বড় প্রাপ্তি সত্যিই নেই আর। লেখার সময় আমারও মনে হয়েছিল অভিষেক দা'র ছবি লেখাটির সঙ্গে দেওয়ার কথা। তবে লেখাটি যেহেতু exclusively "palimpsest" প্রজেক্টটি নিয়ে নয়, তার পরিসর বড় আরও একটু, সে জন্য শেষ অব্দি আমিই অভিষেক দা'র সঙ্গে ছবি দেওয়া নিয়ে আর কথা এগোই নি। তবে পরবর্তীতে অভিষেক দা'র কাজ নিয়ে আরও লেখার ইচ্ছে আছে। আপনাদের মতামত অবশ্যই খেয়াল রাখবো। লেখার সঙ্গে ছবি থাকলে নিঃসন্দেহে তা আরও অনেক সুন্দর হবে।
তুষার
সুন্দর লেখা.পড়েই মনে হলো ছবিগুলো দেখে ফেলি
Arunima Biswas
খুব সুন্দর লেখা। অভির ছবির সাথে পরিচিতি অনেকদিনের। এই লেখার মধ্যে দিয়ে সেই ছবিগুলো যেন স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। যারা ছবিগুলো দেখেন নি, তাদের জন্য অবশ্য তিন চারটি ফটো সঙ্গে থাকলে হয়তো আরো সম্পূর্ণ হতো সম্পর্কটা।
সোমালী
আরও অনেকের মত অভিষেক বিশ্বাসের ছবির জন্য তেষ্টা লাগছিল পড়তে পড়তে। কাল আজ কাল, কালের গতিতে মিলেমিশে মেখে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। বনেদি বাড়ির বারান্দায় প্লাস্টিকের নিওন সবুজ টবের মতন একটা অনুভূতি গায়ে লেগে রইল। লেখককে অভিনন্দন! লেখাখানা বেশ লাগলো!
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত
বেশ ভালো। ঝরঝরে ভাষায় অভিষেকের উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলা হয়েছে। এমনকি palimpsest এও ছন্দপতন হয়নি। এখন ছবিগুলো দেখলেই ষোলো কলা পূর্ণ হয়।
Moumita Koyal
Khub bhalo lekha relatable for us who have seen the change in our Kolkata kintu Avisheker chhobi is missing. His photographs would have made this writeup more vivid.
Debasis Basu
লখায় মুন্সিয়ানার ছাপ রয়েছে অভিষেকের কাজ সম্বন্ধে একটা পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় পুরনোর মধ্যে নতুনের ছোয়া, সাদার মধ্যে কালো, আলোকিত ঝকঝকে রাস্তার পাশে অন্ধকার গলি, পরিকল্পনার মাঝে অপরিকল্পনার ছোঁয়া এগুলো নিয়েই কলকাতা আর এই জন্যই এ শহর আমার এত প্রিয়। অভিষেকের কাজ আগেও দেখেছি ওর ছবির মধ্যে একটা ভাবনা একটা বক্তব্য থাকে যেটা ওকে অনেকের থেকে আলাদা করে দেয়। আমার ভালো লাগে। এবারের পরিকল্পনা যে আরো ভালো হবে এ ব্যপারে আমি নিশ্চিত। শুভেচ্ছা রইল।
Meghna
Good write up, but this does also call for at least a couple of pictures by Avi Biswas.
Indrani Ghosh
Bhalo laglo
Madhurima Biswas
Khub bhalo laglo...ektu pics dile aro bhalo lagto
তপন বিশ্বাস
বিগত যৌবনা কোলকাতা কে বেনারসি পড়লে এখনও সুন্দরী দেখায়। কিন্তু তার ছবি কই?
Anirban Sarkar
লেখাটা পড়ে ভাল লাগল। আমরা যারা সাতের দশকের তারা কোলকাতা ও কোলকাতাবাসীর অনেক পরিবর্তন দেখলাম। বিশেষ করে 1991 এ উদার অর্থনীতির আগমনে পাল্টে যাওয়া মনন এবং সমাজ। আজ যা কিছু দেখছি বা আগামীতে যা কিছু দেখব সবকিছুর জন্যই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে সবটা হয়তো পারছি না। পারা সম্ভবও নয়
Sumon Mukherjee
বেশ সুন্দর লেখা। তবে লেখার সাথে কিছু ছবি থাকলে ভিসুয়ালী অ্যাপিলিং এবং relate করতে সুবিধে হতো।
Souvik
কলকাতার এই ঝুলে থাকাটা তবু খানিক সুর পেয়েছে লেখায়। তবে শুধু কলকাতা নয়, extrapolation এর হিসাব বলে, পৃথিবীর কোনো শহরই আজ ঠিক 'আজ' এ নেই।
Mahasweta Banerjee
খুব ভাল লাগল।