ঘুণ
_1366x1366.jpg)
....................................
।।১।।
বড়দাদুর ঘরটা ওঁর মৃত্যুর পর থেকেই বন্ধ। ঘুমটা ভাঙল, ওই ঘরের কড়াগুলো নড়ল যখন।
ঝড়টা উঠেছিল মাঝরাতে।
আমাদের এই দুমহলা বাড়িতে যখনই ঝড় উঠত, ছেলেবেলায়, দৌড়ে চলে যেতাম নিচের উঠোনে। আমাদের উঠোনটা সর্বদাই কেন যেন ভিজে ভিজে থাকত। চটচটে, কাদা কাদা। যখন বৃষ্টি নামত তখন ওই কাদার মধ্যেই ছুটোছুটি করতাম। জল ঘাঁটতাম, আম কুড়োতাম। সেইরকমই ছিল আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগের একটা আষাঢ়ে বেলা। আমার বয়স তখন বারো। ঠাকুর্দা তখনও বেঁচে। আমরা চার-পাঁচজন নিচে নেমে এসেছিলাম ঝড় শুরু হতেই। এক-একটা দিনের শুরু দেখলে বোঝা যায় কেমন কাটবে, আবার এক-একটা দিন তার আভাসটুকুও দেয় না। সেদিন সকালের মেঘ দেখেই আমি টের পেয়েছিলাম। সেদিন অগ্নি কোণে মেঘ জমেছিল। ঈশান কোণ, অগ্নি কোণ, এসবই ঠাকুর্দার থেকে শেখা। ওরকম নীতিনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ আমাদের গোটা এলাকায় আর ছিল না। সবাই মান্য করত ঠাকুর্দাকে। আমাদের পরিবার ছিল ওঁর স্বপ্ন। সবাইকে এক্কেবারে নিখুঁত করে গড়ে তোলাই ছিল ওঁর ধ্যানজ্ঞান। রাতে ঠাকুর্দার কাছে শুয়ে আমাদের বংশের গরিমার গল্প শুনতাম। শিখতাম আমাকেও কীভাবে তার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে।
মেঘ করলেই আমরা উঠোনে নেমে আসতাম। ঝড় শুরু হবার ঠিক আগেই। আমি, ভাই, আমার খুড়তুতো দাদা, মামাতো দাদা… এদের মধ্যে সবচেয়ে বিচ্ছু ছিল আমার খুড়তুতো দাদা। ওর মুখটা ছিল অসম্ভব মিষ্টি। টুকটুকে ফর্সা, গোলগাল চোখে হালকা পাওয়ারের চশমা। হাতে সবসময় ঘড়ি। স্কুলের সেরা ছেলে ছিল। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় এমন চেহারা আর হাবভাব। ওর অন্যদিকটা কেউ জানত না। আমি জানতাম, বলা ভালো, টের পেতাম। ঠাকুর্দা বলেছিলেন, ওই শান্ত চোখ, নম্র হাসির আড়ালে একটা ভয়ংকর দানো আছে। দানো, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। কোনও রূপক নয়। সত্যিকারের দানো। ঠাকুর্দার কাছে শুনেছিলাম, প্রত্যেক পরিবারেই এরকম একটা করে দানো থাকে। সে দানোকে ধরার চোখ তৈরি করতে হয়। সবাই দেখতে পায় না, পেলেও যা করার তা করে না। আর সে সহজে ধরাও দেয় না…
“আর যখন ধরা দেয় তখন তাকে বাঁধাই করে ফেলতে হয়, বুঝলে দাদুভাই? তোমার বড়দাদু যখন আমার হাতে পরিবারের ভার দিয়ে চোখ বুজলেন তখন আমার বয়স ছিল চল্লিশ। উনি আমাকে সব শিখিয়ে গেছেন। আমি শিখিয়ে যাব তোমাকে…”
ঠাকুর্দার কথাগুলো রাতের পর রাত শুনতে শুনতে ঝিম ধরত। খুব আনন্দ হত। নিজেকে বড় মনে হত, অন্যদের থেকে আলাদা, বিশেষ! সেদিন আমরা যখন আম কুড়োতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই উঠোনের মাঝখানে থাকা নিমগাছটার গোড়ায় স্কুলের ল্যাবরেটরি থেকে চুরি করে আনা ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল দাদা। দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল,... গাছটার শিরায় শিরায় তখন লাভার মতো আগুনে তরল ছড়িয়ে পড়ছে; আমাদের আজন্মকালের পরিচিত সঙ্গী ধীরে ধীরে চূড়ান্ত নিষ্ঠুর একটা পরিণতির দিকে যাচ্ছিল। ওর হাতে তখনও বোতলটা ধরা ছিল। আমিই প্রথম দেখি। সেদিনই বুঝেছিলাম, সময় হয়েছে। ছোট্ট ধাপগুলো পেরিয়ে এসে এবার নিজেকে জাহির করার জন্য ও তৈরি। আর এটাই সময়, বাঁধাই হবার!
আমাদের বড়দাদু ছাপাখানায় কাজ করতেন। ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি তখন আমাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বড়দাদু ছিলেন ঠাকুর্দার থেকেও পণ্ডিত আর নীতিপরায়ণ। এক পয়সার এদিক ওদিক হত না তাঁর। বই-ই ছিল তাঁর সব। ঠাকুর্দা বলতেন, নিজের পুণ্যবলে সেই বড়দাদুই সুযোগ পেয়েছিলেন নিজের মনের মতো একটা বই বানাবার।
“…পরিবার একটা বই, বুঝলে দাদুভাই? আর তোমরা তার এক-একটা অধ্যায়। যে বইটা তোমায় লিখতে হবে নিখুঁত করে। প্রতিটি অক্ষর যেন সমান হয়… একটা ভুল বানানও বইটার গুরুত্ব নষ্ট করে দিতে পারে। অফসেটে যখন এক-একটা পাতায় কালি পড়ে নষ্ট হয়ে যেত, তোমার বড়দাদু তখন সেগুলোকে যত্ন করে গুছিয়ে রাখতেন। একটা, দুটো, তিনটে করে ভুল জমা হত। বড়দাদু অপেক্ষা করতেন। তারপর সময় আসত সেগুলো মুছে ফেলার, যাতে মূল বইটার ছাপায় কোনও ভুল না থাকে।…”
আমি ঠাকুর্দার সব কথা বুঝতাম না। সত্যিকারের দানো হয়, এরকম বিশ্বাসও আমার ছিল না। শুধু অন্ধের মতো মানতাম তাঁকে। জানতাম আমাদের পরিবারের এই রমরমা বড়দাদু শুধুমাত্র অর্জন করেছিলেন। ঠাকুর্দা সেটা ধরে রেখেছেন। বড়দাদুর ঘরটা ওঁর মৃত্যুর পর থেকেই বন্ধ। কোনও তালা নেই কিন্তু, শুধুই বন্ধ। ভেজানো বলে মনে হয়। অনেকেই অনেকবার সে ঘর খুলতে চেষ্টা করেছে, ঠেলেছে, ধাক্কা দিয়েছে, ভেঙে ফেলতে চেয়েছে, লাভ হয়নি।
কিন্তু আমি জানি ঠাকুর্দা একদিন ঢুকেছিলেন ওই ঘরে।
।।২।।
“তুই বাবার কাছে আর শুবি না। এখন থেকে ওপরের বড় ঘরটায় তোর থাকার ব্যবস্থা করেছি।…”
“কেন বাবা? ঠাকুর্দা আমাকে…”
“ঠাকুর্দার বলা গল্প তোমাকে আর শুনতে হবে না।…”
“কেন বাবা?”
“…”
“বাবা, প্লিজ বলো… আমার স্কুলের সব বন্ধুর থেকে ঠাকুর্দা অনেক ভালো। ওরা…”
“তুমি কিচ্ছু জানো না বাবলু, যা বলছি শোনো।…”
“আমি জানি… ঠাকুর্দা আজ বড়দাদুর ঘরে গিয়েছিল।…”
“বাবলু…”
বাবার চোখে হঠাৎ জেগে ওঠা আগুন দেখে এগারো বছরের আমি পিছু হটেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, দীর্ঘদিনের চাপা অজানিত ভয় আর অপ্রমাণীয় আশঙ্কা থেকে বুঝতে পারছিলাম… কিছু একটা গোলমাল আছে। ঠাকুর্দাকে ওই ঘরটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেও কোনও ফল হয়নি। আমাদের বংশে বড়দাদুকে নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। সামান্য ছাপাখানার কর্মচারী থেকে রাতারাতি দুমহলা বাড়ি-গাড়ি, ঠাট-বাট কী করে হলো তা নিয়ে কানাঘুষোও কম হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত যে কথাটা শোনা যেত, সেটাই আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম। দাদু যুদ্ধের বাজারে টাকাটা রোজকার করেছিলেন। যদিও সেটা বড়দাদুর চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। কিন্তু বাবা বলত সেই বাজারে এতগুলো পেটকে টানা,…
“ন্যায়ের সংজ্ঞা বদলায় বাবলু, যখন বড় হবে, বুঝবে।…”
দীর্ঘদিন, অনিচ্ছাতেই বাবার কথাটা বিশ্বাস করেছি। তার কিছু কারণও ছিল। দাদুর ঘরে আমি বেশ কিছু জার্মান পুতুল, কাচের থালাবাটি ছাড়াও দেখেছি বিখ্যাত Wusthof and Henckels এর ছুরি। ঠাকুর্দা বলতেন ওগুলো বড়দাদুর স্মৃতি।
…………………………………………………………………………………………………………………………
ওই নিমগাছটা বড় প্রিয় ছিল। সেদিন মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল আমার। চিৎকার করে ডেকেছিলাম ঠাকুর্দাকে। সেই বৃষ্টির মুহূর্তটুকু কেবল ভুলতে চেয়েছিলাম বাবাকে। বাবা যে এভাবে চলে যাবে আমি ভাবতেও পারিনি। ঠাকুর্দার সঙ্গে বাবার মিলত না, আমার সাথেও বাবার সেরকম সখ্য ছিল না, যেমনটা ছিল ঠাকুর্দার সাথে আমার। কিন্তু…
“দাদার মনে যে এত যন্ত্রণা ছিল, টের পাইনি কখনও…”
কাকার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। কাকা বুঝতে পারছে না! ভাই, দাদা কেউ বুঝতে পারছে না। কিন্তু আমি পারছি, যেমনটা ঠাকুর্দা পারছিলেন। যন্ত্রণা নয়, বাবা ভয় পেয়েছিল। আমাদের চারতলার ছাদ থেকে সটান ওই শানবাঁধানো রাস্তায় যখন বাবার দেহটা পড়েছিল তখন সবে ভোর হচ্ছে। সে রাতে বাবা বারবার আমাকে বলেছিল ওপরের বড় ঘরটায় চলে যেতে। আমি শুনিনি। নিজেকে দায়ী করেছিলাম, ভেবেছিলাম, কেন বাবার কথা শুনলাম না। এগারো বছরের ছোট্ট আমি নিজেকে খুঁড়তে চেয়েছিলাম, বাবার মুখটা দেখার আগে পর্যন্ত।
কিন্তু যে মুহূর্তে বাবার মুখটা দেখলাম… বাবা চেয়েছিল বাড়ি থেকে বাইরে যেতে। রাতেই। কিন্তু পারেনি। একতলায় বড়দাদুর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় কেন যেন আটকে গিয়েছিল বাবা। আমি তখন দাঁড়িয়েছিলাম একটু দূরে, বারান্দাটা যেখানে বাঁক নিচ্ছে। কুড়ি পাওয়ারের আলোর তেরছা হলুদ ছড়িয়ে পড়ছিল বাবার শরীরে। বিবর্ণ হলুদাভ দেহটা স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড়দাদুর ঘরের সামনেই। আমি জানতাম, সেদিন থেকে ঠিক কুড়ি বছর আগে ওই ঘরটায় বড়দাদু ঢুকেছিলেন। আর বার হননি। তারপর কী হয়েছিল তা শত চেষ্টাতেও ঠাকুর্দার মুখ থেকে বার করতে পারিনি। বাবা জানতেন। বাবার ভয় ছিল। সেই বয়সে আর কিছু পড়তে পারি আর না পারি বাবার চোখের ভয়টা পড়তে পেরেছিলাম। বাবার কথা না শোনার জন্য নিজের মনেই একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। ঠাকুর্দা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপিচুপি বেরিয়ে আসছিলাম বাবার ঘরের দিকেই, তখনই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলাম। নিচে নেমে বাবার ওই চেহারা দেখে কেন যেন আমিও থম মেরে গিয়েছিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। জানি না কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম,… ততক্ষণ, যতক্ষণ না ওই শব্দটা কানে এসেছিল। ধপ… একটি সামান্য অব্যয়, একটি সামান্য মুহূর্ত! কিন্তু কী অসীম তার শক্তি। বিজ্ঞান বলে, আমাদের কানের এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে আতঙ্ক তৈরি করার। যা শুনছি, তার গুরুত্ব, সে যত আংশিক আর অবোধ্যই হোক না কেন, সটান গিয়ে ধাক্কা মারে বুকের অন্তঃস্থলে। কিছু দেখার প্রয়োজন থাকে না আর। ওই শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। রাসায়নিক বললে রাসায়নিক, জৈবিক বললে জৈবিক।বাবা ছাদের সেইদিক থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল যেদিকটায় পিচরাস্তাটা পড়ে। উল্টোমুখে, যাতে বাবার মুখটা নষ্ট না হয়। আমি জানতাম কেন, আমি যেন বাবার মুখটা দেখতে পাই। বাবার চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছিল সকেটের বাইরে। করোটি ভাঙার অভিঘাতে। কিন্তু মুখ সেভাবে বিকৃত হয়নি। ঠাকুর্দা দেখাতে চাননি, কিন্তু আমি জোর করেই দেখেছিলাম। কারণ আমি জানতাম আমার ভয়টা সত্যি। আমি শুধু সেটাকে মিলিয়ে নিতে গিয়েছিলাম। ঠাকুর্দাকে সেদিন নিজের মনে একটা কথাই বলতে শুনেছিলাম, “এভাবে চক্র ভাঙা যায় না। তুই ভুল করলি বাবু…”
।।৩।।
ঝড়টা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। আমারই বুঝতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন বড়দাদুর ঘরের তালাবিহীন কড়াগুলো নড়ে উঠল, আমার এযাবৎকালের সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে রেখে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম দরজাটার সামনে। মাথা এখনও পরিষ্কার কাজ করছে, তাই আমি জানি, তালাহীন হলেও, যদি আমার সময় না হয়ে থাকে তাহলে আমি এ ঘরে ঢুকতে পারব না। সুখের কথা হল, আমার মন বলছে, সময় হয়েছে! বাবা চেষ্টা করেছেন, কাকাও। আমি জানি আর চেষ্টার কিছু নেই। তাই কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরের ঝড় প্রবলাকৃতি হয়ে উঠছে! আর ভিতরে আমি টের পাচ্ছি সেই শব্দটা। খসখসখস, কেউ যেন টেনে টেনে কাদাছাপ ফেলে হেঁটে আসছে।
…………………………………………………………………………………………………………………………….
চোখের সামনে ফুটে উঠছে আমার বারো বছর বয়সের উঠোন। কাদামাখা উঠোনে আমি দ্বিতীয়বারের জন্য দেখেছিলাম সেই ছাপ। ভারী অদ্ভুত, উল্টোনো পায়ের ছাপ। কাদামাখা সেই ছাপ শেষ হয়েছিল বড়দাদুর ঘরের সামনে গিয়ে। ঠাকুর্দাকে বলেছিলাম। ঠাকুর্দা আমার মুখ চেপে ধরেছিলেন। বলেছিলেন ও ছাপ মুছে যাবে এখনি। হয়েও ছিল তাই। শুধু আমার খুড়তুতো দাদাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেদিন রাত থেকে ঠাকুর্দার কাছে শুতে যাইনি আর। ওঁর ঘরে পড়েছিল আমার অনেকগুলো বইখাতা। আনিওনি সেগুলো। কিন্তু স্কুলের জন্য দরকার হয়েছিল। কতদিন আর দেরি করব!
দাদা হারিয়ে যাবার চারদিন পরের ঘটনা। রাতে শোবার আগে খেয়াল পড়ল কালই লাগবে একটা বই। দোতলায় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলাম একতলায়। ঠাকুর্দার ঘরের কাছাকাছি আসতেই শুনতে পেলাম তর্কাতর্কিটা।
“এ তুমি কী করেছ বাবা! এ তুমি কী বলছ! দাদা তাহলে সত্যি বলেছিল! দাদা… তখন ওর কথা বিশ্বাস করতে পারিনি, ভেবেছিলাম ওর মানসিক সমস্যা… এও কি সম্ভব!...”
“আমার যা বলার স্পষ্ট করেই বললাম বুলু। বাকি তুমি নিজের চোখেই দেখলে।…”
“আমি আজই ভাঙব ওই ঘর! না, পুড়িয়ে দেব… পুড়ে যাবে ওই উইল!”
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কাকা ঘর থেকে বেরোবার আগেই ঠাকুর্দা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছিলেন কাকার হাত।
“ঠিক এই কারণেই কাউকে কিছু জানানো বারণ। তোমরা মূর্খ! ও সাধারণ কোনও উইল নয়! ও যে সনদ! বাঁশুড়ের সনদ! ওর প্রাপ্য ওকে না দিলে, সব হারাতে হয়।… তোমার দাদা ভেবেছিল সময়ের আগে নিজেকে শেষ করে আমাদের উপকার করছে, এই চক্র ও ভেঙে দিতে পারবে! কিন্তু সে যে মস্ত বড় ভুল, এখন প্রমাণ হল তো!...”
“ওই পায়ের ছাপ ধরেই আমি লোকটাকে ধরে ফেলতাম, যদি না তুমি…”
“মহামূর্খ তুমি! ও পায়ের ছাপের মালিককে কেউ কোনোদিন ধরতে পারেনি। স্বেচ্ছায় ধরা দিলে শাস্তি কমবে। একটা তালাবিহীন ঘর কেন কেউ শত চেষ্টাতেও খুলতে পারেনি কোনোদিন, ভেবে দেখেছ!...”
“বাবা, তুমি নিজের বংশধরকে এভাবে উৎসর্গ করবে! এ কীরকম শর্ত, এ শর্তে কোনও মানুষ রাজি হয়!...”
“হয়, দিনের পর দিন না খেতে পেলে, পুথির কাব্যিক সুন্দর পৃথিবীর বাস্তব কালো রূপটা দেখতে পেলে, দেশ আর সমাজ যখন বেছে বেছে নিরপরাধ দুর্বলদের হত্যা করে, অথবা নিশ্চিত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মজা দেখার জন্য, সেই শকুন-সভ্যতার শবের ওপর দাঁড়িয়ে সবকিছুই করতে পারে একটা মানুষ, যদি তার ভেতরে সেই আপামর স্পর্ধাটুকু থাকে! সেই আগুনটুকু থাকে!...”
স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাবার মুখে শুনেছিলাম একবার। বছরখানেক আগে। বাবা আমাকে বলেননি। জেঠুকে বলছিলেন। ঠাকুর্দার অফিসের কাছেই ছিল ফলপট্টি। সেখানে সৈন্যরা ফল কিনতে আসত। একছড়া কলা কিনতে ১৯৪০ সালে এক-একজনকে বড়দাদু দেখেছেন একশো টাকা পর্যন্ত দিতে। লুটে, ফেলে ছড়িয়ে শহরটাকে ছিন্নভিন্ন করে যেত তারা। সেরকমই এক সৈন্য একদিন রাস্তায় নেশা করে পড়ে ছিল। গাড়ি চাপা পড়ে মারাই যেত, দাদু বাঁচিয়েছিলেন তাকে। সে-ই দাদুকে দিয়েছিল বইটা। আমার আজন্ম শান্ত জেঠু বাবাকে সেদিন কিছু বলেননি উত্তরে। তারপর জেঠুকে আর পাঁচদিন দেখতে পেয়েছিলাম। পঞ্চম দিন সেই কাদামাখা পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। প্রথমবার।
তখনও পর্যন্ত জিনিসটাকে আমি বই বলেই ভাবতাম।
………………………………………………………………………………………………………………………
চড়াৎ…
কমে আসা বৃষ্টি আর ঝড়ের ঝিমোনো শব্দ পেরিয়ে পুরোনো কাঠের আওয়াজটা কানে নয়, বুকের ভিতরে এসে ধাক্কা মারল। খুলে গেছে। মহার্ঘ মেহগনির পাল্লা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ভিতরের ভ্যাপসা হাওয়া মুখে এসে ধাক্কা মারছে। বুকটা সম্পূর্ণ খালি। কিচ্ছু মনে আসছে না আর। অদ্যই শেষ রজনী। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা মৃতবৎসা হাসির আভাস নিজেকে পীড়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পা দিলাম শতাব্দীপ্রাচীন সম্পূর্ণ ফাঁকা ঘরটিতে। না, ভুল! সম্পূর্ণ ফাঁকা নয়! ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল রয়েছে। ধপধপে সাদা। জানি না কীভাবে এই বদ্ধ ঘরে ঝকঝকে আছে সেটা। তার থেকেও বড় কথা টেবিলের ওপর রয়েছে জিনিসটা… হালকা বাদামি কাগজটার খসখসে ভাবটা চোখে দেখেই ধরতে পারছি। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। না, আমার হাত কাঁপছে না। খসখসে শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আমি অপেক্ষা করছি। নিষ্প্রদীপ, ঝড়েলা, একটি পাথরবাড়ির অন্ধগর্ভে, আমি, একার অপেক্ষায়। আজ মুখোমুখি হবার সময়।
সতর্ক হাত রাখলাম সনদের ওপর। আর হাত রাখতেই চমকে উঠলাম! এ তো কাগজ নয়। এ যে… চামড়া। প্রথম পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ল বড়দাদুর নাম। ভূমিকায় তাঁর পরিচয়, তারপর লেখা শুরু হয়েছে। বড়দাদুর আত্মজীবনী। সব পড়ার দরকার নেই, দ্রুত সাবধানী হাতে উলটে গেলাম পাতাগুলো…
“হ্যাঁ, উহাকে দেয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রতি পুরুষে একটি করে আত্মা উৎসর্গীকৃ্ত হইবে। পরিবর্তে সে দান করিবে খাদ্য, বৈভব এবং বাকি প্রজন্মের আজন্ম নিরাপত্তা। আমার নিকট ইহা চন্দ্র হস্তগত হইবার অপেক্ষা কম কিছু নহে। প্রথম উৎসর্গ হিসাবে আমি স্বেচ্ছায় স্বীয় আত্মাই বাছিয়া লইয়াছি। জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তে পরিবারের সকল দায় অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত। উহাদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত রহিল। ইহার অপেক্ষা আনন্দের কী-ই বা থাকিতে পারে!...”
নিস্পন্দভাবে পাতা ওল্টালাম। জ্যাঠামশাই…
“বাবামশাই চেষ্টা করেছিলেন। আমিই চাইনি। ওঁর মধ্যে যে দৃঢ়তা আর উদ্যম রয়েছে তা আমার মধ্যে নেই। খুড়োমশাইকে উনি নিজের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। জানি খুড়োমশাই অতি কুটিল এবং ক্ষতিকারক মানুষ ছিলেন। আমাদের দেশের বাড়িতে উনিই আগুন ধরিয়ে আমাদের পরিবারকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাহলেও আমার পক্ষে এই মারাত্মক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হবে না কোনোদিনই। বাবা আমাকে আমার পুরুষের অধিকারী করতে চাইছেন ঠিকই, কিন্তু আমি কাকে বলি দেব? নিজের বলিষ্ঠ ভাইকে? তাও যে কিনা নির্দোষ! আর তারপর? এর থেকে নিজের জীবন দেওয়া অনেক সহজ। এ সাফল্যের জীবন থাকার চাইতে যাওয়াই অনেক ভালো।…”
পাতা ওল্টালাম…
বাবা… “আমি এই শৃঙ্খল ভেঙে দেব। তার একমাত্র উপায় নিয়ম ভাঙা। একই পুরুষে দুবার উৎসর্গ। কিন্তু না, আমি নিজেকে ওই ঘরে বন্দি করব না কিছুতেই। ওই সনদ আমি পুড়িয়ে স্বেচ্ছায় মরব, বাড়ির বাইরে। কিন্তু যখনই ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, জানি না কী হল আমার। যেন পা দুটো মাটিতে আটকে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই বুঝলাম আমার থেকে অনেক বড় এক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছি আমি। এ অসম যুদ্ধে জেতার ক্ষমতা নেই আমার। কিন্তু তখন আর ফেরার কোনও উপায় বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না। কেউ যেন আমার শরীরকে চালনা করে ছাদে নিয়ে গেল। বুঝলাম আড়ালে নিষ্ঠুর হাসি হাসছে অদৃশ্য, অভিশপ্ত বাঁশুড়ে।…”
পাতা ওল্টালাম…
ঠাকুর্দা… “আমি শুধু চেয়েছিলাম আমার পরিবার অচ্ছেদ্য পূর্ণতা পাক। যাবতীয় কালোর থেকে আলাদা করে, এক খুঁতহীন দুর্ভেদ্য জগৎ গড়ে উঠুক। বুঝিনি, সে এক বালখিল্যতা ছিল। বাবা নিজেকে বলি দিতে একবারও ভাবেননি। তাঁর দেওয়া সূত্র ধরে চলতে গিয়ে এতবড় ভুল করে ফেললাম!
প্রত্যেক পরিবারেই বিকার থাকে। সে জিনিস সবার মধ্যে সমানভাবে প্রকাশ পায় না। সে বিকার এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁশুড়ের সনদ অনুযায়ী আমাদের ঠাটবাট অটুট থাকার মূল্য ছিল এক পুরুষের একটি আত্মা। আর সেটা বাছাও ছিল সহজ। তার দুরকম পন্থা ছিল। এক, কেউ নিজেকে বলি দিতে পারে। দুই, প্রতি প্রজন্মের সমস্ত বিকার জড়ো হবে একটিমাত্র ব্যক্তির মধ্যে, তাকে বলি দেওয়াই যথেষ্ট! মেনে নিয়েছিলাম এ নিয়ম। এই জঙ্গলরাজের দুনিয়ার কিছু নিয়ম তো দরকার! কেউ দেখার নেই আমাদের, কেউ শোনার নেই। তাই নিজেদের নিয়মে নিজেদের একচ্ছত্র উন্নতি করতে হবে। এর জন্য যদি কিছু বলিদান লাগে তাতে কষ্ট হলেও সেটার জন্য প্রস্তুতি রাখতে হবে! আমরা পুজোয় যে বলি দিই সেটা কীসের প্রতীক! বকরি ইদের বলি কীসের প্রতীক! খারাপকে ত্যাগ করাই ধর্ম শেখায় না কি আমাদের! পরিবর্তে যদি আমরা জীবনভর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি পাই, তাতে ভুল কোথায়! ছোটখোকার ছেলে এক আস্ত দানব! আমি জেনেও অপেক্ষায় ছিলাম। ভাইবোনেদের নষ্ট করা শুরু করেছিল সে। মেজোখোকার ছেলে যদি তাকে তাকে শনাক্ত না করত, তাহলে আমিই… শুধু ওই ঘরের দরজায় তিনবার টোকা, ব্যস! কিন্তু না, আজ বুঝতে পারছি, ভুল, ভুল ছিল আমার! এভাবে হয় না। আমার প্রাণপ্রিয় নাতি আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে! বাবার মৃত্যুর জন্য ও কি আমাকে সন্দেহ করে কোনোভাবে? আমি তো চেষ্টা করেছিলাম, মৃত্যু-ইচ্ছা ছাড়া ও ঘরে ঢোকা যায় না। সে ইচ্ছা নিয়েই আমি সেদিন ওই ঘরে ঢুকেছিলাম। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল! বড়খোকা, মেজোখোকা! চক্র যে ভেঙে গেছে সেদিনই টের পেয়েছিলাম আমি। বাঁশুড়ে কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে না! ভালো আর কালো এভাবে আলাদা হয় না। আর না… রূপ, মান, যশ, অর্থ… সব মিথ্যা! হে ঈশ্বর…”
দরজাটা সামান্য নড়ে উঠল। ষষ্ঠেন্দ্রিয় অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে রয়েছে। টের পাচ্ছি একটা মনুষ্য অবয়ব। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম!
“আমি প্রস্তুত!” স্পন্দনহীন গলায় বললাম আমি।
খলখলে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। আলখাল্লার মতো পোশাকে অদ্ভুত চেহারার একজন ঘরে ঢুকেছে। উপকথার বাঁশুড়ে তবে সত্যি!
“চক্র ভাঙার মূল্য জানো?”
“জানি…” অকম্পিত কণ্ঠ আমার।
আবার হাসির শব্দ।
“তোমরা ভাবো বাঁশুড়ে কেবল একজন! জার্মান দেশেই তার ঠিকানা, তাই না!”
“সারাজীবন সততার বদলে অপমান আর যন্ত্রণা সহ্য করা আমার বড়দাদু শুধু চেয়েছিলেন যাতে আমরা ভালো থাকি। আমাদের রক্ত যেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হয়, আর আমাদের ক্ষমতা…”
খলখলে হাসিটা যেন থামতেই চাইছে না।
“তোমার কি মনে হয়, কীভাবে এ পৃথিবীতে যুদ্ধ শুরু হয়? হিংসা? বর্ণবিদ্বেষ? লালসা?...”
ভেতরটা শুকিয়ে আসছে, টের পাচ্ছি। কাঁপা গলায় আপ্রাণ শীতলতা ধরে রাখার চেষ্টা করতে করতে বললাম, “চক্র ভেঙেছে! এবার সবাইকে তুমি নেবে! এই তো সোজা কথা! এ বাড়িতে এক আমিই তো রয়ে গেছি! দেরি কেন তবে? আর কথারই বা কী দরকার!”
“দরকার আছে বই কি! তোমরা নিজেরা লাভের লোভটুকুই দেখেছ, তার দামটুকু জানবে না! আমার কাজ এখানে শেষ। আত্মার ওই সনদ আমার! এবার তোমার কাজ শুরু!”
যেন মায়াবলে পুরোনো সনদের জায়গায় টেবিলের ওপর হাজির হল এক নতুন সনদ। সম্পূর্ণ ফাঁকা।
“সনদের শেষ কথাটুকু তোমাকে কেউ বলেনি? আমরা শেষজনকে বেছে নিই… আজ থেকে তুমি নতুন বাঁশুড়ে। সংগ্রহের কাজ শুরু তোমার!...”
আরও পড়ুন : এক আকাশের শূন্যতা / ঋভু চট্টোপাধ্যায়
হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে বাঁশুড়ে, মিলিয়ে যাচ্ছে ঘর, মিলিয়ে যাচ্ছে আমার চেনা সবকিছু…
“না… আমাকেও নিয়ে যাও… ওই সনদের রক্তাক্ষরে গেঁথে নাও আমারও আত্মা আলেখ্য…”
কেবল এই শেষ চিৎকারটুকুই মনে আছে আমার… তারপর…
..............................................
[অলংকরণ ; অভীক ]
#গল্প #রবিবারের গল্প #বাংলা গল্প #শরণ্যা মুখোপাধ্যায় #সিলি পয়েন্ট #silly পয়েন্ট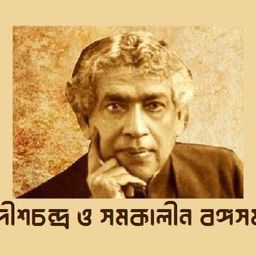
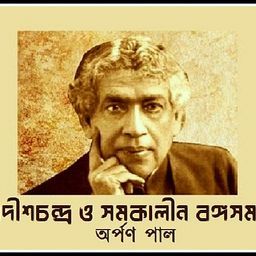
kousik chatterjee
দুর্দান্ত টানটান৷শেষের ট্যুইস্টও চমৎকার৷