সত্যজিৎ ও পাশ্চাত্য সমাজচেতনা – এক অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন
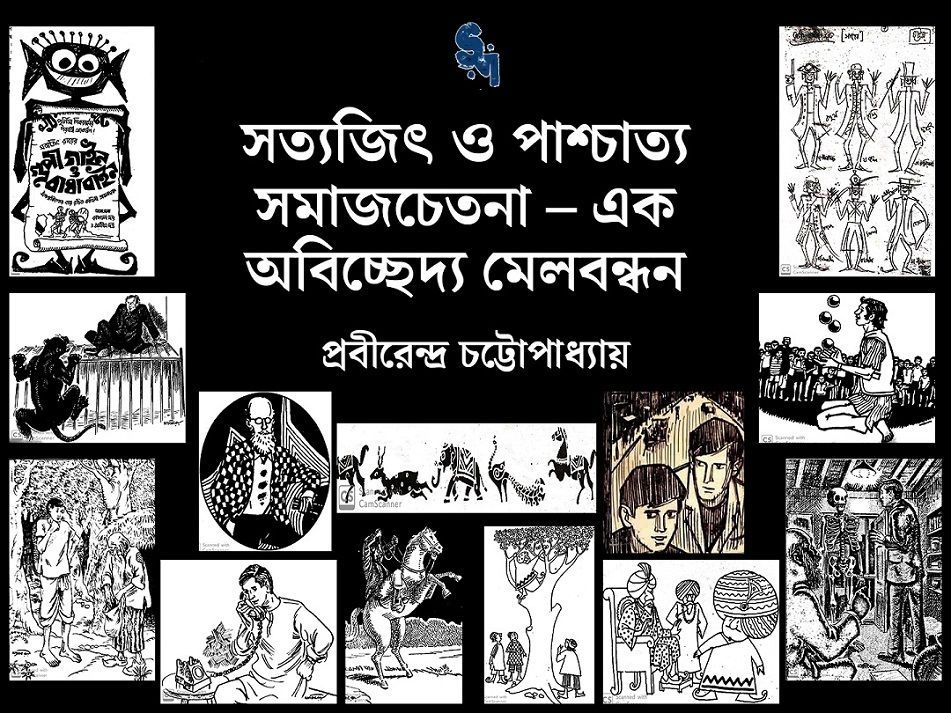
বড়োদিনের ছুটিতে ফের একবার ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ দেখতে বসেছিলাম। বিরিঞ্চিবাবার অমোঘ টানে মাঝেমাঝেই চোদ্দ নম্বর হাবশি বাগান লেনের সেই ঠেকে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এ যাত্রা সোমেন–সতীন্দ্র–সত্যদের আড্ডায় না ঢুকে চলে গেলাম উত্তরবঙ্গের সেই জনবিরল চা-বাগানের বাংলোতে যেখানে ক্রমেই ঘনিয়ে উঠছে এক অমোঘ টেনশন। ছড়িয়ে পড়ছে এক অবধারিত যৌনঈর্ষা। এবং ‘কাপুরুষ’ দেখতে বসে আবারও খেয়াল পড়ল প্রেমেন্দ্র মিত্রের মূল গল্প (‘জনৈক কাপুরুষের কাহিনী’) এবং সত্যজিতের সিনেমার মধ্যে অনেকটাই বিচ্যুতি। এবং সে বিচ্যুতি পুরোপুরিই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সে বিচ্যুতি সত্যজিতের মননশীলতায় ভাস্বর। গল্পের প্রোটাগনিস্ট অমিতাভ রায় ভাগ্যচক্রে তার ভূতপূর্ব প্রেমিকা করুণার বাড়িতে হাজির হওয়ামাত্রই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে এক নাটকীয়তা নিয়ে আসেন।
‘‘হঠাৎ তাকে করুণার কথায় সবিস্ময়ে থেমে যেতে হয়েছে। করুণা হেসে বলেছে –“বিদেশ-বিভূঁয়ে একটু কষ্ট হলই বা ভদ্রলোকের!”
বিমলবাবু অবাক হয়ে আমাদের দুজনের মুখের দিকে চেঁচিয়ে ওঠেন —“তার মানে! এঁকে তুমি চেনো নাকি!”
“তা একটু চিনি বৈকি!”— করুণা হেসে উঠেছে।”
এই নাটকীয়তা আকস্মিক, খানিক গায়েপড়া। ছোটোগল্পের সার্থক রূপরেখা অনুসরণের প্রয়াস।
সত্যজিৎ তাঁর মাধ্যমে কিন্তু এই আকস্মিক নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে আদৌ গেলেন না। হতচকিত সৌমিত্র প্রথম এক ঝলকের পর মাধবীর মুখ দেখতেই পেলেন না। বিব্রত মাধবী অস্ফুটে বলে উঠলেন ‘‘কী বিশ্রী দিন!” সে দ্ব্যর্থবোধক কথাটি শুধু যেন দর্শকদের শোনানোর জন্যই। আরও পরে দেখি হারাধনের জবানবন্দিতে মাধবী জানাচ্ছেন তিনি কলেজে থাকতে এক অমিতাভ রায়কে চিনতেন বটে কিন্তু চিত্রনাট্যকার অমিতাভর কথা তিনি আগে শোনেননি। এখানেও সত্যজিৎ ব্যাজস্তুতির কিছু অবকাশ রেখে গেলেন, দিয়ে গেলেন এক টেনশনের আভাস, কিন্তু গার্হস্থ্য নাটকের মধ্যে তাঁর চরিত্রদের সরাসরি এনে ফেললেন না।

এই মিতভাষী এবং সংযত আবেগের বহিঃপ্রকাশ কিন্তু লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখাননি। তখনও, হয়তো এখনও, সাধারণ বাঙালি বাড়িতে অনুভূতির এই অভিজাত বহিঃপ্রকাশ চট করে দেখা যেত না বা যায় না। এ বহিঃপ্রকাশে রয়ে গেছে পাশ্চাত্য সমাজচিন্তার অনিবার্য স্বাক্ষর। আপাত-অপরিচিত মানুষকে ডেকে আনার জন্য সামান্য অনুযোগও করুণা জানায় না। আবার পরে অমিতাভ যখন যৌনঈর্ষার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়ে এক প্রায় অশ্লীল প্রশ্ন করে বসে (‘‘তুমি ওই লোকটাকে ভালোবাসো?!”), করুণা আদৌ তাকে তিরস্কার করে না, বরং এক অনায়াস এবং মার্জিত প্রত্যুত্তরে দর্শককে কাছে পেয়ে যায় (‘‘তুমি তো চেনো না ওকে। একদিনের আলাপে মানুষ চেনা যায়?”)। এই করুণা যেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসকন্যা নয়, বরং ‘কাপুরুষ’-এর তিন বছর আগে মুক্তি পাওয়া রোমান পোলানস্কির ‘নাইফ ইন দ্য ওয়াটার’ (১৯৬২) সিনেমার মুখ্য চরিত্র ক্রিস্টিনার ছায়াবিশেষ। অপ্রত্যাশিত আলাপ থেকে অবধারিত যৌনঈর্ষা, সামলাতে হয়েছিল ক্রিস্টিনাকেও। করুণার মতন ক্রিস্টিনার কাছেও সেসব জাগতিক সত্য মাত্র, এক বৃহত্তর প্রেক্ষিতের সামান্য অংশ। সে সত্যিকে অস্বীকার করে অনর্থক উত্তেজনা বা তাকে উপহাস করে অযাচিত মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে করুণা বা ক্রিস্টিনার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।
এক আপাদমস্তক বাঙালি পরিবেশে বড় হয়েও সত্যজিতের জীবনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং সমাজবোধ এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সেই ছেলেবেলা থেকেই। সাড়ে আট বছর বয়সে সত্যজিৎ ফিফথ ক্লাসে (ক্লাস সিক্স) ভর্তি হয়েছিলেন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। আজকের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ১৯২৯-এর বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের আকাশপাতাল তফাৎ। শ্রেণিচরিত্রে। বেলতলা রোডের এই বাংলা মাধ্যম স্কুলে অধিকাংশ ছাত্রই আজ আসে নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। প্রায় একশো বছর আগে কিন্তু এই স্কুলে পড়তে আসত দক্ষিণ কলকাতার প্রায় সমস্ত বনেদি বাড়ির ছেলেরা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনী ‘বাঙালনামা’য় জানিয়েছিলেন বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে বালিগঞ্জের ছাত্রদের ট্যাঁশপনায় তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজিতেই কথা বলত, সিগারেট খাওয়া এবং অন্যান্য বাবুয়ানি উঁচু ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেদের মধ্যে দেখা যেত। পারিবারিক অর্থবল প্রকাশ্যে দেখাতেও বহু ছেলে এবং তাদের বাপমায়েরা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সত্যজিৎ নিজেও ‘যখন ছোটো ছিলাম’ বইতে সে কথা লিখে গেছেন। এরকমই এই ছাত্র, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিনহার নাতি অনিল গুপ্ত ছিলেন সত্যজিতের সহপাঠী। এবং এই অনিল গুপ্তর দৌলতেই সত্যজিতের পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সঙ্গীতে হাতেখড়ি সেই হাইস্কুল থেকেই। তেরো বছর বয়স থেকে অনিল এবং সত্যজিৎ মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতার দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়াতেন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল গানের রেকর্ড। বিঠোফেনের ফিফথ সিম্ফনি তাঁরা শুনেছেন এই সময়ে। এবং সেখানেই থামছেন না তাঁরা। প্রথমে অনিল এবং তারপর অনিলের উৎসাহে সত্যজিৎ-ও পড়ে ফেলছেন অ্যান্টন শিন্ডলারের লেখা বিঠোফেনের জীবনী। এর পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকদের অবদানও মনে রাখতে হবে। সত্যজিতের মাস্টারমশাইরা স্কুলেই সাহেবি উচ্চারণে পড়াচ্ছেন বিদেশি ক্লাসিক আইভ্যান হো, ইংরেজি কথোপকথনে সামান্যতম খুঁত-ও যাতে না থাকে তা সুনিশ্চিত করছেন, কিশোর সত্যজিৎ জেনে যাচ্ছেন ভাওয়েল-এর আগে the-র উচ্চারণ হবে দি, আর কনসোনেন্টের আগে দ্য। ইংরেজি শব্দের যে দীর্ঘায়িত উচ্চারণে সত্যজিৎ হাজার হাজার মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন, তার হাতেখড়ি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের সেই সাহেবি অলিন্দেই। সময় সময় সেই বিলিতি ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর বাংলা উচ্চারণেও।
আরও পড়ুন : সুরের সত্যজিৎ (দ্বিতীয় পর্ব) / প্রতিষ্ঠা আচার্য, সৃজিতা সান্যাল
পাশ্চাত্য এবং ভারতীয়, দু-ঘরানার ধ্রুপদি সঙ্গীতকেই সত্যজিৎ অনায়াসে তাঁর চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন। ফরাসি চিত্র-পরিচালক পিয়ের-আন্দ্রে বোটাঙ্গকে ১৯৮৯ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন বাঙালি বা ভারতীয়রা যে মিশ্র সংস্কৃতিতে জীবনযাপন করেন তাকে ধরতে গেলে শুধু ভারতীয় সঙ্গীতের আশ্রয় নেওয়া সমীচীন হবে না। কিন্তু শুধুমাত্র মূর্ত আধুনিকতার প্রেক্ষিতেই পাশ্চাত্য সঙ্গীত সত্যজিৎকে প্রভাবিত করেনি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিমূর্ত এক প্রভাবও সত্যজিতের কাজে লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সঙ্গীত যেখানে সবসময়েই এক নির্দিষ্ট কাঠামো অনুরসণ করে, সেখানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কিন্তু অধিকাংশ সময়েই উদ্ভাবিত, সঙ্গীতজ্ঞর আশুরচনার ওপর দাঁড়িয়ে। সত্যজিতের চলচ্চিত্রই হোক বা ফিকশনাল লেখালেখি, এই নির্দিষ্ট কাঠামোটি সবসময়েই খুঁজে পাওয়া যাবে। এক হিসাবে বলা যায় এই নির্দিষ্ট কাঠামো সত্যজিতের কাজের ভিত্তি। ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেন তাঁদের কাজে যে improvisation এনেছেন, তা সত্যজিৎ সযত্নে বর্জন করে এসেছেন। কারণ সত্যজিতের কাছে একটি গল্প মুনশিয়ানার সঙ্গে বলে উঠতে পারার গুরুত্ব অনেক। তিনি জানতেন অকারণ বা অপটু আশুরচনা গল্পের গতিকে ব্যাহত করতে পারে, বিষয়বস্তুর থেকেও অনর্থক গুরুত্ব দিয়ে ফেলতে পারে গঠনশৈলীকে। চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীত, দুই-ই সময়নির্দিষ্ট বলে ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যবহার সত্যজিতের কাছে ছিল মূলত আলঙ্কারিক। পিয়েরকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ নিজেই জানিয়েছিলেন সে কথা।
সত্যজিৎ জন্মেছিলেন ১৯২১ সালে। তার দশ বছর আগেই কলকাতা খুইয়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীর মর্যাদা। কিন্তু বেড়ে ওঠার বছরগুলিতে সত্যজিৎ যে ঔপনিবেশিক শহরকে দেখেছিলেন তা স্পষ্টতই তাঁর মনে দাগ কেটে গেছিল। এবং সে কলকাতা শুধু ঔপনিবেশিক নয়, বহু সংস্কৃতির রসধারায় পরিপুষ্ট এক শহর। সে শহরে তখনও বসবাস করছেন আর্মেনিয়ান এবং গ্রিকরা। তখনো বহু ব্যবসার মালিকানা রয়েছে ইহুদিদের হাতে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ভারতীয় সমাজে প্রান্তবাসী হতে তখনও বহু দেরি। ফলে ষাট কি সত্তরের দশকেও সত্যজিতের গল্পের চরিত্ররা অ্যারাটুন ব্রাদার্সের নিলামে অংশগ্রহণ করছেন, বসবাস করছেন ল্যান্সডাউন রোড বা রডন স্ট্রিটে, গ্যারাজে রাখছেন লাগান্ডা বা শেভ্রোলে গাড়ি। ফেলুদা-ও ‘মিত্র’ এবং Mitter পদবির সমব্যবহারে রীতিমতো অভ্যস্ত। তার স্রষ্টার মতনই। বাবা সুকুমার রায় হয়ে থাকলেও সত্যজিৎ রায়ের থেকেও যেন বেশি ‘রে’। বিদেশি গাড়ির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। হাতেগোনা যে কটি বিষয়ে সত্যজিৎকে আমরা স্মৃতিমেদুরতায় ভুগতে দেখেছি তার মধ্যে একটি হল এই বিদেশি গাড়ি। তাঁর স্মৃতিকথার প্রথম অনুচ্ছেদেই খান ষোলো গাড়ির নাম নিয়েছিলেন সত্যজিৎ। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বিলাসবহুল গাড়ি চড়ার সৌভাগ্য বা সাধ কোনোটাই বিশেষ চোখে পড়ে না। এবং তিনি যে অনাড়ম্বর, স্পার্টান জীবনযাপন করেছেন তার সঙ্গে হয়ত অ্যাম্বাসাডর ব্র্যান্ডের গাড়িই খাপ খায়। তাই এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না বিদেশি গাড়ি নিয়ে সত্যজিতের স্মৃতিমেদুরতার মূল কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর এক আত্মিক সম্পর্ক। রায়পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্দশার দিনেও সত্যজিৎ দক্ষিণ কলকাতার এক বনেদি পাড়ায় থেকেছেন। ছুটির দিন হলেই বেরিয়ে পড়েছেন মধ্য কলকাতা সফরে, যেখানে ব্রিটিশ স্থাপত্যকলা অমলিন শোভাবর্ধন করেছে। স্বাধীনতা আসতে তখনও এক দশকের বেশি সময় বাকি। সাতচল্লিশের পরপরেই আমরা নান্দনিকতার তোয়াক্কা না করে মধ্য কলকাতায় একের পর এক অফিসবাড়ি বানিয়েছি, যা গরিব দেশের পড়তায় পোষালেও এমনকি টিঁকে থাকা ব্রিটিশ স্থাপত্যকলাকেও অসুন্দর করে তুলেছে। সেই দিন, সেই যুগ দেখে ব্যক্তি সত্যজিৎ এবং তাঁর শিল্পী সত্তা যে যারপরনাই দুঃখিত হয়েছিলেন সে কথা ভেবে নেওয়াই যায়।
আরও পড়ুন : একটি নীল রঙের খাতা আর সত্যজিতের লেখা বড়দের গল্প / বিবস্বান দত্ত
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এই আত্মিক সম্পর্ক নিয়ে সত্যজিৎ যে খুব একটা রাখঢাক করেছেন তাও নয়। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর সিনেমার প্রকৃত বোদ্ধা পশ্চিমী দর্শকরা। ভাষাগত কারণে ভারতের অন্য রাজ্যে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছনোর সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। বাংলায় তিনি অবিসংবাদিত ইন্টেলেকচুয়াল, বিশ্ববরেণ্য পরিচালক। কিন্তু সাধারণ দর্শকের ওপর তাঁর আস্থা বিশেষ ছিল না। পরিচালকের নাম না সিনেমার গুণগত মান, কোনটি তাঁর জয়ধ্বজা ওড়াচ্ছে সে নিয়ে সম্ভবত এক সংশয় তাঁর মনে ছিল। মনে রাখা ভালো বক্স অফিসের নিরিখে বাংলাতেও কিন্তু তাঁর সাফল্য জোরদার নয়। ফেলুদা এবং প্রোফেসর শঙ্কু না এলে শেষ জীবনে হয়তো সত্যজিৎকে অর্থচিন্তাতেও পড়তে হত। বিজয়া রায়ের আত্মজীবনী ‘আমাদের কথা’ পড়লে সে কথা বেশ টের পাওয়া যায়। বার্লিন থেকে ভেনিস, লন্ডন থেকে কার্লোভি ভেরি, একের পর এক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সত্যজিতের সাফল্য অর্থচিন্তা দূর না করলেও তাঁকে বিশ শতকের এক অন্যতম শিল্পী হিসাবে সারা পৃথিবীতে মর্যাদা দিয়েছে। এবং বহু সময়েই দেখা গেছে নিজের দেশের পুরস্কার এসেছে বিদেশি পুরস্কারের লেজুড় হয়ে। কিন্তু কেন এসেছে এই সাফল্য? গত ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমী চিত্রসমালোচকরা সত্যজিতের কাজ নিয়ে যা লেখালেখি করেছেন তা পড়লে কতকগুলো কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে – সত্যজিৎ মেলোড্রামাকে সচেতনভাবে বর্জন করেছেন, স্থান এবং কালের বিস্তৃত ব্যবহারে তিনি মননশীল দর্শকের ক্রমাগত মনোযোগ দাবি করেছেন, এবং চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে দৃশ্যপট, সবর্ত্র তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর এক অভাবনীয় উৎকর্ষের সন্ধান দিয়েছে। এক কথায় সংযত, মেধাবী, পরিশ্রমী এক মানুষকে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন এক অপরিচিত সমাজে। পশ্চিমী চিত্রকলা, পশ্চিমী সাহিত্য, পশ্চিমী ইতিহাসবর্ণন, এই সব জায়গাতেই সংযম, মেধা ও পরিশ্রম সেই নবজাগরণের সময় থেকেই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এবং তিনটি গুণের সমন্বয় চট করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, সে কথা এই সমালোচকরা ভালোভাবেই জানেন। এ কথা মনে করার কারণ অবশ্যই নেই যে এর কোনও একটিতে কমতি পড়লেই প্রতিভার উন্মেষ ঘটবে না। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় মেলোড্রামা পশ্চিমী দুনিয়া সেভাবে গ্রহণ না করলেও স্বয়ং সত্যজিৎ বলেছেন সেই আঙ্গিকের হিসাবে ঋত্বিকের সিনেমাগুলি সার্থকভাবে ভারতীয় হয়ে উঠেছে। আবার এই তিনটে গুণের বাইরেও কিছু চাহিদা থাকতে পারে। যেমন রাজনৈতিক সচেতনতা বা রাজনৈতিক আধুনিকতা। যে কারণে ত্রুফোর মতন বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক সত্যজিতের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। তাঁর কাছে সত্যজিতের কাঠামোটি এক ঔপনিবেশিক কাঠামো, যা যথেষ্ট আধুনিক তো নয়ই বরং উত্তর-ঔপনিবেশিক শিল্পচর্চার প্রতিপন্থী।
কিন্তু মোটের ওপর সত্যজিতের মধ্যে পশ্চিমী চিন্তাবিদরা নিজেদের সমধর্মী বিদ্বজ্জনকেই খুঁজে পেয়েছেন। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সময়, ভিন্ন সমাজ বিষয়বস্তু হলেও যে উৎকর্ষের সন্ধান সত্যজিৎ করেছেন তার সঙ্গে পূর্বতন পরিচয় আছে এই মানুষগুলির। আবার উল্টোদিকে সত্যজিৎ-ও নিজের জীবনীকার অ্যান্ড্রু রবিনসনকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে জানিয়েছেন ইওরোপীয় সাহিত্য, ইওরোপীয় শিল্পকলা বা পাশ্চাত্য সঙ্গীত তাঁর একটিবারের জন্যও বিদেশি লাগেনি। এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতেও এহেন স্বীকারোক্তি কিন্তু সহজে মেলা ভার।

ঠিক কী খুঁজে পেয়েছিলেন সত্যজিৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে? সম্ভবত এক উন্নত কিন্তু মানবিক সমাজচেতনা যা পরাধীনতার গ্লানির মধ্যেও কিছু নতুন আশা জাগিয়েছিল। এবং এই আশা সবথেকে বেশি মূর্তমান তাঁর সিনেমার নারীচরিত্রগুলির মধ্যে। করুণার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। যে আত্মনিয়ন্ত্রণ করুণা দেখিয়েছেন তা এক উন্নত সমাজচেতনারই প্রতিফলন। কিন্তু করুণাতেই তো শেষ নয়। ‘মহানগর’-এর আরতি (মাধবী মুখোপাধ্যায়) চরিত্রটির কথা ধরুন। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আনার জন্য যে আরতি নির্দ্বিধায় চাকরি করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনিই তাঁর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সহকর্মীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনায়াসে সে চাকরি ছেড়ে দেন। এ সিনেমা কিন্তু ষাট সালের। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ততদিনে ভারতীয় সমাজে প্রান্তবাসী হতে শুরু করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের উপেক্ষা হোক বা সংসার বাঁচানোর তাড়না, দায় এড়ানোর অজুহাত তো কতই ছিল তাঁর। কিন্তু সত্যজিতের সমাজে আত্মত্যাগী আরতিরা অপরিহার্য, কসমোপলিটান কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হোক বা এক সার্থক উত্তর-ঔপনিবেশিক শহর গড়ে তুলতে। এই সার্থক নির্মাণে মানবিকতার অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কিন্তু অনুভূতির প্রবল বহিঃপ্রকাশে সেই সার্থকতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। মনে পড়ে যায় আরেক নায়িকা অদিতির কথা (‘নায়ক’), অরিন্দমের একাকিত্ব সে টের পায়। ব্যথিত হয়। কিন্তু সে ব্যথার প্রাবল্যে অদিতি আত্মসমর্পণ করে না। প্রেমের থেকেও বড়ো হয়ে দাঁড়ায় মানবিকতা, এক মানুষের আরেক মানুষকে বোঝার সদিচ্ছা। এই সংযমটুকুই শেখার। সত্যজিৎ শিখেছিলেন। তাঁর কাজ থেকে আমরা শিখব, শিখবে আগামী প্রজন্ম, সত্যজিতের জন্মশতবার্ষিকীতে এর থেকে বেশি আর কীই বা চাওয়া যায়।
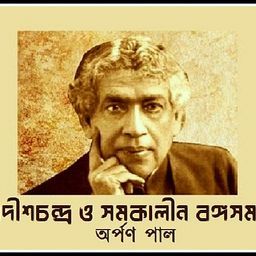
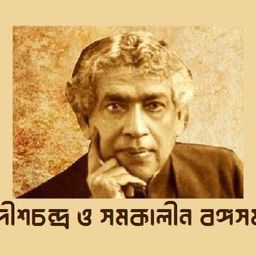
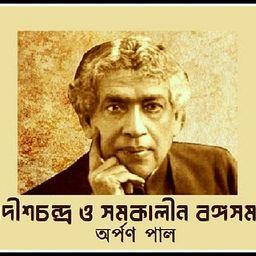
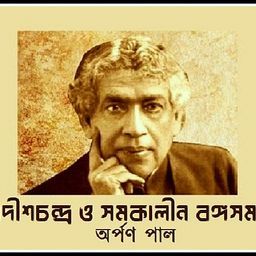
সরোজ দরবার
চমৎকার উপভোগ্য আলোচনা। আপনার লেখা একটা বড়ো ক্যানভাসের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে হয়। সত্যজিতের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাবটি কিছুটা রবীন্দ্রনাথ থেকেও সঞ্চারিত। বিরক্ত তরুণ রবীন্দ্রনাথকে একবার বেশ রাগতস্বরেই বলতে শোনা যায় যে, বাঙালির কাছে সব বৃহৎ ভাব যেন শেষমেশ স্ল্যাং হয়ে যায়। বৈষ্ণব আন্দোলনের পরিণতি নিয়ে ছিল তাঁর এই বক্তব্য। প্রায় একইরকম বিরক্তি সত্যজিতেও পাই, যখন সেই প্রথম বাংলা ছবিতে পা ঘষা জাতীয় দৃশ্য দেখছেন তিনি। পরিমিতি, সংযমের মধ্যেই যে বৃহতের মর্যাদা - এরকম একটা উপলব্ধির জায়গা দুজনের ক্ষেত্রেই পাই। যেমন, আর একটা প্রসঙ্গ - চারুলতার একা শোকপ্রকাশ মুহূর্তে ভূপতির উপস্থিতিকে একরকম নাকচ করছেন রবীন্দ্রনাথ। তীব্রভাবেই করছেন। অথচ শোকপ্রকাশের এই রীতি তো ঠিক আমাদের নয়। একজন কাঁদলে এখানে পাঁচজন হাউহাউ করে ওঠে। দুর্গার মৃত্যুর পর তাই কান্নার বদলে যখন যন্ত্র বেজে ওঠে, আমার খুব মনে হয়, সেটা যেন ওই একা ব্যক্তিগত শোকপ্রকাশের চলচ্চিত্রিত সংযোজন হয়ে উঠছে। ঋত্বিকের মেলোড্রামাটিক অভিব্যক্তির একেবারে বিপরীত কোটিতে যার অবস্থান। এমনকি সমাপ্তিতেও মেয়েটিকে বিষণ্ণ মুহূর্তে একা একা নদীর ঘাটে বসে থাকতে দেখা যায়, দোলনায়। যদিও, সেখানে বাবার একটা সংযোগ ছিল।মনে হয়, শোক যে একার, এই ব্যাপারটিও ওখানে রয়ে আছে। রবি ঠাকুরের সন্দীপ-নিখিলেশকে গড়া আর সত্যজিতের ঘরে বাইরে নির্বাচনও এর একটা ইঙ্গিত বলে মনে হয়। আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে অধ্যয়নও সত্যজিতকে এই নিয়ন্ত্রণ, সংযম, মিতকথনের দিকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। যা আসলে, আপনি যেমনটা বলেছেন, মানবতা ও উন্নততর সমাজচেতনার দিকেই আমাদের এগিয়ে দেয়।