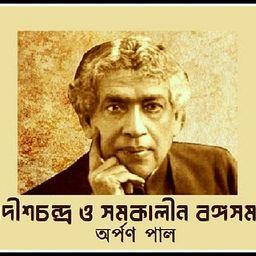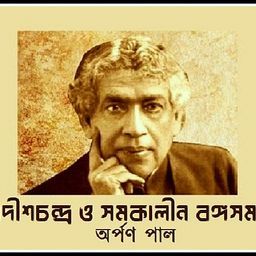জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ (নবম পর্ব)
_1366x1366.jpg)
...............
পর্ব ৯। দেশে ফেরবার পর কয়েক বছরের যৌথ কর্মকাণ্ড
বিলেত থেকে জগদীশচন্দ্রর সস্ত্রীক দেশে ফেরবার বেশ কয়েক মাস আগেই, ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে মাদ্রাজের বন্দরে পৌঁছলেন নিবেদিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত আর মিসেস সারা বুলকে সঙ্গে নিয়ে। ‘মম্বাসা’ জাহাজ থেকে বন্দরে নামবার পরের দিনই মহাজন-সভা হলে তাঁকে এবং রমেশবাবুকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এই সংবর্ধনার সময় নিবেদিতা যে বক্তৃতা দেন, সেখানে তিনি জগদীশচন্দ্রর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন: ‘...অতঃপর হিন্দু জীবন ও চিন্তাধারার আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর জে. সি. বোসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উল্লেখপূর্বক নিবেদিতা বলেন, ‘স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ব্যাপারে আপনারা দাতা, পাশ্চাত্যের নিকট আপনাদের শেখবার কিছু নেই। সামাজিক ব্যাপারেও সেইরকম। ...’ (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-র নিবেদিতা জীবনী, ২১১ পৃ)
দীর্ঘদিনের বিদেশ-সফর সেরে কলকাতায় ফেরবার পর নতুন করে আবার কাজের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবেদিতা। স্কুল খোলবার তোড়জোড় চলতে লাগল, পাশাপাশি তিনি ব্যস্ত রইলেন বাড়িতে আসা বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের আপ্যায়ন করতে। এইসময় নিবেদিতার সঙ্গে প্রায় নিয়মিতই সাক্ষাৎ করতে আসতেন রমেশচন্দ্র, আনন্দমোহন বসু, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, একদিন এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধীও। তাঁর বোসপাড়ার বাসা যেন একটানা আন্দোলিত হতেই লাগল সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের চঞ্চলতার ঢেউয়ে।
অন্যদিকে এইসময় নানারকম শারীরিক অসুস্থতায় জেরবার ছিলেন স্বামীজী। যে কারণে তিনি বেশ কয়েক দিন কাটিয়েছিলেন কাশীতে, গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে। সেখান থেকে বেলুড়ে ফেরেন মার্চের ১১ তারিখে। মঠের নানা কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেও তিনি মনে মনে যেন টের পাচ্ছিলেন, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে। কদিন মিস ম্যাকলাউডকে ডেকে বলেন, ‘আমি কখনও চল্লিশে পৌঁছাব না।’ (মুক্তিপ্রাণার নিবেদিতা জীবনী, ২১৫ পৃ)
১৯০২-এর এপ্রিল মাসের সাত তারিখে কলকাতায় এলেন স্বামীজীর আর এক অন্তরঙ্গ শিষ্যা ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল। জার্মানির ন্যুরেমবুর্গে তাঁর জন্ম, বয়সে তিনি ছিলেন নিবেদিতার চেয়ে এক বছরের বড়, আর নিবেদিতার মতোই প্রথম দিকে তিনি স্কুলেই পড়াতেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ১৮৯৬ সালে আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে, এবং ওই আলাপের আগে-পরে স্বামীজীর বেশ কয়েকটি বক্তৃতা শোনবার পর তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন স্বামীজীর প্রতি। পরে নিবেদিতার মতোই সিদ্ধান্ত নেন ব্রহ্মচর্য নিয়ে ভারতে চলে আসবেন, এখানেই বাস করবেন পাকাপাকিভাবে। সেইমতো কলকাতায় এসে তিনি নিবেদিতার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়েন নানা কর্মকাণ্ডে। স্কুলের মেয়েদের কাছে নিবেদিতা ছিলেন সান দিদি আর ক্রিস্টিন মুন দিদি। ছাত্রীদের সেলাই শেখানোর কাজ খুব ভালো পারতেন ক্রিস্টিন, স্বামীজী তাঁকে মনে করতেন যে ‘She is pure in soul, I knew it, I felt it.’
প্রবল গরমের কারণে ১৯০২-এর মে মাসে গরমের ছুটিতে নিবেদিতা-ক্রিস্টিন যাত্রা করলেন মায়াবতীর উদ্দেশ্যে। সঙ্গী হলেন জাপানি শিল্পী কাকুজো ওকাকুরা এবং আরও কয়েকজন। সেখানে প্রকৃতির কোলে বেশ কয়েকদিন সুখে অতিবাহিত করবার পর নিবেদিতা কলকাতায় ফিরলেন জুনের ছাব্বিশ তারিখে। দু-দিন পর, আঠাশ তারিখে স্বামীজী এলেন বোসপাড়ায়। সেদিন খাওয়াদাওয়ার পর স্বামীজী নিজের হাতে নিবেদিতার হাত ধুইয়ে দেন, যে ঘটনা নিবেদিতাকে মনে করায় যিশুর জীবনের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে একইভাবে শিষ্যের হাত ধুইয়ে দেওয়ার সেই প্রসঙ্গকে।
বেলুড় মঠে নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর শেষ সাক্ষাৎ জুলাইয়ের ২ তারিখে। স্বামীজী মনে-মনে নিশ্চয়ই তখন আসন্ন বিদায়ের পদধ্বনি টের পাচ্ছিলেন, নইলে কেনই বা বলবেন, ‘আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে।’ (মুক্তিপ্রাণা, ২১৭ পৃ) সেদিন নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর আরও একটি বিষয়ে আলোচনা হয়। তাঁর স্কুলটিতে বিজ্ঞানের কোনো বিষয় পাঠ্য হিসেবে রাখবেন কি না, এটাই ছিল আলোচ্য। মুক্তিপ্রাণা জানাচ্ছন, ‘বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার তখন একটা বিশেষ ঝোঁক আসিয়াছে; শ্রীযুক্ত বসুর সহিত আলাপ-আলোচনার ফল। নিবেদিতার যুক্তিগুলি শুনিয়া স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর দিলেন, ‘তোমার কথা ঠিক হতে পারে, কিন্তু এসব ব্যাপার আমি আর আলোচনা করতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলেছি।’ (মুক্তিপ্রাণা, ২১৮ পৃ)
জুলাইয়ের চার তারিখ ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সেইদিন রাত্রি ন’টার সময় ঘুমের মধ্যেই প্রয়াত হলেন স্বামীজী। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর। নিবেদিতা সেদিন ছিলেন বাগবাজারেই। ভোরবেলা তাঁর কাছে চিঠি এল বেলুড় থেকে, চিঠির বক্তব্য পড়ে যেন চেতনা লোপ পেল তাঁর। তবু নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করে নিবেদিতা তক্ষুনি রওনা দিলেন বেলুড়ের দিকে।
স্বামীজীর মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা
ক. জগদীশচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া
স্বামীজীর প্রয়াণের সময় জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিলেতেই। ওখান থেকে তাঁর লেখা দুটো চিঠি পাওয়া যায় যাতে স্বামীজীর প্রসঙ্গ রয়েছে; একটি সারা বুল-কে লেখা, অন্যটি নিবেদিতাকে। প্রথমটি এই:
8th July, 1902
It seems to me that nothing is lost and all the great thoughts and work and service and hope remain embodied in and about the place which gave them birth. All our life is but an echo of a few great moments, an echo which reverberates through all time... That great soul [of Swami Vivekananda] is released; his heroic deeds on this earth are over. Can e realise what that work has been— how one man did all this? When one is tired it is best that he should sleep, but his deeds and teachings will walk the earth and waken and strengthen.
দ্বিতীয় চিঠিটা এইরকম:
LONDON July, 9th, 1902
...What a void this makes! What great things were accomplished in these few years! How one man could have done it all! And how all is stilled now. And yet, hen one is tired and weary, it is best that he should rest. I seem to see him [Swami Vivekananda] just as I saw him in Paris two years ago... the strong man with the large hope, everything large about him.
I cannot tell you what a great sadness has come. I wish we could see beyond it. Ou thoughts are in India with those who are suffering. (এই দুটি চিঠি Letters of Sister Nivedita vol 1, 529 pp. থেকে নেওয়া)
খ. নিবেদিতার বেলুড় মঠ ত্যাগ
স্বামীজীর প্রয়াণের পরের দিন নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, ‘Swami Died’, স্বামীজী নেই। বৃহত্তর জগতে এর আগেই পা বাড়িয়ে রেখেছিলেন, এবার নিবেদিতার কর্মময় জীবন যেন নতুন এক মাত্রা পেল।
এটাই তাঁর ভারতীয়-জীবনের তৃতীয় পর্ব। এর আগেই তিনি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর মনোজগতের। তাঁর গবেষণাগারে বহু সময় কাটিয়েছিলেন, পারিবারিক একটা বন্ধন তৈরি হয় গিয়েছিল বসু দম্পতির সঙ্গে। এই দম্পতি ছাড়াও ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত অন্যান্য আরও ব্যক্তিদেরকেও বেশ পছন্দ করতেন নিবেদিতা, এখন তাঁদের সঙ্গেও মেলামেশা বৃদ্ধি পেল, অন্যদিকে রামকৃষ্ণ মিশন নিজেকে পুরোপুরি রাজনীতির সংস্রবমুক্ত রাখতে চায়, নিবেদতার কিছু কর্মকাণ্ড তাদের ক্ষুণ্ণ করে তুলল।
এরই ফলশ্রুতি, জুলাইয়ের ১৯ তারিখে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে জানানো হল যে এর পর থেকে নিবেদিতার কাজকর্মের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন বা মঠের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তিনি যা-কিছু করবেন সে সবই হবে পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তে, সে সব ব্যাপারে মিশনকে কোনোভাবে জড়াবেন না তিনি। এরপরেই তাঁর ভারত-সফরের আরও এক অধ্যায়ের শুরু।
নাগপুর-বোম্বে থেকে শুরু করে বরোদা, আমেদাবাদ, ইলোরা ইত্যদি স্থান ঘুরে নিবেদিতা কলকাতায় ফেরেন নভেম্বর মাসে। প্রত্যেক বক্তৃতার বিষয়বস্তু স্বামীজী আর ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের মুগ্ধ বিবরণ। তখনও নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে নেননি।
এরপরে আবার দক্ষিণ ভারত। ওই বছরের ডিসেম্বরেই। বেশ কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার পর কলকাতায় ফিরে আসা, এবং নিজের তৈরি করা স্কুলটিকে নিয়ে আবার লেগে পড়া। টাকার টানাটানি, কীভাবে আসবে প্রয়োজনীয় অর্থ, তা নিয়ে চিন্তায়-চিন্তায় জেরবার। নতুন বই লিখে কিছু অর্থাগম হতে পারে, এই ভেবে হাত দিলেন ‘দ্য ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ’ নামে বই লেখায়। কিন্তু কলকাতায় বসে লেখার ক্ষেত্রে মূল সমস্যা ব্যাস্ততা, আর অভাব একাগ্রতার। নির্জনতার খোঁজে তাই যাত্রা করলেন দার্জিলিং। ফিরলেন বইয়ের পাণ্ডুলিপি রেডি করে। সেই বই প্রকাশ পেল ১৯০৪-র মাঝামাঝি। বইটির ভূমিকা লিখে দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জগদীশ-অবলার সন্তান-প্রসঙ্গ
অবলা বসুর সন্তানসম্ভবা হওয়া নিয়ে নিবেদিতা যে যথেষ্ট উত্তেজিত এবং আনন্দিত ছিলেন, তা প্রকাশ পায় মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ১৯০৩-র ২৩ এপ্রিল তাঁর চিঠির বিভিন্ন অংশ থেকে:
‘তোমাকে বলেছি কি, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মিসেস বসুর সন্তান হতে যাচ্ছে! অপূর্ব নয় কি ব্যাপারটি!
আরও একটি চিঠিতে দেখি:
‘তোমার ভালোবাসা বে-আনকে (জগদীশচন্দ্র) দিয়েছি, তোমাকে সে তার ভালোবাসা জানাচ্ছে। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে। ছোট্ট বউটি, বলব কি মাতৃত্বে একেবারে জ্যোতির্ময়ী। যেকোন দিনই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা। তার দর্শন পেতে আমার ব্যাকুলতার কথা কি করে বোঝাই বল!’
এরপর এসে গেল ১৯০৩-এর মে মাস। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মে মাসের পনেরো তারিখ বৃহস্পতিবার, একেবারে মাঝরাতে এক মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করলেন অবলা। সদ্যজাত মেয়ের মৃত্যুজনিত শোক কাটিয়ে উঠতেই আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসের দিকে দিন কয়েকের জন্য দার্জিলিং যাত্রা করলেন জগদীশচন্দ্র-অবলা। সঙ্গী হলেন নিবেদিতা। তাঁর ইচ্ছে, ওখানে গিয়েই নিরিবিলিতে তিনি তাঁর ‘ওয়েব অভ ইন্ডিয়ান লাইফ’ বইটা লেখবার কাজ গুছিয়ে সারবেন।
দার্জিলিং থেকে ফিরে আসবার পর ওই ১৯০৩-এরই নভেম্বরের ১৩ তারিখে শান্তিনিকেতনে আসেন জগদীশচন্দ্র। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন। দিন তিনেক বাদে তাঁরা একসঙ্গে কলকাতায় ফেরেন।
পরের বছর, গরমের ছুটিতে নিবেদিতা বসু-দম্পতিকে নিয়ে যাত্রা করলেন মায়াবতীর উদ্দেশ্যে। সঙ্গে গেলেন সিস্টার ক্রিস্টিন। এই মায়াবতীতেই জগদীশচন্দ্র শুরু করেন তাঁর দ্বিতীয় বই ‘প্ল্যান্ট রেসপন্স অ্যাজ আ মিনস অভ ফিজিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন’ লেখবার কাজ।
১৯০৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে নিবেদিতা জড়িয়ে পড়েন আরও এক বিতর্কিত বিষয়ের সঙ্গে। সেই ঝামেলার মিটমাট করতে তাঁর যে সফর, তাতে সঙ্গী হবেন সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথও। তবে সে আলোচনা, পরের পর্বে।
........................