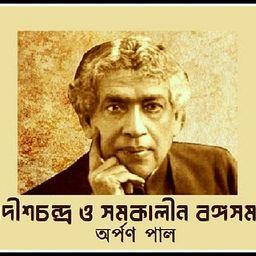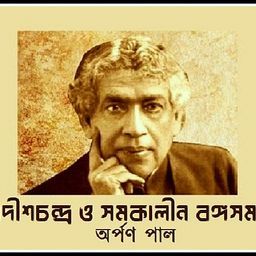ভাবের ঘরে জালিয়াত, অঙ্কের চালে কুপোকাত

ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা তো করেন, মাস গেলে এটিএম থেকে টাকাও তোলেন। শুধু সরাসরি লেনদেন নয়, মোবাইল ফোন থেকে টিকিট কাটা, জামাকাপড় কেনা, যাবতীয় সবরকম আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন শুধুমাত্র ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর পরিষেবার উপর ভরসা করে। আর এইসব জায়গায় সুরক্ষার চাবিকাঠি আপনার পিন নম্বর। কিছু শুভানুধ্যায়ী আছেন আমাদের জীবনে, মাঝেমাঝেই বিবিধ মেসেজ পাঠিয়ে জানান, আপনার অ্যাকাউন্ট এই বন্ধ হল বলে কিংবা আপনি এই দশলাখি লটারি জিতলেন বলে, শুধু পিন নম্বরটা বললেই... । কেন পিন নম্বর হাতাতেই এত এত উৎসাহ? আপনার বেচাকেনা, অ্যাকাউন্ট ইত্যাদির যাবতীয় তথ্য তো ইন্টারনেটেই মজুত, আর সে এক প্রকৃত মুক্ত বিশ্ব। হ্যাকার তো চাইলেই সে সব তথ্য পড়ে নিতে পারে এক লহমায়। পারে না, কারণ সমস্ত আর্থিক লেনদেনের তথ্য রাখা থাকে এনক্রিপশনের মোড়কে। কোনও তৃতীয় পক্ষ যদি সে তথ্য দেখেও নেয়, তার মর্ম উদ্ধার করার উপায় তার হাতে নেই। আপনার তথ্য আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে অন্যের ঘরে পোঁছনোর মাঝে তাকে সাংকেতিক জগাখিচুড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়।
সংকেত ব্যবহার করে বার্তা পাঠানোর তত্ত্ব আধুনিক যুগের আবিষ্কার নয়, প্রাচীন কাল থেকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ চলে আসছে। শুরুতে ধাঁধা বা হেঁয়ালির মারফত তা করা হলেও অচিরেই তার জায়গা নেয় গাণিতিক সংকেত। অপরাধী বুদ্ধিমান হলে হেঁয়ালির উত্তর বের করা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু যদি এমন সংকেত ব্যবহার করা হয় যার জ্ঞান শুধু প্রেরক আর প্রাপকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহলে তৃতীয় কারও পক্ষে সেই বার্তার পাঠোদ্ধার করা মুশকিল হয় বই কি। প্রাচীনতম সংকেতের মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত “সিজার সাইফার”, যা রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রথম চালু করেন গ্যালিক যুদ্ধের সময়ে শত্রুর নজর এড়িয়ে নিজের নির্দেশ প্রেরণের জন্য। তখন রোমান বর্ণমালার এক একটি অক্ষরকে তার কয়েক ঘর পরের অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হত। সাংকেতিক বার্তা যিনি পাচ্ছেন, তাকে শুধু জানতে হত ঠিক কত ঘর পিছিয়ে শুরু করতে হবে। এবার মুশকিল হল সেই রোমান থেকে হালের ইংলিশ, মোটে ২৫টা বর্ণ – অর্থাৎ সবচাইতে বেশি পিছোতে পারবেন কোনও অক্ষরের পরের পঁচিশ ঘর অবধি। আপনার বাড়ির কম্পিউটারের কাছে সে হিসেব তো নস্যি। তাই নতুন যুগের প্রয়োজনে অক্ষরের জায়গা নিয়েছে মৌলিক সংখ্যা আর তাকে এলোমেলো করে সাজানোর পোশাকি নাম হয়েছে এনক্রিপশন। কিভাবে কাজ করে এই এনক্রিপশন? শুরুর দিকে তার কাজের ধরন ছিল অনেকটা সিজার সাইফারের মতোই। সংকেত ভাঙ্গাগড়ার একটাই চাবিকাঠি, যা শুধু প্রেরক-প্রাপকের মধ্যেই গোপন থাকল। এই পদ্ধতির প্রথম সার্থক রূপকার আমেরিকার Data Encryption System (DES), তাদের চাবিকাঠির মান ছিল ৫৬ বিট বাইনারি অর্থাৎ ১ আর ০ মিলিয়ে মোট ছাপ্পান্ন অঙ্কের একটা সংখ্যা। এতদূর অবধি সবাই জানত, কিন্তু কোন জায়গায় কোন সংখ্যা ব্যবহৃত হচ্ছে তা জানার উপায় নেই। কারণ পিন কোড উদ্ভাবনের দায়িত্ব কম্পিউটারের, আর সে কাজ হবে কোনও নির্দিষ্ট ক্রম না মেনে। যেহেতু শুধু ১ আর ০ দিয়ে লেখা তাই যেকোনও সময়ে ২^৫৬ (২ এর ৫৬ ঘাত) সংখ্যক অঙ্কের যে কেউ পিন সংখ্যা হতে পারে। DES যখন চালু ছিল, তখন সবাই ভেবেছিল এতগুলো সংখ্যা ঝেড়েবেছে আসল পিন পাওয়া অতি ধুরন্ধরের পক্ষেও দুঃসাধ্য। কিন্তু ফ্লপি ডিস্ক থেকে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ অবধি যাত্রাপথে সে কাজ বালখিল্য হয়ে গেছে। তাহলে উপায়?

ধরুন, আপনি তৈরি করলেন এমন একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহার করে যে কেউ আগের মতোই সাংকেতিক ভাষায় আপনাকে তথ্য পাঠাতে পারবে, কিন্তু চাবিকাঠি একটা নয়, দুটো। সংকেত লেখার চাবিকাঠি রইল সবার হাতে, কিন্তু সংকেত ভেঙ্গে আসল কথাটি বের করার চাবিকাঠি শুধু আপনারই হাতে। যিনি পাঠাচ্ছেন, তিনিও প্রোগ্রামের তৈরি সংকেত আর ভাঙ্গতে পারবেন না। এই ধারণা প্রথম দেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তরুণ গবেষক মার্টিন হেলম্যান আর হুইটফিল্ড ডিফি, ১৯৭৬ সালে। তার অনতিকাল পরেই এমআইটির তিন গবেষক, আদি শামির, রোনাল রিভেস্ট আর লিওনার্ড অ্যাডলম্যান, এই ধারণাকে বাস্তবের রূপ দেন। তারা বলেন, সংকেত পড়ার চাবিকাঠি হতে পারে খুব বড়ো দুটো মৌলিক সংখ্যা। আর তা লেখার চাবিকাঠি? ওই দুটো সংখ্যার গুণফল। কারণ, কম্পিউটারের সাহায্যে অনেক অনেক বড়ো দুটো মৌলিক সংখ্যাকে সহজেই গুণ করে নেওয়া যায়, কিন্তু উলটো কাজটা অর্থাৎ গুণফলকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আবার ওই মৌলিক সংখ্যা দুটোয় ফিরে আসা কম্পিউটারের সাধ্যের অতীত। এমন কোনও গাণিতিক সমীকরণ আজ অবধি অনাবিষ্কৃত যা দিয়ে যে কোনও সংখ্যাকে তার মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যাবে। ফার্মার সেই বিখ্যাত শেষ উপপাদ্য এর কিছুটা ধারেকাছে আসে, তবে মৌলিক সংখ্যার জগতের এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পুরোপুরি অতিক্রম করা আজও বহু গণিতজ্ঞের স্বপ্নের গবেষণা। মজার কথা এই যে, অঙ্কের এহেন ব্যর্থতাই হয়ে উঠেছে আমাদের তথ্য-সুরক্ষার মূল ভিত্তি। ১৯৭৭ সালে এই প্রোগ্রামের কথা ঘোষণা করার সময়ে তিন গবেষক মিলে প্রথম চাবিকাঠি হিসেবে দিয়েছিলেন ১২৯ অঙ্কের একটা গুণফল, যার মূলে ছিল অজানা দুই মৌলিক সংখ্যা। তাঁরা খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানালেন, অন্য চাবিকাঠি, অর্থাৎ ওই দুই উৎপাদক খুঁজে বের করার জন্য। তৎকালীন কম্পিউটারের ক্ষমতা অনুযায়ী কোনও জিনিয়াস হ্যাকার একটা শক্তিশালী কম্পিউটিং সিস্টেম নিয়ে বসলেও কয়েকশো বছরের আগে সে হিসেব শেষ করে উঠতে পারত না। বাস্তবে অবশ্য এমনটা হল না। এমআইটি ও অক্সফোর্ডের কিছু গবেষক, দুনিয়া জুড়ে ৬০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে মিলে, প্রতিদিন ধরে চেষ্টা করে অত্যাধুনিক সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে সেই সংকেত ভেদ করতে পেরেছিলেন। তাতেও সময় লেগেছিল সতেরো বছর!
অঙ্ক যেখানে সমাধান দিতে অক্ষম সেখানেও সে অপরাধীকে মাত করে। আর যেখানে সে সক্ষম? সেই জায়গায় সে গোয়েন্দাদের সেরা হাতিয়ার। জটিলতম সমীকরণে সে বলে দেয় সিরিয়াল কিলারের সম্ভাব্য ঠিকানা। কীভাবে? সে কথা জানতে হলে পড়ে ফেলুন বইমেলায় প্রকাশিতব্য সিলি পয়েন্টের নতুন বই “ডিটেক্ট ইট” – বাস্তবের গোয়েন্দা আর গুপ্তচররা কীভাবে কাজ হাসিল করে, তারই বিভিন্ন পদ্ধতির বিশ্লেষণে ভরপুর এই কিতাব।
তবে আর দেরি কীসের?
.........
#encription #atm fraud #Data Encryption System #silly পয়েন্ট #digital fraud