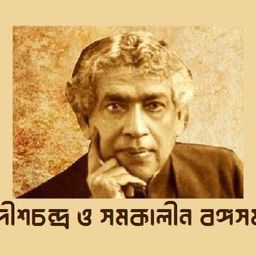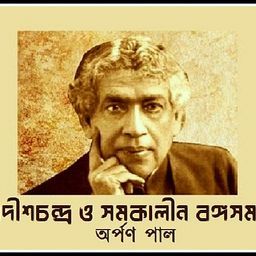পেন, স্ক্যালপেল, Life (দ্বিতীয় ভিজিট)
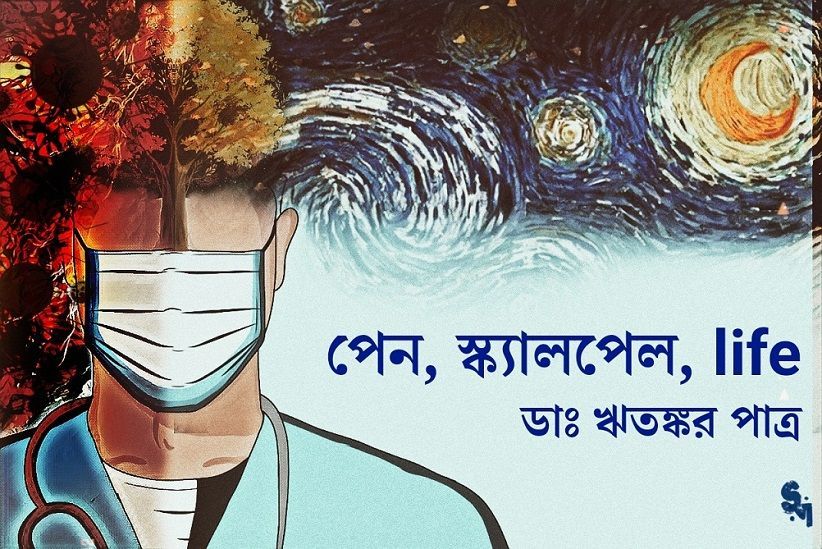
আমরা যখন ছোটো ছিলাম, নানান জিনিসকে জীবনের সার সত্য বলে ধরে নিতাম।
ক্লাস টেনে পড়ার সময় কারুর ল্যাপটপ দেখলে মনে হত আমাদের ওই জিনিসটা চাই - ওটাই জীবনের একমাত্র সত্য। আস্তে আস্তে বড় হতে হতে বুঝলাম, জীবনে সত্য মাত্র দুটোই - জন্ম আর মৃত্যু। এর বাইরে কিছু হয় না।
গত বছরের কথা। তখন সদ্য দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতকোত্তরে পা রেখেছি। লকডাউন চলছে। আউটডোরে একজন পেশেন্ট আসে। ১৭-১৮ বছর বয়েস। শরীরে থাবা বসিয়েছে ক্যান্সার। রেক্টাল বা মলদ্বারে ক্যান্সার। এসব ক্ষেত্রে আমরা ক্যান্সার কেটে মলত্যাগ করার রাস্তা আলাদা করে বানিয়ে ফেলি। সেখান দিয়ে সে সারাজীবন মলত্যাগ করে। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে ‘স্টোমা’। এখানে ছেলেটি যখন আসে, তখন বাইরে কোথাও থেকে স্টোমা করে এসেছে।
এইসব ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে পাঠিয়ে দিই রেডিয়েশান আর কেমোথেরাপির ঘরে, যাতে কেমো পেয়ে ক্যান্সারটা একটু ছোটো হয়ে যায় আর অপারেশানে সুবিধা হয়। ছেলেটা এসেছিল স্টোমাতে ব্যথা হচ্ছে বলে। দুদিন থাকে ব্যথা, ওষুধে কমে যায়। আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিই, সঙ্গে বলি - “কেমোর ডেট ভুলো না।”
এইভাবে কেটে যায় তিন সপ্তাহ। লকডাউন আস্তে আস্তে শিথিল হচ্ছে। সপ্তাহে এক কিংবা দুদিন লকডাউন চলছে। সেই সময় আবার ফিরে আসে ছেলেটা। ধরে নেওয়া যাক, ওর নাম আব্বাস। এবারে ছেলেটা ফিরে আসে আরো দুখানা স্টোমা নিয়ে। পেটের চারিদিকে চারখানা স্টোমা। ভীষণ অবাক হয়ে যাই। এরকম কী করে সম্ভব? বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করি, “এত স্টোমা কি করে হল? আর কোন হাসপাতালে করে দিল?” উত্তর আসে, "স্যার নার্সিংহোমে করিয়েছি। খরচায় আর পোষাতে পারছিলাম না।" আমি বলি, “না সেসব তো বুঝলাম, কিন্তু এত স্টোমা কী করে হল?”
"ক্যান্সার সব খেয়ে নিচ্ছে স্যার।"
"কেমো চলছে?"
"হ্যাঁ স্যার চলছে। কিন্তু কাজ তো কিছু হচ্ছে না।"
পেটে হাত দিয়ে চমকে যাই। নাভির তলা থেকে পুরো তলপেট যেন একটা শক্ত পাথর। যেন অনেক আগে থেকে সে বসে আছে ওইখানে। খুব অবাক হলাম। এত তাড়াতাড়ি কী করে ছড়িয়ে পড়ে ক্যান্সার? মাত্র তিন সপ্তাহ। তাও কেমো চলছে। আমি মাথা চুলকে আব্বাসের বাড়ির লোককে বলি, “আপনাদের পেশেন্টের বাঁচার আশা নেই!”
বাড়ির লোকের চোখ ছলছলে হয়ে যায়, "স্যার একবার শেষ চেষ্টা করুন! বড্ড বাচ্ছা ছেলে আমার!"
আরও পড়ুন
পেন, স্ক্যালপেল, LIFE (প্রথম ভিজিট)
পরদিন স্যার আসেন। বাড়ির লোককে স্যার একই কথা বলেন। বাড়ির লোক স্যারকেও একই অনুরোধ করে। নতুন করে সিটি স্ক্যান হয়। তাতে দেখা যায় ক্যান্সার শুধু ছড়িয়েই পড়েনি, সঙ্গে এদিক ওদিক মূত্রথলি,মূত্রনালি, কিডনি সব কিছু আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আমাদের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রিপোর্ট দেখে। ততদিনে আব্বাস হাসপাতালে কাটিয়ে ফেলেছে ৫-৬ দিন। এই ৫-৬ দিন আব্বাস রোজ ব্যাথায় কুঁকড়ানো মুখ নিয়ে শুয়ে থাকে। আমরা ওকে কিছু না কিছু ওষুধ দিই। কোনওদিন বাইরে থেকে তরল খাবার সোজা রক্তে পাঠিয়ে দিই। কোনওদিন প্রোটিন দিই। সঙ্গে রক্ত দেওয়া তো চলতেই থাকে। স্যার বেশ খুশি হন আমাদের কার্যকলাপ দেখে। আব্বাসের বাড়ির লোকও ভারি খুশি।
১৪ দিনের মাথায় আব্বাস যেন একটু সুস্থ হয়। আমাদের দেখলে হাসে। আমাদের সাথে হাসিঠাট্টা করে। আমরা জানি ওর ভবিতব্য কী। তাও আমরা ওর সাথে আড্ডা মারি রোজ। ওয়ার্ডে গিয়ে সবার আগে ওর সাথেই কথা বলি। কথায় কথায় জানতে পারি, ছেলেটার একটা মেয়েকে ভালো লাগত। ছেলেটার বড় বিজনেসম্যান হওয়ার ইচ্ছে ছিল। ছেলেটার কালো রং বেশ ভালো লাগত। ছেলেটার খুব সাধারণভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল।
আরও পড়ুন
প্রহারের অপেক্ষা : এক চিকিৎসকের রোজনামচা
রাউন্ডের শেষে চা-সিগারেট আমাদের ঐতিহাসিক প্রথা। একদিন চা খেতে খেতে আমার কো-পিজিটি সত্রাজিৎ বলেই ফেলে," ১৭ বছর বয়সে কী হতে চেয়েছিলি বল তো?"
মিথ্যা বললে পাপ হয়। বললাম, "ডাক্তারই হতে চেয়েছিলাম।"
"নাহ ভাই, আমি পাইলট হতে চেয়েছিলাম,” বলে একটু থেমে সত্রা বলে, “ছেলেটার কী দোষ বল তো? ওর একটা ইচ্ছাও কি বেআইনি? কিন্তু এটা ওর সাথেই কেন হল? আরও তো লোক ছিল। মাত্র ১৭ বছর বয়স। জীবনটা সদ্য শুরু হয়েছিল ওর।” আমরা দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকি। তারপর আধপোড়া সিগারেট ফেলে দিয়ে দুজনে হাঁটা লাগাই হোস্টেলের দিকে।
২০-২২ দিনের মাথায় আব্বাসের শরীর খারাপ হতে শুরু করে। সারা গায়ে জল জমতে শুরু করে। আমরা বিপদ গুনি। শেষের সময় আসতে চলেছে। শেষের সে সময় বড্ড ভয়ংকর। এরকমই একদিন আউটডোরের শেষে নতুন ফোন কেনার আনন্দে নাচতে নাচতে যখন ডিউটিতে সবে ঢুকেছি তখন ইন্টার্ণ দৌড়ে আসে, "দাদা, আব্বাস বোধহয় মারা গেছে!"
আমি সব ছেড়ে দৌড়ে যাই। বেডের পাশে সত্রাজিৎ দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে। বেডে আব্বাসের নিথর দেহ। যা হওয়ার হয়ে গেছে ততক্ষণে। পাশ থেকে আব্বাসের বাবা বলেন, “দু মিনিট আগেও শ্বাস নিচ্ছিল স্যার। তারপরে...।”
ওনাকে কি করে বোঝাই যে এভাবেই মৃত্যু থাবা বসায়। আচমকা। এভাবেই শেষ হয়ে যাই আমরা সব্বাই। হঠাৎ। চকিতে। কোনওমতে আব্বাসের বাবাকে বলি, “আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু…।”
আমার হাত ধরে ফেলেন আব্বাসের বাবা, ”স্যার আপনারা যা করেছেন.. কেউ করত না এরকম। আপনারা ভগবান স্যার। আপনাদের কোনও দোষ আমি দিচ্ছি না। সব দোষ আমার ছেলের ভাগ্যের স্যার।"
আমার তখন কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে এই ভদ্রলোকের একটা ছবি ল্যামিনেট করে টাঙিয়ে রাখি ওয়ার্ডের দেওয়ালে - ডেকে ডেকে সব পেশেন্টের বাড়ির লোককে দেখাই যে এই দেখুন! এঁকে চিনে রাখুন!
এসবের মাঝে চটকা ভাঙে - "স্যার খালি বডিটা যদি একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন…।"
সত্যি! কত সহজে একজন ছেলে থেকে বডি হয়ে যায়!
সিস্টারকে তাড়াতাড়ি বডি ছেড়ে দিতে বলে কিছুক্ষণ আব্বাসের নিথর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা আবার ফিরে গেলাম নিজেদের কাজের জগতে। আবার পরের পেশেন্ট দেখার জন্য।
আব্বাস তখন আমাদের জন্য শুধু একটা ধূসর স্মৃতি।
[লেখক নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক]
............................................
[কভার : অর্পণ দাস]