পুজোর বাড়ি, বাড়ির পুজো

দক্ষিণ কলকাতার বেশ সমৃদ্ধ লেক-গার্ডেন্স চত্বরে গুহমুস্তাফীদের বাড়ির বয়স আজ প্রায় তিপান্ন হলো। সে বাড়ির বড়-বউ সম্পর্কে আমার মেজো(রাঙা)পিসি। ছোট থেকেই আমার কাছে সেই বাড়িটি রাঙাপিসি-রাঙাপিসোমশায়ের বাড়ি; তাঁরা দোতলার বাসিন্দা। এই বছরের শুরুর দিকেই অবশ্য দীর্ঘ অসুস্থতার শেষে রাঙাপিসি চলে গেছেন, সেই বাড়ি ও পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আমার অস্তিত্বের এক বিরাট প্রাণবন্ত অংশও বিদায় নিয়েছে তাঁরই সঙ্গে। কিন্তু সব গিয়েও যা পড়ে থাকে স্মৃতি হয়ে, তার মূল্যই দিনশেষে অপরিসীম হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। আমার ক্ষেত্রেও কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি এর; কারণ এ তো আর রোজকার দশটা-পাঁচটার স্মৃতি নয় ঠিক; সে আমার একান্ত প্রিয় বাড়ির পুজোর স্মৃতি। সে শুধুই 'বাড়ি' নয়, পুজোবাড়ি।
জীবনের প্রথমদিকের স্মৃতিহীন কয়েক বছর যদি বাদও দিই, নয়-নয় করে এই পুজোবাড়ির সঙ্গে আমার সখ্য প্রায় ২৮-২৯ বছরের। আমি বড় হয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পুজোর স্মৃতিরা জমা হয়েছে মনের কোঠায়। একবারে পিছনে ফিরে তাকালে এখন আর প্রতিটা বছরের স্মৃতি স্পষ্টত ধরা দেয় না, ঘটনাক্রম আগে পরে হয়ে যায়। তাই, সেই চারণে এখন যদি পথে নামি, তা কিছুটা ঢিমে তালের হবে, এবং অসংলগ্নও বটে। পাঠকেরা, যাঁরা পুজোবাড়ির আবহের সঙ্গে পরিচিত, জানবেন, ঘটনাক্রম স্মরণ করার অতীতে বাড়ির পুজোর আরও একটি অবয়ব আমাদের মনে তৈরি হয় -- সামগ্রিকভাবে, প্রতিবছর পাঁচ দিনের যৌথতায় আমরা যে জীবন বেঁচে এলাম, তার স্মৃতি। আমার এই লেখা সেই উঠোনেই হাঁটাচলা করবে; কখনো হয়তো নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা স্মৃতিতে ভেসে উঠলে তাদের লিখে ফেলবো, তবে বেশিটাই আনাগোনা করবে বাড়ির পুজোর আমেজে, গন্ধে, শব্দে, বর্ণে, দৃশ্যে।
স্মৃতিবর্ণনের আগে পুজোবাড়ির একটা মোটামুটি স্পষ্ট মানচিত্র থাকা প্রয়োজন পাঠকের মনে। বড়রাস্তা (লর্ডস বেকারির মোড়) থেকে কিছুটা ভিতরে একটি মোটামুটি চওড়া বাই-লেনে আমাদের এই পুজোবাড়ি। মূল গেট দিয়ে ঢুকে একটি বড়সড় গাড়ি-চাতাল, এবং তার শেষপ্রান্তে নাটমঞ্চ -- পুজো হয় ওখানেই। বাঁ দিকে বাড়ির ভিতরে সিঁড়ি উঠে গেছে। একতলার বসার ঘরে সব সরঞ্জাম সরিয়ে এই পাঁচদিন প্রসাদ ভাগ ও বিতরণ হয়। দোতলা পেরিয়ে তিনতলার ছোট ছাদে ত্রিপল টাঙিয়ে খাওয়া-দাওয়া হতো দুপুরে-রাতে পাত পেড়ে, মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। বড় হওয়ার পর অবশ্য একেবারে চারতলার বড় ছাদেই এই ভোজন পর্বটি সারা হতে দেখেছি।
যে কোনও কিছুরই শুরুরও শুরু থাকে। তেমনই, পিসির বাড়ির পুজো খাতায় কলমে যতই শুরু হোক ষষ্ঠীর বোধনে, 'ব্যাকস্টেজ' কাজকর্ম শুরু হয়ে যেত দিন তিনেক আগে থেকেই। শুধুই কি মূল পুজোর আয়োজন, সরঞ্জামের জোগাড়, লার্জ স্কেলে রান্নাবান্নার কাঁচা বাজার? না, সব রকম ট্যালেন্টেরই কদর আছে পুজোবাড়িতে। থার্মোকল এনে, জলরং নিয়ে বসে যায় বাড়ির সব শিশু বা তরুণ শিল্পীরা। মণ্ডপের চারপাশের দেওয়াল বিভিন্ন থার্মোকল-কাটিং দিয়ে সাজানো হবে, জলরঙে আঁকা হবে শরতের মেঘ, কাশফুল, ঢাকির ঢাক-বাজানোর ভঙ্গিমা। নাটমঞ্চের লাল রঙের সীমানা সেজে উঠবে সাদা আলপনায়। এতসবের শেষে গিয়ে হবে বোধন, ষষ্ঠীর সন্ধেয় বাড়ির লোকজন আর নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতিই বেশি।
বেশিরভাগ সময়ই ষষ্ঠীর সন্ধেতে বা সপ্তমীর সকালে যখন আমি গিয়ে পৌঁছতাম, তখন পুজোর প্রত্যক্ষ কাজের চাপ বেশ রে-রে করে বাড়তে শুরু করেছে, আর পাশাপাশি বেড়েছে কাঁচা বাজারের চাপ। কাছেই লেক গার্ডেন্স সুপার মার্কেট, কথায় কথায় এর-তার উপর দায়িত্ব পড়ছে। স্বভাবগত উচ্চগ্রামে আলাপচারিতা চলছে --
"মিষ্টি আনা হয়েছে?"
"মিষ্টি?"
"তোকে তো বললাম সকালে সাতটা নাগাদ! আশ্চর্য!"
"সত্যিই তো আশ্চর্য! আমি তো এলামই দশটা নাগাদ! সাতটায় আমাকে কোথায় পেলে?"
"তবে কি হরিপদকে বললাম?"
"সে তুমিই জানো!"
"যাক গে, তুই নিয়ে আয়। হরিপদ শিওর ভুলেছে!"
কিছুক্ষণ পর একই দোকান থেকে হরিপদ এবং সে একই মিষ্টি দশ মিনিটের ব্যবধানে দুবার করে কিনে হাজির!
সপ্তমীর সকালে কলা-বৌকে স্নান করিয়ে আনার পর ঠাকুরমশাই আর পিসোর মুখ তুলে তাকানোর সময় বড় একটা নেই। তাঁরা নাটমঞ্চে পুজোর তৈয়ারিতে মগ্ন। তার মধ্যেই সম্পূর্ণ অসংলগ্ন, উদ্ভট, গোবিন্দভোগ চাল কিনতে গিয়ে চাঁদের ওজন জিজ্ঞেস করার মতো প্রশ্ন নিয়ে এক একজন আসছে।
"জলের বোতলগুলো কি তিনতলায়? খুঁজে পাচ্ছি না।"
"আমি কি তিনতলায় আছি বলে মনে হচ্ছে?"
"ও।"
কয়েক বছর আগে অব্দিও পুজোবাড়িতে ধীরেন ঠাকুর আসতেন তাঁর দলবল নিয়ে, পাঁচ দিনের জন্য। তিনতলার ছোট ছাদের একপাশে আড়াল করে নিতেন এসেই। সকাল থেকে সেই আড়ালে ছ্যাঁক-ছোঁক; আমরা ছোটরা খেলতে খেলতে এক একবার উঁকি মেরে দেখতাম -- ওই তো ঝুরি ঝুরি আলুভাজা সবে উঠলো কড়া থেকে, সঙ্গে একটু বাদাম আর কারিপাতা দেওয়া!
"ও ধীরেন জেঠু, একটু টেস্ট করাও!"
ধীরেন জেঠু অবশ্য খুবই স্নেহপরায়ণ মানুষ, চাইলে তাঁর ইয়াব্বড় মুঠোয় এতটা আলুভাজা তুলে, একটা থার্মোকলের বাটিতে করে আমাদের দিতেন। কিন্তু ধীরেন জেঠু কোনও কাজে একটু এদিক-সেদিক গেলে যিনি দায়িত্বে থাকতেন, মায়াদয়ার বড় অভাব সে শরীরে। আলুভাজা চাইতে এলে মাছি তাড়াচ্ছেন না মানুষ, বোঝা যেত না।
ধীরেন ঠাকুরের দলের কাজ নেহাৎ কম ছিল না -- দু বেলার বড় রান্না তো বটেই, তার সঙ্গে রোজ সকালে বেশ জম্পেশ ব্রেকফাস্ট; কোনোদিন লুচি-তরকারি, কোনোদিন চাউমিন! বাড়ির রান্নাঘর সে কদিনের জন্য ছুটি পেত। ত্রিপলের আড়াল থেকে ম্যাজিকের মতো পাত্রভরা সব খাবার বেরিয়ে আসতো, আর সকাল-দুপুর অতিথিদের পাত পেড়ে নুন-লেবু দেওয়া থেকে শুরু করে খাবার সার্ভ করার প্রাথমিক দায়িত্ব থাকতো আমাদের, ছোটদের। খাবার দেওয়ার সে কী আনন্দ! গরম-গরম মাছের কালিয়ার ট্রে, ভাতের ট্রে, মাছের মাথা দেওয়া মুগডালের বালতি হাতে জনে জনে গিয়ে জিজ্ঞেস করা, "আরেকটু দিই?" সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী প্রতিদিন দুপুরে বসতো প্রায় ২৫ জন করে তিনটে পুরো ব্যাচ; তাদের সবাইকে দেখেশুনে খাওয়ানোর দায়িত্ব কম বুঝি? তিন ব্যাচ সামলে চতুর্থ ব্যাচে আমরা ভাইবোনেরা বসতাম যখন খেতে, ততক্ষণে খিদে যেমন পেত, তেমন শেষ ব্যাচের সুবিধাও পাওয়া যেত কিছু! তখন ভাঙা আসর; যথেচ্ছ আলুভাজা, মাছ, চাটনি -- ডাক দিলেই পাতে পড়ে যাচ্ছে।
নীচে নাটমঞ্চে পুজোর ব্যস্ততা, এবং ছাদে অতিথিসৎকারের পূর্ণ আয়োজনের মাঝে এক মহা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল মণ্ডপে অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ ও সময়ে-সময়ে প্রসাদ বিতরণ। এই কাজের যে বিপুল চ্যালেঞ্জ, তা কাউকে বিন্দুমাত্র বুঝতে না দিয়ে রাঙাপিসিকে বছরের পর বছর দায়িত্ব পালন করে যেতে দেখেছি আমি। পিসির হাঁটুর ব্যথা ছিল, তাই বারবার উপর-নিচ করতে হবে এমন কাজে পিসি বড় একটা থাকতে চাইতেন না। সকাল সকাল স্নান সেরে সেই যে মণ্ডপে আসতেন, পুজোয় নজর রাখা থেকে শুরু করে অঞ্জলি-আরতির সময়ে সবার কাছে ডাক পাঠানো, বাড়ির অন্য বউদের সঙ্গে মিলে একজোটে প্রসাদ ভাগ করা থেকে শুরু করে অভ্যাগতরা দুপুরের খাবার খেতে যাওয়ার আগে যেন প্রত্যেকে প্রসাদ পান সেদিকে নজর রাখা, কারো তাড়া থাকলে মিষ্টির বাক্সে প্রসাদ ভরে তার হাতে দেওয়া -- আপাতভাবে তেমন চোখে পড়ার মতো কাজ না হলেও দিনশেষে পুজোবাড়ির সোপান-পরম্পরার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই সবই।
বছর দশেক আগে অবদিও এই পুজোবাড়ির একেবারে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল অষ্টমী আর নবমীর সন্ধেতে উত্তাল ধুনুচি নাচ। বিরাট গাড়িচাতালে হাত থেকে হাতে ঘুরত বড় বড় তিনটে ধুনুচি, সন্ধ্যারতির পর। বসার চেয়ার-টেয়ার সরিয়ে দেওয়া হতো; বাড়ির সকলে, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি পথচলতি মানুষও তখন এসে ভিড় করে দাঁড়াতেন সে নাচ দেখতে। বাচ্চা-বুড়ো একে একে কতজন আসতেন, ধুনুচি নিয়ে সে কী কসরৎ! মাঝেমাঝে ধুনুচি নামিয়ে তাতে ধুনো ছিটিয়ে, বাতাস করে আরও জাগিয়ে দেওয়া হতো যেন! তখন এক পরিবেশ -- রবি শাস্ত্রীর কমেন্ট্রিতে একেই বলে বোধ হয় 'ইলেক্ট্রিফায়িং অ্যাটমস্ফিয়ার'! এমনকি আমরা -- যাদের কাছে উঠোন প্রায় চিরন্তনই বাঁকা -- তারাও সাহস করে নেমে দেখতাম, আরে! একেবারে যে হচ্ছে না, তা তো নয়। ঢাকের তালে তালে কাজ চালিয়ে দিতে পারছি বেশ। অবশ্য ওটুকুই; ট্রেনিং-ব্যতীত এর বেশি কেরদানি করতে গেলে জ্বলন্ত ছোবড়া উড়ে পাশের মানুষের চুল পুড়ে যাওয়ার ঘটনা খুব অসম্ভব ও অভিপ্রেত, কোনোটাই নয়।
ধুনুচি নাচের পর নবমীতে আরেকটা গুরুদায়িত্ব থাকতো ১৫-৩০ বছর বয়সের মানুষজনের -- একটা নির্ভেজাল বিচিত্রানুষ্ঠান নামানো! তিরিশের আশেপাশে বাড়ির বড় দিদি বা দাদারা এ বিষয়ে ম্যানেজারের পদে থাকতেন, তাঁদের কাজ ছিল প্রথমেই শিল্পীদের নামের একটা লিস্টি তৈরি করা। এইটা বোধহয় পুজো শুরুর আগেই তৈরি হয়ে যেত; তখন সবাই বলতো গান, আবৃত্তি, নাটক সব করবে। তারপর এক একটা দিন এগোতো, আর নামের ভিড় কমতে থাকতো। যে তুড়ি মেরে বলেছিল সে অলরাউন্ডার, এখন বলতে শুরু করতো কোরাস ছাড়া গাইবে না, কারণ আচমকাই গলায় একটু ‘খুশখুশ’। এদিকে নবমীর আগের দিনগুলোয় দুপুরে খাওয়ার পর, আর সন্ধেয় আরতির পর ঘর বন্ধ করে কঠিন রিহার্সালের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতো কোনও নাটক -- বেশিরভাগ সময়ই সুকুমার রায়ের কোনো না কোনো গল্পের আদলে। এক বছর নবমীতে অভিনীত হবে 'সবজান্তা দাদা'। সর্বার্থে থার্ড থিয়েটার যাকে বলে আর কী -- তিনদিক দিয়ে বাড়ির মানুষ ঘিরে বসেছে, নাটক হচ্ছে মঞ্চের নীচে, আর মঞ্চের উপরে আবার মা, তাঁর চার সন্তান, বাহন, অসুর, মায় মোষটা অব্দি টেরিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। দৃশ্যটা এমন – একজন মনখারাপ করে একা বসে আছে, তাকে সান্ত্বনা দিতে আসবে আরেকজন, বুঝিয়ে-বাঝিয়ে আবার অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তা যার মনখারাপ, সে তো বেজায় মুখভার করে হুলো বেড়াল হয়ে বসে আছে। এদিকে, সান্ত্বনা দিতে আসবে যে, সে তার আগের দৃশ্যটাতেই উইং থেকে নাটক দেখতে দেখতে খুব হেসেছে, এখনও থামাতে পারছে না সেই হাসি। অন্য উইং থেকে ম্যানেজার দিদি ডুবে যেতে থাকে জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো উদ্ভট হাত-পা নেড়ে তাকে ঢুকতে বলছে। সে ঢুকলো, এগিয়ে গেল মনখারাপির কাছে, কিন্তু গিয়েই "আমি না, আরেকটু পরে আসছি" বলে হাসির দমকে কাঁপতে কাঁপতে অন্য উইং দিয়ে বেরিয়ে গেল।
এই করতে করতে এসে পড়তো দশমী। বিদায়ের সুর লাগতো সবখানেই, যেমন লাগে। অন্য চারদিনের তুলনায়, দশমীর দুপুরে মণ্ডপে এসে পড়া রোদকে আরও কিছুটা ম্লান মনে হতো। বরণডালা সাজিয়ে বাড়ির এয়োস্ত্রীরা মায়ের গালে রাখতেন পানপাতা, সবার মুখে সন্দেশ দেওয়া হতো। আমরা ছোটরা প্রাণপণে অসুরকেই সিঁদুর মাখিয়ে চামুন্ডা করে তুলতাম প্রায়! দশমীর দুপুরের খাওয়া-দাওয়ায় মন বসত না কারুরই। বিকেল না আসতেই একটা মাঝারি সাইজের লরি করে একচালায় সবাইকে নিয়ে রওনা দেওয়া হতো বড়গঙ্গায়, বাবুঘাটে। বয়সের, বা বিষাদের ভারে যাঁরা তদ্দূর আর যেতেন না, বারান্দায়-ছাদে দাঁড়িয়ে বলতেন, "আবার এসো, আবার এসো"।
কিন্তু এই দৃশ্যমান দশমীর অতীতে ক্রমশই অলক্ষ্যে বৃদ্ধি পেয়ে চলে আরেক দশমী, যেমন আজ-কাল-পরশু জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় একজন মানুষের জীবনকাল। সেই দশমীতে মা যদি বা বারবার যাওয়া আসা করেন, অতিপরিচিত পুজোবাড়ির চেনা চেনা মুখগুলো একবার যে যায়, আর আসে না। কেউ যায় দেশ ছেড়ে, কেউ দেহ ছেড়ে। এমনিতে গুহমুস্তাফীদের এই পুজোর বয়স ৩০০ বছরেরও বেশি, এর ইতিহাস ছড়িয়ে আছে পূর্ববঙ্গে। তবু, শুধু যদি লেক গার্ডেন্সের এই বাড়ির পুজোর কথাই ধরি, ২০১৮ সালে যখন সে পুজো পঞ্চাশ বছরে পা দিল, তখন প্রবীণ প্রজন্ম হারিয়ে যাচ্ছে অবসরে, অনিবার্যতায়, অথচ নবীন প্রজন্ম আশ্চর্য উদাসীন। চোখের সামনে মণ্ডপ ফাঁকা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে, দুপুরে-রাতে অতিথিভোজন নামমাত্র। ঠাকুরদের বড় বড় কড়ায় রান্নাবান্না বন্ধ হচ্ছে, তাঁদের প্রয়োজন ফুরোচ্ছে; এসে পড়ছে হোম ডেলিভারি। দশমীর বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার মানুষের সংখ্যা কমে আসছে, কমছে লরিতে চেপে বড়গঙ্গা যাওয়ার ভিড় ও উৎসাহও। এই ক্রমবর্ধমান দশমীতে দাঁড়িয়ে আবার ষষ্ঠীর বোধন ফিরিয়ে আনা যায় না; এই দশমীর শেষে কোনও 'আসছে বছর' নেই, তাই 'আবার হবে' বলার সাহসও মুখে জোগায় না। ২০১৯-এর পর থেকে আপাতত এই বাড়ির পুজো স্থগিত। অতিমারি, রোগ, মৃত্যুমুখে মণ্ডপে মানুষের অনুপস্থিতিই স্থান পেয়েছে, নাটমঞ্চে ধুলো পড়েছে। ঝড়ঝাপটা সামলে আবারও নিশ্চয়ই ফিরবে পুজোবাড়ি, তবে ততদিন স্মৃতিই ভরসা।
আরও পড়ুন: একটি পুজোর গোড়ার কথা শৌভিক মুখোপাধ্যায়
চিত্র সম্পাদনা- অর্পণ দাস
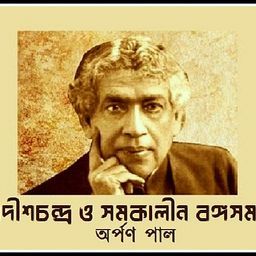
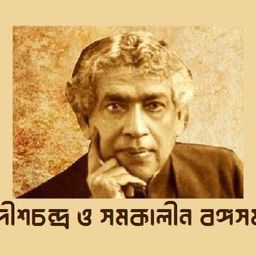
Amitava Moitra
খুব কাছ থেকে অনুভব করতে পারছি শব্দগুলোকে। খুব চেনা সুর।